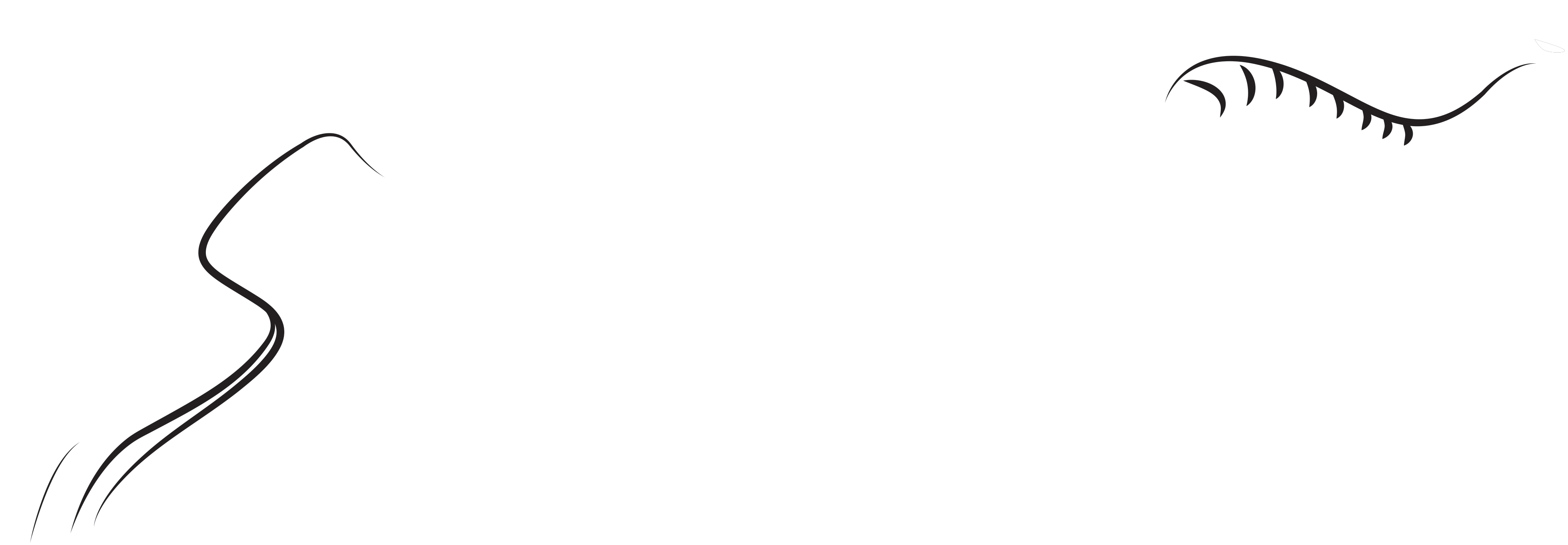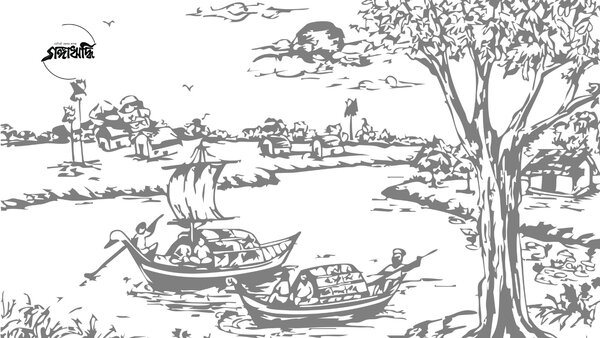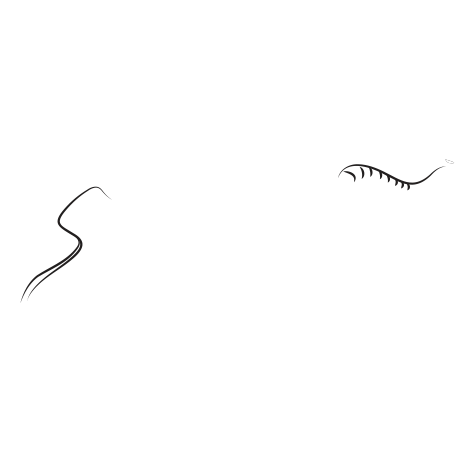ভরতেরকান্দী
যতোটুকু জানা যায়, বর্তমান ভরতেরকান্দী এলাকায় একসময় ভরত নামে একজন হিন্দু ছিলেন। তিনি পেশায় কুমোর ছিলেন। হাড়ি-পাতিল তৈরির কুমোর শুধু নয়, দেখতেও নাকি ছিলেন রাজকুমারের মতো। অতিশয় সুন্দর ভরত বাবু আচার-আচরণে এলাকার সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। এলাকায় যথেষ্ঠ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো তার। গুণমুগ্ধতার কারণে একটি সময়ে এসে এলাকা তথা গ্রামের নাম রাখার প্রয়োজনে সবাই মিলে ভরত বাবুর নাম অনুসারে গ্রামের নাম রাখেন ভরতকান্দী। ওই ভরতকান্দী পরবর্তীতে হয়ে যায় ভরতেরকান্দী। ভরতেরকান্দীতে একটি বাজার আছে। নাম পেত্নির বাজার। আগের দিনে রাতের বেলায়, বিশেষ করে গভীর অন্ধকার রাতে এ-বাজারে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতো, যা ভূত-পেত্নিরা ঘটাতো মনে করে বাজারের নাম রাখা হয়েছিলো পেত্নির বাজার। গ্রামের ভরতেরকান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৩৯ সালে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব মরহুম আবদুর রাজ্জাক মোল্লা সাহেবের দানকৃত জমির উপর। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন মরহুম হাফিজ উদ্দিন সরকার, মো. তমিজ উদ্দিন প্রধান, আবদুল ওয়াহাব মোল্লা, দানিছ মোল্লা এবং জমিদাতা আবদুর রাজ্জাক মোল্লা। বিদ্যালয়ের কীর্তিমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. একেএম রাশিদুল আলম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
কুমরাদী
এই গ্রাম নিয়ে আধ্যাত্মিক ও মজার ঘটনা রয়েছে। একসময় গ্রামটিতে একজন অসুস্থ মহিলা ছিলেন। তার নাম ছিলো ‘রাদী’। তার অসুস্থতা এমন মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছিলো যে, কোনোপ্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হচ্ছিলো না। অনেক কিছুর পর একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির চিকিৎসায় মহিলা সুস্থ হয়ে ওঠেন। জানা যায়, রাদীকে চিকিৎসা দেয়ার পর বুজুর্গ ব্যক্তিটি উচ্চস্বরে বলেছিলেন, “কুমরাদী বা উঠো রাদী।” ‘কুমরা’ শব্দের একটি অর্থ গড়াগড়ি খাওয়া। অসুস্থ সেই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করছিলেন। বুজুর্গ হুজুর বলেছিলেন, কুমরাদী বা গড়াগড়ি থেকে উঠো। হুজুরের সেদিনের সেই কথার পর আর তাকে গড়াগড়ি করতে হয়নি এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই ‘কুমরাদী’ বলা থেকেই পরবর্তীতে গ্রামের নাম হয়ে যায় কুমরাদী। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, কুম্ভরাণী নামে সে-এলাকায় একজন জমিদার ছিলেন এবং তার নাম থেকেই প্রথমে কুম্ভরাণী ও পরে কুমরাদী নামটি এসেছে। এলাকায় আরো জনশ্রুতি আছে যে, এখানে একসময় গভীর জঙ্গল ছিলো। ওই গহীন জঙ্গলে শাহ মনসুর আলী (র.) নামে একজন দরবেশ বসবাস করতেন। তখনকার সময়ে অতি দ্রুত দরবেশের নাম ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নামধাম শুনে বর্তমান কুমিল্লার স্থানীয় এক নিঃসন্তান রাজা তার রাণীসমেত সন্তান লাভের আশায় আমাদের নরসিংদীর কুমরাদীতে দরবেশের আস্তানায় হাজির হন। দরবেশের সাথে সাক্ষাত করে তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সন্তান লাভের প্রার্থনা করেন। দরবেশ সন্তান লাভের জন্যে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সাথে কিছু শর্ত যুক্ত করে দেন। শর্তে বলা হয়েছিল যে, যদি তারা কন্যা সন্তান লাভ করে, তবে সেই কন্যাকে দরবেশের সাথে বিয়ে দিতে হবে। দিগ্বিদিক চিন্তা না করে রাজা-রাণী দরবেশের শর্তে রাজি হয়ে যান। দরবেশ আল্লাহর নিকট তাদের সন্তান লাভের প্রার্থনা করলে মহান রাব্বুল আলামিন তাতে সাড়া দেন। তাদের ঘরে আলো ঝলমলে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। সেই কন্যা শাহজাদীর নাম রাখা হয় রাদী। শাহজাদী ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকেন। একসময় রাজ্যের ভবিষ্যত শাহজাদী বিবাহযোগ্যা হন। অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের শর্তের কথা রাজার মনে থাকলেও রাণী তা বেমালুম ভুলে যান। তাকে বিষয়টি অবগত করানো হলে তিনি আগের শর্ত মানতে রাজি হননি। তড়িঘড়ি করে অন্য কোনো রাজ্যের রাজপুত্রের সাথে রাণী শাহজাদীর সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেন। রাজ্যময় বিয়ের সানাই বেজে ওঠে। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন চলে। সমস্ত প্রজাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এর মাঝে হঠাৎ শাহজাদী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক কান্নাকাটি, বড়ো বড়ো বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করানো হলেও শাহজাদী সুস্থ হননি। শর্ত ভঙ্গের কারণে রাজা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। অনন্যোপায় হয়ে রাজা পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে মেয়েকে নিয়ে কুমরাদীতে দরবেশের আস্তানায় চলে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু দুঃখজনক যে, দরবেশ তখন আস্তানার বাইরে ছিলেন। কোনো উপায় করতে না পেরে রাজা মেয়েকে আস্তানায় রেখে চলে যান। তার অনেক পরে দরবেশ ফিরে এসে এহেন অবস্থা দেখে সহজেই ঘটনা বুঝে ফেলেন। তিনি মেয়েটিকে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে ওঠেন, “কুম, কুম”, যার অর্থ রাদী উঠো। সহসা শাহজাদী জ্ঞান ফিরে পান। এ-ঘটনা পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। এভাবে গ্রামের নাম হয় কুমরাদী। অনেকের মতে, কুমরাদীতে বর্তমানে যেই ভগ্নদশার দরগাহ রয়েছে, তা সেই আধ্যাত্মিক দরবেশেরই। এখনো প্রতিদিন অনেক মানুষ তা দেখতে আসেন। দরগাহ বা মাজার সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পরবর্তীতে, সাথে এতিমখানা। কুমরাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে, ব্রিটিশ আমলে। মাওলানা আবদুল আজিজ এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন পুটিয়া ইউনিয়নের এককালের প্রখ্যাত চেয়ারম্যান আবদুর জব্বার মাস্টার, যিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আরো সহযোগিতা করেছেন মরহুম আলাউদ্দিন শিকদার, মো. শামসু ভূঁইয়া ও মো. আবুল হাশেম। প্রায় ১০৪ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্যেও স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের পুত্র ব্যারিস্টার আবু তাহের আবদুল্লাহ। এই গ্রামেই রয়েছে দেশ বিখ্যাত ও একসময়ের আন্তর্জাতিক মানের কুমরাদী দারুল উলুম মাদরাসা।
কুমরাদী গ্রাম ও শিবপুরে মাদরাসা শিক্ষার কথা
মাদরাসা শিক্ষা সর্বপ্রথম চালু হয়েছিলো মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মাদরাসা স্থাপনের মাধ্যমে। তিনি মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববীর পাশে ‘সুফফা আবাসিক’ ও ‘দারুল কুববাহ’ নামে দুইটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন বলে ইতিহাস রয়েছে। এছাড়াও তিনি মসজিদভিত্তিক মাদরাসা চালু করেছিলেন। খলিফাগণের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় এবং হযরত আলী (রা.) বুশরা ও কুফায় মাদরাসা শিক্ষা চালু করেছিলেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলেও মাদরাসা শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছিলো। কোথাও কোথাও মাদরাসাভিত্তিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাও চালু হয়েছিলো।
বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়েছিলো সুলতানি আমলে। ১২৭৮ সালে সোনারগাঁয়ে একটি মাদরাসা স্থাপিত হয়, যেটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদরাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৭৮০ সালে কলকাতায় আলিয়া মাদরাসা স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে ‘দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা হওয়ার পর এদেশে কওমী মাদরাসার প্রচলন শুরু হয়। তারও আগে ঢাকায় হাজী মহসিন ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও চালুর এমন ধারাবাহিকতায় নরসিংদীর শিবপুরে ‘কুমরাদী দারুল উলুম মাদরাসা’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল আজিজ। এই মাদরাসা হতে বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে জগতখ্যাতি অর্জন করেছেন। আজিজ সাহেব মাদরাসার পাশাপাশি স্বতন্ত্র এতিমখানাও তৈরি করেছিলেন। বহু এতিম এখানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেয়ে লেখাপড়া করে তাদের জীবনের পথ খুঁজে নিতে পেরেছে। এখানে এতিম মেয়েদের পড়াশোনার পর তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে এতিমখানার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত পাত্রের কাছে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। শুধু তা-ই নয়, নবদম্পতির ভবিষত উন্নয়নের জন্যে আর্থিক সহযোগিতারও ব্যবস্থা করে দেয়া হতো।
লেখক : সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার