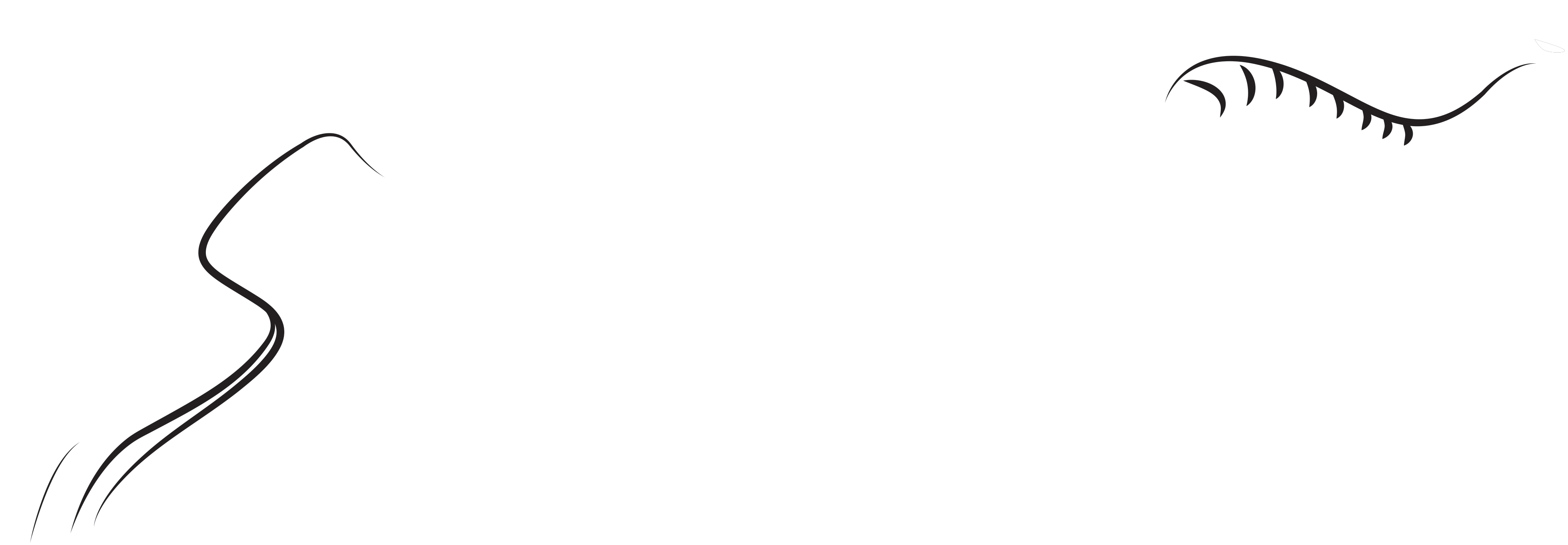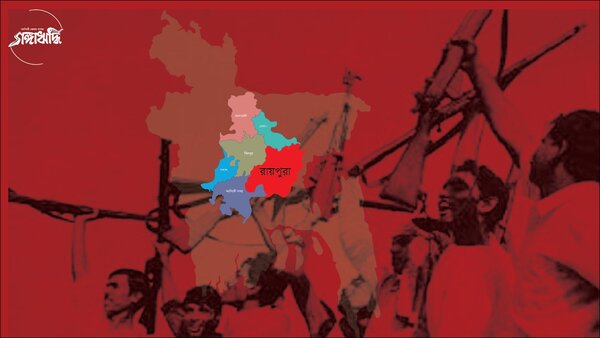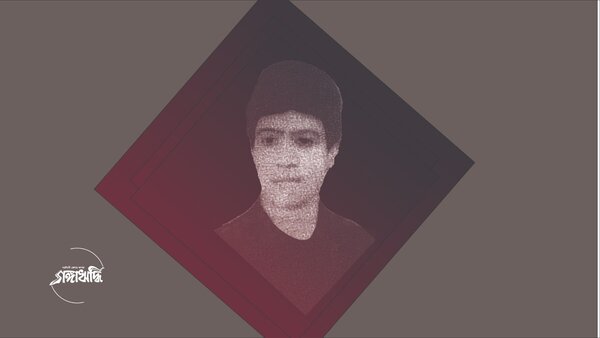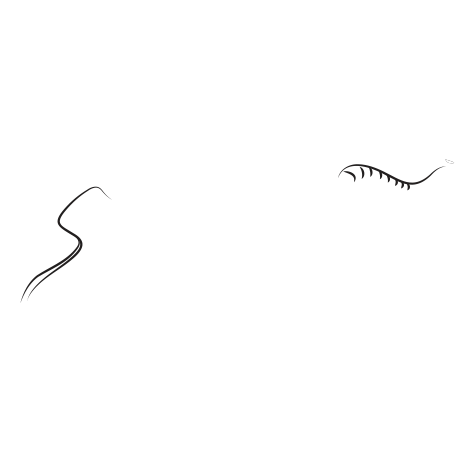প্রসন্নতারা গুপ্তা
প্রসন্নতারা গুপ্তার জন্ম ১৮৫৫ সালের ২ এপ্রিল। তাঁর পৈতৃক নিবাস নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারের দুপতারা। দুুপতারার এই গুপ্ত জমিদার পরিবার প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন। ভাটপাড়া গুপ্ত পরিবারের সাথে দুুপতারা গুপ্ত পরিবারের আন্তরিক যোগাযোগ ছিলো, ছিলো গভীর সম্পর্ক। কে জি গুপ্তের বাবা কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন একজন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আলোকিত মানুষ। তিনি সমাজসেবা ও নারী জাগরণের বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে নারী জীবনের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা সভা’। নামই বলে দেয় তার কার্যক্রম, লক্ষ্য ও আদর্শ কী ছিলো। ‘অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা সভা’ সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের সময়ে (১৮৭০) প্রসন্নতারা গুপ্তা একজন তরুণী। তিনি এ-সংগঠন গঠনে আন্তরিক প্রয়াস চালান। তা দেখে কালীনারায়ণ অত্যন্ত প্রীত হন। সে-সময় কে জি গুপ্ত মাত্র ১৯ বছরের তরুণ (১৮৫১ সন)। ধারণা করা যায় যে, প্রসন্নতারার মেধা-প্রজ্ঞা ও কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করেই কালীনারায়ণ তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে বেছে নেন।
১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা ‘সখি সমিতি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন এই প্রসন্নতারা গুপ্তা। উক্ত সমিতিতে একমাত্র মুসলিম সদস্য ছিলেন লাকসামের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী। উক্ত সমিতির মাধ্যমে কে জি গুপ্তের স্ত্রী প্রসন্নতারা স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিয়ের প্রচলন, সহমরণ প্রথা রোধ তথা মেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্যে অনেক কাজ করেছেন। এই ‘সখি সমিতি’র আরো একজন সুহৃদ ও সহযোগী ছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তাঁর আত্মচরিত থেকে জানা যায়, তিনি নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের একজন প্রবক্তা। এমনকি মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার সাথেও তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ চলতো, চলতো মতবিনিময়।
প্রসন্নতারা গুপ্তার ডাকনাম ‘তুফানি’। তিনি যথার্থভাবে তুফানের ন্যায় কাজ করতেন বলে জানা যায়। তাঁর কর্মবহুল জীবন মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে এ-বিদুষী ও প্রগতিশীল মহিলা ১৯০৮ সালের ১৫ আগস্ট লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘পারিবারিক জীবন’ প্রকাশিত হয় ১৩১০ বঙ্গাব্দে। ঈর্ষণীয় সামাজিক জীবনের পাশাপাশি প্রসন্নতারা ও কে জি গুপ্তের দাম্পত্য জীবন তথা পারিবারিক জীবনও ছিলো সাবলীল। সংসারে সাফল্যের কোনো অন্ত ছিলো না। মোট চার সন্তান জন্ম নেয় তাঁদের ঘরে। বীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, ধীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত ও হেমকুসুম। এই হেমকুসুমই বাংলার প্রসিদ্ধ গীতিকবি অতুলপ্রসাদ সেনের স্ত্রী।
অবিভক্ত বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ, ধর্ম সংস্কার, বিধবা বিবাহ, সহমরণ প্রথা বাতিলসহ আরো অনেক জনহিতকর কার্যে কে জি গুপ্তের অবদান যেমন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনই স্মরণীয় হয়ে আছেন প্রসন্নতারা গুপ্তা।
প্রিয়বালা গুপ্তা
বিশ শতকের একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রতিকূল সমাজে নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অদম্য তাগিদ নিয়ে জন্মেছিলেন একজন নারী। নাম প্রিয়বালা গুপ্তা। ১৮৯৯ সালে ভাগলপুরে জন্ম হলেও পৈতৃক বাড়ি নরসিংদীর পাঁচদোনায়। শৈশবেই মেধার পরিচয় দিলেও অল্প বয়সেই পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। এবং ১৩ বছর বয়সেই মাধবদীতে বনেদি রায় পরিবারে বিবাহিত জীবন শুরু করতে বাধ্য হন। একান্নবর্তী রায় পরিবারে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রিয়বালার সংবেদনশীল মনে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। সাহিত্যচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই সময়ই গ্রামের নিরক্ষর বধূদের নিয়ে সপ্তাহের প্রতি রোববার আসর বসাতেন। সেখানে গল্পের ছলে দেশ, সমাজ, ভূগোল, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হতো। এই আসরই পরবর্তীতে মেয়েদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত তৈরি করে। সেই সময় পঞ্চাশের মন্বন্তর বা বাংলার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র সাথে যুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৪ সালে প্রিয়বালার উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয় ‘মাধবদী শিশু সদন বিদ্যা নিকেতন’। স্বামী যতীন্দ্রমোহন রায় ও তৎকালীন মাধবদী হাই স্কুলের হেডমাস্টার শচীনন্দন সাহেবের সহায়তায় বাড়ির বৈঠকখানায় মাত্র দুজন মেয়ে নিয়ে এর সূচনা হয়। প্রারম্ভে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত খোলার প্রস্তাব থাকলেও শিশু শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিলো। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মাধবদীর পাশাপাশি সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রীরা আসতো। নানা বিপত্তি পেরিয়ে স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ সালে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের একটি কেন্দ্রের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ‘সাহিত্যভারতী’ উপাধি পান। ইতোমধ্যে গীতিনাট্য রচনায় তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। ঢাকা রেডিওতে তাঁর রচিত গীতিনাট্য ‘শকুন্তলা’, ‘শবরীর প্রতীক্ষা’, ও ‘উর্মিলা’ সম্প্রচারিত হয়। তৎকালীন সমাজে শিশু ও প্রসূতি পরিচর্যায় বিবিধ কুসংস্কারে বিচলিত হয়ে পড়েন প্রিয়বালা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী হয়েও ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে এগিয়ে আসেন। এসব কাজের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলেন।
বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মনোগঠন নির্মাণ ও বিকাশকল্পে মাধবদীর বদ্ধ সমাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত নাচ, গান, আবৃত্তি ও মূকাভিনয় হতো। হাতে লেখা সাহিত্য পত্রিকা ‘কিশলয়’ বের হতো। গান লেখার প্রতিভা ছিলো তাঁর। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও সঙ্গীতশিল্পীদের অনুরোধে গান লিখে দিতেন। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর অনিরাপত্তায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশত্যাগ বাড়তে থাকে মাধবদী অঞ্চলে। পড়াশোনার জন্যে পুত্র-কন্যাকে পার্শ্ববর্তী দেশে পাঠিয়ে দিলেও নিজে রয়ে যান এই দেশে। মানুষের ভালোবাসায় মাধবদী বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি হয়ে রয়ে গেলেন। ১৯৫৪ সালে প্রিয়বালার স্বামী মারা গেলেন। এক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে সন্তানদের দেখতে গিয়ে নানা জটিলতায় আর ফিরে আসতে পারেননি এই বাংলায়। মৃত্যুর পূর্বে ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি ‘স্মৃতিমঞ্জুষা’ নামে আত্মজীবনী লিখতে থাকেন। এই আত্মজৈবনিক রচনা তাঁর জীবনীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশসহ নানা বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষ্য হয়ে রইলো। সমাজ সংস্কারক ও মহীয়সী প্রিয়বালা গুপ্তা ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। প্রিয়বালার দৃঢ় সংকল্প জীবনযাত্রা দেখিয়ে দেয়, পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজে কীভাবে শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে সচেতনতা ও মুক্তমনের প্রদীপ জ্বালানো যায়, ঘটানো যায় পরিবর্তন।
হিরণবালা রায়
এ-অঞ্চলের খুবই কম আলোচ্য, বলা যায়, ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করা লোকজনের আলোচনায় না থাকা একজন নারী ছিলেন হিরণবালা রায়। একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী ছিলেন তিনি।
মাধবদীর আটপাইকা গ্রামটির তালুকদার ছিলেন মণীন্দ্র রায়, সতীন্দ্র রায় ভ্রাতৃদ্বয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক। বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সংস্পর্শে এসে দুই ভাই অনুশীলন পার্টি, পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আটপাইকায় তাঁদের বাড়িটি কমিউনিস্ট পার্টির অঘোষিত কেন্দ্র ছিলো। তাঁরা আশেপাশের দশ-বারো গ্রামে কৃষক সমিতি’র কাজে নিয়ত ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের দিদি হিরণবালা থাকতেন আসামে, স্বামী চা বাগানের ডাক্তার, সাত সন্তানের জননী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ছ’টি ছেলেই মারা যায়, স্বামীও কী এক অজানা রোগে মারা যান। সর্বশেষ ছেলেটি হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় চলে যায়, যোগাযোগ ছিন্ন। হিরণবালা রায়ের পাগল হতে বাকি। জীবনের এই চরম দুর্ভোগমুহূর্তে তিনি আটপাইকায় ভাইয়ের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। হতাশাগ্রস্ত এক বিষণ্ণ বিধবা। ক্রমে ভাইয়ের পরামর্শ ও চেষ্টার ফলে স্বাভাবিক হন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই বাড়িটা যেহেতু একটা রাজনৈতিক আড্ডাখানা ছিলো, তাই হিরণবালাও দূরে থাকতে পারেননি এসব থেকে। সমাজের আর্তপীড়িত মানুষের সেবায় নিয়োজিত হলেন।
তিনি মহিলা আন্দোলন শুরু করলেন। হিরণবালা রায় ছিলেন নরসিংদী থানার প্রথম মহিলা সংগঠক। আটপাইকা থেকে সাটিরপাড়া, নরসিংদী; শেখেরচর, ভাটপাড়া, পাঁচদোনা থেকে মাধবদী, কাশীপুর, আলগী পর্যন্ত ছিলো তাঁর কর্মক্ষেত্র। সবই পায়ে হেঁটে। তিনি পরে নবপ্রতিষ্ঠিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নরসিংদী থানা কমিটির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। সম্ভবত পরে সমিতির জেলা কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।
চল্লিশের দশকে যখন এ-অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, হিরণবালা রায় গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাথে ছিলেন মাধবদীর আরেক মহীয়সী নারী প্রিয়বালা গুপ্তা। দেশভাগের খড়গ যখন সাম্প্রদায়িকতার নীল রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো, তখন হিরণবালা রায়ের মতো মানবতাবাদী মানুষেরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন প্রতিবেশিদের রক্তে যেন রঞ্জিত না হয় প্রতিবেশির শরীর। দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেছিলেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত তা পেরে না ওঠায় আর কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকেই ছদ্মবেশে ওপার বাংলায় পাড়ি দেন। পরে আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।
এই সাহসী নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিরণবালা রায় সব যুগের নারীদের জন্যে আদর্শ।
মতিজান খাদিজা খাতুন
তিনি শহীদ আসাদের মা হিসেবেই বেশি পরিচিত। তবে তিনি একজন সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন মহীয়সী নারী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা অনন্য। স্বামী প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, ঋদ্ধ শিক্ষাবিদ শিবপুরের ধানুয়া গ্রামের মৌলানা মো. আবু তাহের। শুধু আসাদ নয়, তাঁর ছেলেমেয়েদের সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। খাদিজা খাতুনের বড়ো পরিচয়, তিনি নারী স্বাধিকার আন্দোলনের সাহসী সৈনিক ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণ তথা নারী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে (বেগম রোকেয়ার মৃত্যুসন) নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় আইইটি অর্থাৎ ইসলামী এডুকেশন ট্রাস্ট। সেই আইইটির ফসল নারায়ণগঞ্জ আইইটি গার্লস স্কুল। শুধু তা-ই নয়, তিনি নিযুক্ত হন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেও। সে-সময়ের বাস্তবতায় এমন সাহসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম মহিলা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলো। তাই তাঁকে যদি নরসিংদীর বেগম রোকেয়া বলা হয়, তাহলে খুব অন্যায় হবে বলে মনে করি না।

খাদিজা খাতুন নারী স্বাধিকার আন্দোলনের নেত্রীই ছিলেন না শুধু, জাতীয় উন্নয়নেও তাঁর কর্মতৎপরতা ছিলো প্রশংসনীয়। বিশেষ করে, স্বামী মৌলানা মো. আবু তাহেরের ইসলামী উম্মাহর খেদমতে ও শিক্ষা বিস্তারে বরাবর তাঁর ভূমিকা ছিলো ইতিবাচক।
ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে তিনি হারান পুত্র আসাদকে। অন্য আট-দশজন মহিলার মতো তিনি কেঁদে-কেটে অস্থির হননি। তার প্রমাণ মেলে আসাদের শাহাদত বরণের মাত্র ১৫ দিন পর ১৯৬৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (রোকেয়া হল) থেকে প্রকাশিত স্মরণিকায় তাঁর লিখিত বাণীতে :
“আমার আসাদ মরেছে। কিন্তু আজ আমি লাখো আসাদ পেয়েছি। আমার আসাদ বলতো, মা, আগামী দশ বৎসরে আমরা এক নতুন দেশ গড়ে তুলব। তোমরা তার সাধ পূর্ণ করো।”
ড. আফিয়া খাতুন
ড. আফিয়া খাতুনের জন্ম ১৯২৭ সালে, ঢাকায়। পৈতৃক নিবাস বর্তমান নরসিংদীতে। তাঁর পিতা কিংবদন্তী সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ সেকান্দর আলী মাস্টার ও মা শফুরা খাতুন। ১৯৪০ সালে ইডেন স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইন্টারমিডিয়েটেও একই ফল। ইডেন কলেজের এই কৃতী ছাত্রী ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। ভাষা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিলো অভূতপূর্ব। তিনি ইডেন কলেজে অধ্যাপনার (১৯৫৪-১৯৬১) মধ্য দিয়ে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করেন। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯৫৩ সালে নিউজিল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আফিয়াই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পান। তিনি ইউনিভার্সিটি অব নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষকতা করেছেন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্প্রসারণ সেন্টার, ঢাকা ও পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা সম্প্রসারণ সেন্টার, লাহোরে। তিনি পড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি, কলাম্বিয়া ও সান ডিয়াগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ড. আফিয়ার প্রথম স্বামী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (১৯১৮-৬৫)। শামসুল হক ও আফিয়া খাতুন দম্পতির দুই সন্তান উম্মে বতুল ফাতেমা জোহরা এবং উম্মে বতুল তাজমে তাহেরা। পরে ড. আফিয়ার আবার বিয়ে হয় সহকর্মী ভাষাবিজ্ঞানী, পাঞ্জাবের জলন্ধরের অধিবাসী অধ্যাপক আনোয়ার দিলের সঙ্গে।
ড. আফিয়া খাতুনের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড কালচার, বেঙ্গলি নার্সারি রাইমস : অ্যান ইন্টারন্যাশনাল পারসপেকটিভ, টু ট্র্যাডিশনস অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ। বাংলা ভাষায় রচিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের পত্র, ক্যারোলাইন প্রাটের আই লার্ন ফ্রম চিলড্রেন (বাংলা অনুবাদ, ১৯৫৫), যে দেশ মনে পড়ে (১৯৫৭, ভ্রমণকাহিনি), হেলেন কেলারের লেখা মাই টিচার (বাংলা অনুবাদ : হেলেন কেলার আমার শিক্ষক)। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও নাটক ‘তরঙ্গভঙ্গ’ তিনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। স্বামী আনোয়ার দিলের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন উইমেন্স চেঞ্জিং পজিশন ইন বাংলাদেশ : ট্রিবিউট টু বেগম রোকেয়া, ডেভেলপিং সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান। তাঁদের ৪০ বছরের যৌথ গবেষণার ফসল ইংরেজিতে রচিত ৭৭৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ। বিশেষ করে, এই গ্রন্থটি ভাষা আন্দোলনের ফলাফলস্বরূপ সার্বিক বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রিক একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আছে। এই মহীয়সী নারী ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।
তথ্যসূত্র
১. কন্যা জায়া জননী, সরকার আবুল কালাম ও
২. আলোর অভিমুখে : প্রিয়বালা গুপ্তার জীবন ও সময়, রঞ্জন গুপ্ত