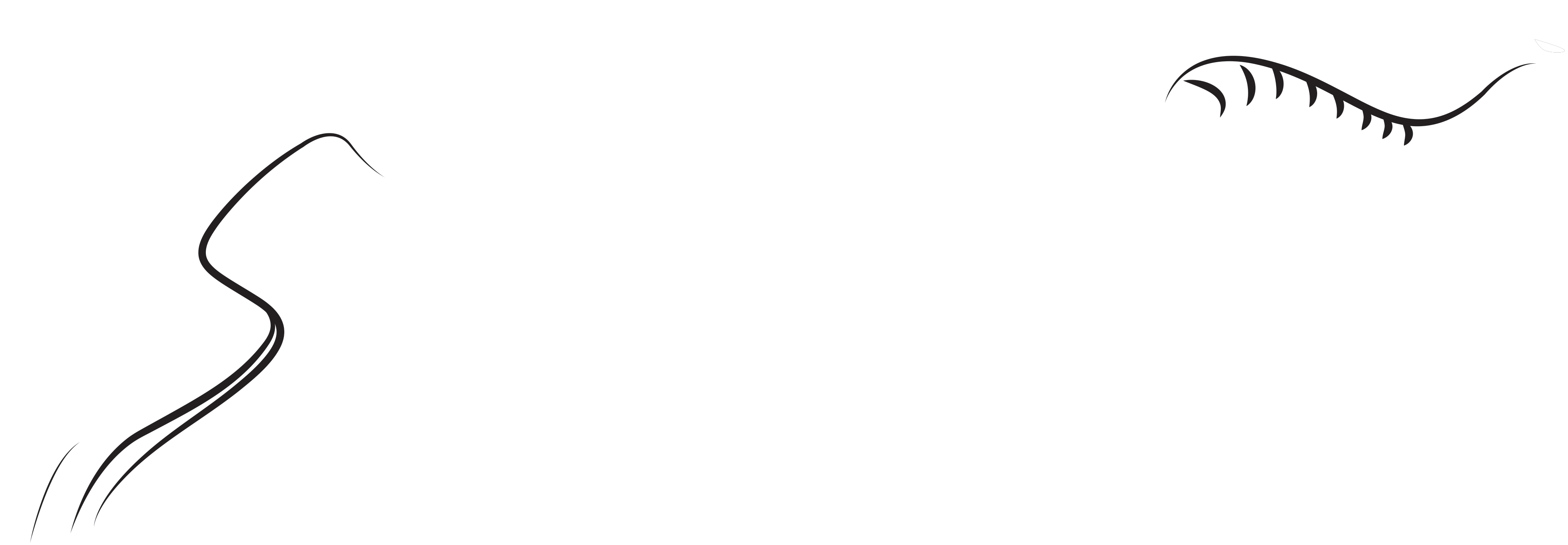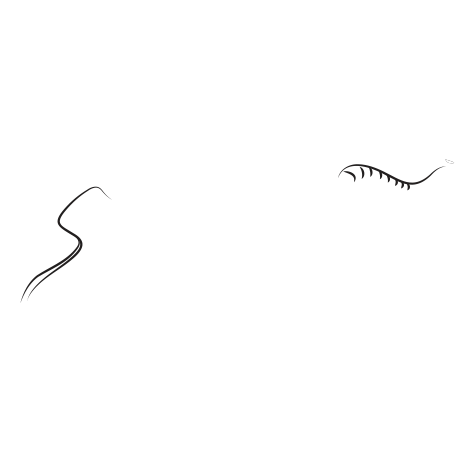১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। দেশব্যাপী চলছে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠায় মানুষজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়িঘর ছেড়ে ছুটছে অজানা গন্তব্যের দিকে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে সাধ্যমতো। শহর, বন্দর, স্টেশন, এমনকি গ্রাম থেকে গ্রামে সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাকিস্তানি সেনারা স্থাপন করছে তাদের ক্যাম্প। এমনি একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয় বর্তমান পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের বড়িবাড়ি গ্রামে, বড়িবাড়ি রেলব্রিজের নিচে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ থেকে রেলব্রিজটিকে রক্ষার জন্যেই হয়তো এই ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছিলো। জিনারদী ইউনিয়নের বরাব-বড়িবাড়িসহ আশেপাশের পুরো এলাকায় মূলত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিলো। হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনের খবর পেয়ে এলাকার মানুষ পরিবারসহ পালিয়ে যায়। জনশূন্য ভূতুড়ে এক জনপদে পরিণত হয় বড়িবাড়িসহ আশেপাশের গ্রামগুলো। কিন্তু পাক আর্মি ক্যাম্পেরই একদম কাছে একটি বাড়িতে রয়ে যান এক বিধবা নারী; তার এক ছেলেকে নিয়ে। দুই মেয়েকে পাঠিয়ে দেন শিবপুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি— সকলেই এলাকা ছেড়েছে। এদিকে বাড়িতে ধান থাকায় নিরুপায় হয়েই সেখানে রয়ে যান মা ও ছেলে। দূরের এক আত্মীয় নৌকাযোগে ধানগুলো নিতে এলেই তারাও সাথে চলে যাবেন, এই আশায় দিন কাটাচ্ছেন।
পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প স্থাপনের কারণে এলাকায় গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনাও বেড়ে যায়। আশেপাশের বাড়িঘরে মানুষজন না থাকায় স্বভাবতই মুক্তিযোদ্ধারা কোনো প্রয়োজন হলে সেই বিধবা নারীর বাড়িতে এসে উঠতেন। তাছাড়া তার বাড়ির পেছনের জঙলায় লুকিয়ে ক্যাম্পের সেনাদের গতিবিধি নজরে রাখা সহজ ছিলো। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরিবারটির একরকম সখ্য গড়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের রান্নাবান্না করে খাওয়াতেনও মাঝে-মধ্যে। পাশাপাশি পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন তথ্য এনে দিতেন। বাড়ির ছোটো ছেলেটিও নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।
হঠাৎ একদিন পাক হানাদার বাহিনীকে এসব কথা জানিয়ে দেন সিরাজুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক রাজাকার। এরপরই পাক হানাদার বাহিনী সেই নারীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। তিনদিনব্যাপী তার উপর চালায় অমানুষিক নির্যাতন। সেই সাথে গণধর্ষণ। নির্যাতনের তীব্রতা এতোটাই মারাত্মক ছিলো যে, তিনি একদম অচেতন হয়ে পড়েন। পাক বাহিনী মৃত ভেবে তাকে রেল লাইনের পাশেই একটি ডোবায় ফেলে দিয়ে যায়। কতো সময় পর তার জ্ঞান ফেরে, তা তিনি বলতে পারেন না। জ্ঞান ফিরলেও ডোবা থেকে উঠে আসার মতো শারীরিক শক্তি ছিলো না তার। রাতের অন্ধকারে হাতড়ে তা-ও ডোবা পার হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই পাড়ে উঠে আসতে পারছিলেন না। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা আগেই জেনে গিয়েছিলেন তার এই পরিণতির কথা। তারাও নানাভাবে তাকে উদ্ধারের জন্যে তৎপর ছিলেন। পরে মানিক সেন নামে এক মুক্তিযোদ্ধা তাকে সেই ডোবা থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার করে নিয়ে যান স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার ময়েশ চন্দ্রের কাছে। চিকিৎসা শেষে আশ্রয় নেন দুই-তিন কিলোমিটার দূরের গোপীরায়েরপাড়ায়, এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে চলে যান শিবপুরের আজকিতলায়, আরেক আত্মীয়ের বাড়ি। যুদ্ধের বাকি সময় সেখানেই অবস্থান করেন।
রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর অমানবিক এই ঘটনার শিকার সেই নারীর নাম বেদনা দত্ত। শরীরের নানা স্থানে স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন নিয়ে তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বাস করছেন সেই বড়িবাড়ি গ্রামের তার নিজ বাড়িতেই। বয়সের ভারে ন্যুব্জ নিপীড়িত এই নারীর জীবনের গল্প যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতা যুদ্ধে অজানা অনেক নারীর করুণ পরিণতি আর আত্মত্যাগের বিস্মৃত ইতিহাস।

বেদনা দত্তের জন্ম ঢাকার কদমতুলি থানা এলাকায়, ১৯৪০ সালে। তাঁর বাবা যোগেন্দ্র দে। ছোটোবেলায়ই বাবা-মাকে হারান তিনি। ১৫ বছর বয়সে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের বড়িবাড়ি গ্রামের এই বাড়িতে নরেন্দ্র দত্তের সাথে বিয়ে হয় তাঁর। সংসার জীবনে তাঁদের এক ছেলে— গোপাল দত্ত এবং দুই মেয়ে— জ্যোসনা দত্ত ও মল্লিকা দত্তের জন্ম হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে নরেন্দ্র দত্ত অসুস্থতাজনিত কারণে মারা যান ১৯৬৯ সালে। তিন সন্তান নিয়ে বিধবা বেদনা দত্ত মহাবিপদে পড়েন। তবুও কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়ে নিচ্ছিলেন সংসার।
এরই মধ্যে শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। শুরু হয় পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডব। শুরু হয় আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ। সেই সাথে পলাশের বড়িবাড়ি গ্রামে বেদনা দত্তের সাথে ঘটে যায় নির্মম সেই ঘটনা।
একসময় আমরা স্বাধীন হই। কিন্তু বেদনা দত্তের ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে সমাজের মানুষের কাছে তিনি অবহেলিত হতে থাকেন। মানুষের কটু কথা আর একঘরে করে রাখার তৎপরতায় বিষিয়ে ওঠে তাঁর জীবন। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধের সময় দুই বছর বয়সী শিশুকন্যা মল্লিকা দত্ত পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ফলে জন্ম নিয়েছে, এমন গুজবে আজো তাঁর বিয়ে দিতে পারেননি। ছেলে গোপাল দত্তই উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি। তিনি কৃষিকাজ ও গবাদিপশু পালন করেই সংসার চালাচ্ছিলেন।

এভাবেই দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যকে সাথে নিয়ে চলছিলো বেদনা দত্তের জীবন। ইতোমধ্যে কেটে গেছে স্বাধীনতার ৫০ বছর। মুক্তিযোদ্ধাসহ বীরাঙ্গনা নারীদের বহু তালিকা হয়েছে। তাঁদের সম্মাননা-ভাতা-বাড়িঘর দেয়া হয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে তাঁদের ফিরিয়ে আনার নানা তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন নানা সরকারসহ সমাজের কেউই বড়িবাড়ির বীরাঙ্গনা বেদনা দত্তের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসেনি।
তখন ২০২১ সাল। নরসিংদীর একজন সাংবাদিক শরীফ ইকবাল রাসেল (বাংলা টিভি) কোনোভাবে জানতে পারেন তাঁর সেই ঘটনা এবং করুণ জীবনযাপনের কথা। তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে খুঁজে বের করেন সুবিধাবঞ্চিত বেদনা দত্ত, তাঁর পরিবার ও বাড়িঘর। তিনি জানান, “প্রথম যেদিন বেদনা দত্তের বাড়ি আবিষ্কার করি, সেদিন বাড়ির উঠোনে উঠে দেখি, বেদনা দত্তের মেয়ে মল্লিকা দত্ত গ্রামের কোনো মাঠ থেকে কলমি তুলে এনেছেন। পাশেই চুলায় পানি গরম হচ্ছে। কলমি সিদ্ধ করে তাঁরা দুপুরে খাবে।” এই দুরাবস্থা, ভাঙা বেড়ার ঘর দেখে ও তাঁদের সাথে কথা বলে তিনি মর্মাহত হন এবং বেদনা দত্ত ও তাঁর পরিবারের হেন অবস্থা নিয়ে একের পর এক নিউজ করতে থাকেন। পাশাপাশি নিজেই প্রশাসনের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে নানা জায়গায় চেষ্টা-তদবির চালাতে থাকেন। অবশেষে তিনি ঊর্ধ্বতন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।
সমাজের প্রভাবশালীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অবহেলিত বেদনা দত্তকে অবশেষে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ‘বীরাঙ্গনা’ স্বীকৃতি দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগিদের হাতে নির্যাতিত হওয়ায় বীরাঙ্গনা বেদনা দত্তকে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট জারি করে তৎকালীন সরকার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) ৭৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীরাঙ্গনা বেদনা দত্ত এই স্বীকৃতি পান। তখনো পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা ২৭২ জন।
তখন থেকে সরকারি ভাতা এবং আরো পরে বাড়ি বরাদ্দ পান বেদনা দত্ত। কিন্তু ধীর গতির কাজ, ঠিকাদারদের অবহেলা আর নানা জটিলতায় বাড়ি নির্মাণ আটকে ছিলো দীর্ঘদিন। অবশেষে ২০২৩ সালে দুইটি শোবার ঘর, দুইটি টয়লেট, কিচেন, বসার ঘর ও বারান্দা সম্বলিত নবনির্মিত বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তিনি। বাড়িতে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ, পানি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হয়।
যুদ্ধের সময় মুক্তিরা আমগো বাড়িত আইতো। দিনে নানান জাগায় যাইতো। রাইতে খাওয়ার সময় অইলে আইতো। আমি রাইন্ধা-বাইড়া দিতাম। ভাত দিতাম, মাঝে-মইধ্যে রুটি বানায়া দিতাম। যন্ত্রপাতি আগায়া দিতাম। রেললাইনে ক্যাম্প করছিলো পাঞ্জাইব্যারা। এক রাজাকার আমার কথা তাগো কাছে কইয়া দিছে। বাড়িত আমি আর আমার ছেলে থাকতাম। বাড়ির ভিত্রে আইয়া আমারে ধরছে আর আমার পোলায় সামনেই পানি আছিলো, লাফ দিয়া পানিত পইড়া গেছে। তো আমারে লইয়া গেছে ক্যাম্পে। নিয়া আটকাইয়া রাখছে, লাত্থি দিছে, মাইরধর করছে ইচ্ছামতো। আর অত্যাচার করছে তিন-চাইর দিন ধইরা। আরো অনেক লোকে মিল্যাও অত্যাচার করছে।
বেদনা দত্ত ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানতে এবং স্বচক্ষে অবলোকন করতে আমরা যাই তাঁর বাড়িতে। চরনগরদী বাজার হয়ে বরাব মন্দির পেরিয়ে ছোটো একটি কালভার্টের পরেই হাতের বামদিকে চলে গেছে ছোট্টো পাকা সড়ক। সড়কটি বেদনা দত্তের বাড়ি পেরিয়ে একদম রেললাইন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে ‘বীরাঙ্গনা বেদনা দত্ত সড়ক’ নামে। জানতে পারি, তাঁর সম্মানেই বেহাল সড়কটি নতুন রূপ ধারণ করেছে। তবে এখনো সড়কের নামফলক বসানো হয়নি।
বাড়িতে ঢুকেই বেদনা দত্তকে দেখতে পাই। উঠোনে বসে আছেন মাথা নিচু করে। ৮৫ বছর বয়স্ক বীরাঙ্গনা এই নারী অনেকটাই অসুস্থ এখন। সোজা হয়ে চলতে পারেন না। তাঁর পুত্র গোপাল দত্তের স্ত্রী স্বর্ণা দত্ত ও মেয়ে রাখি দত্ত চেয়ার পেঁতে আমাদের বসতে দেন। আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রহণ করায় শুরু থেকেই আমরা আলাপে ঢুকে পড়ি। বেদনা দত্তের বয়স্ক কণ্ঠ আমাদের ইতিহাসের গভীরে নিবদ্ধ রাখে অনেকক্ষণ। আমাদের জানান একাত্তর সালের ভাদ্র মাসে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া অমানবিক ঘটনার নির্যাস। তবে অসুস্থ থাকায় খুব বেশিক্ষণ বলতে পারলেন না। তিনি বলেন, “যুদ্ধের সময় মুক্তিরা আমগো বাড়িত আইতো। দিনে নানান জাগায় যাইতো। রাইতে খাওয়ার সময় অইলে আইতো। আমি রাইন্ধা-বাইড়া দিতাম। ভাত দিতাম, মাঝে-মইধ্যে রুটি বানায়া দিতাম। যন্ত্রপাতি আগায়া দিতাম। রেললাইনে ক্যাম্প করছিলো পাঞ্জাইব্যারা। এক রাজাকার আমার কথা তাগো কাছে কইয়া দিছে। বাড়িত আমি আর আমার ছেলে থাকতাম। বাড়ির ভিত্রে আইয়া আমারে ধরছে আর আমার পোলায় সামনেই পানি আছিলো, লাফ দিয়া পানিত পইড়া গেছে। তো আমারে লইয়া গেছে ক্যাম্পে। নিয়া আটকাইয়া রাখছে, লাত্থি দিছে, মাইরধর করছে ইচ্ছামতো। আর অত্যাচার করছে তিন-চাইর দিন ধইরা। আরো অনেক লোকে মিল্যাও অত্যাচার করছে। কোনো খাওয়া-দাওয়া আছিলো না। কতো আর সহ্য করমু? পরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ছি। হ্যারা মনে করছে, আমি মনে হয় মইরা গেছি নাকি কী চিন্তা কইরা আমারে লাইনের পাড় ফালায়া দিছে। আমার যহন কিছু জ্ঞান আইছে, তহন ভোর রাইত। আমি পলাইতে গিয়া খালের এই পাড় আইছি কোনোমতে। পরে মুক্তিরা দেখছে। পরে আমারে তুলছে। তুইল্যা ডাক্তরের কাছে নিছে। পরে আমি শিবপুর গেছিগা। স্বাধীনের পরে আবার বাইত আইছি।”
যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রতি পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, “এহনো মানুষ আমারে নিয়া নানান কথা কয়। আমার একটা মাইয়্যা আছে, বিয়া দিতারি নাই তো। মাইনষের আজগুবি কথায় আমার মাইয়্যাডার বিয়া অইছে না।”

সমাজের এমন নিগ্রহে রাগ-দুঃখ প্রকাশ করলেও শেষে তিনি জানান যে, তাঁর আত্মত্যাগ আর সন্তানদের দুর্গতির বিনিময়ে হলেও এই দেশের মানুষ যে মুক্ত হয়েছে, সেই কারণে তিনি গর্ববোধ করেন।
বেদনা দত্তের বিচলিত কণ্ঠ নেমে আসে ধীরে ধীরে। আমরা অপেক্ষা করি গোপাল দত্ত ও মল্লিকা দত্তের জন্যে। তাঁরা পারিবারিক কাজে জিনারদী বাজারে অবস্থান করছিলেন। ততোক্ষণে রেললাইনসহ আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখি। স্বচক্ষে দেখে আসি বড়িবাড়ি রেলব্রিজ ও পাকিস্তান আর্মির ক্যাম্প স্থাপনের জায়গাটি। ঘণ্টাখানেক পর দুই ভাই-বোন একসাথে এসে হাজির হন বাড়িতে। তাঁদের সাথে কথা বলে জানতে পারি একাত্তরসহ পরবর্তী আরো নানা ঘটনা। যুদ্ধের সময় গোপাল দত্তের বয়স ছিলো ১২, তাঁর বোন জ্যোসনা দত্তের ৮ এবং মল্লিকা দত্তের ২। অল্প বয়সে দেখা যুদ্ধ ও তাঁর পরিবারের দুর্দশার কথা আমাদের বর্ণনা করেন গোপাল দত্ত। সেই সাথে যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন দেশে সামাজিক নিগ্রহ ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “যুদ্ধের পরে যহন বাড়িতে আসি, আইসা দেখি যে, বাড়ির চারপাশে বড়ো বড়ো ঘাস। বেড়া বিভিন্ন দিক দিয়া ভাঙ্গা, কিন্তু বাড়িটা পাইছি। …আর এলাকার মানুষও ফেরত আইছে। সবাই ঘটনাটা জানছে। এলাকায় আমার মায়ের নামে অনেক বদনাম ছড়াইয়া যায়। কেউ কিছু হইলেই কইতো, তোর মারে পাকিস্তানিরা ধইরা নিছে, এই করছে সেই করছে। আমার খারাপ লাগতো অনেক। কিন্তু কিছু কইতে পারতাম না। তবে এহন কেউ আর আগের মতো করে না। ’২১ সালে সম্মানটা পাওয়ার পরে আর কেউ কিছু কয় না।”
স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হলেও তাঁরা কেন এতোদিন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে জানান, “আমরা আসলে সরকারি ভাতা সম্পর্কে এতোটা জানতাম না। জানতাম, খালি মুক্তিযোদ্ধাগোরে ভাতা দেয়। আর কেউ কোনো-সময় আমগোরে কিছু কয়ও নাই। চার-পাঁচ বছর আগে নসন্দী থেকে এক সাংবাদিক আইয়া আমগোর খোঁজ-খবর নেয়। উনিই আমগোরে বীরাঙ্গনা উপাধির কথা জানায়, ভাতার কথা জানায়। পরে পলাশ উপজেলা পরিষদ আর ঢাকা দৌড়াদৌড়ি কইরা কাজটা করি। উপজেলা অফিসারও অনেকবার বাড়িত আইয়া দেইখ্যা ছবি-টবি তুইল্যা নিছে। তো এইভাবেই আসলে সব হইছে।”
গোপাল দত্ত তাঁর মায়ের আত্মত্যাগ নিয়ে গর্ব করেন এবং আমাদের অর্জিত স্বাধীনতাকে সবার উপরে স্থান দেয়ার কথা বলেন। সবশেষে তাঁদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্ক তিনি বলেন, “সরকারি যেই ভাতা পাই, সেইটা আমার মা আর বোনের পিছেই খরচ করি। নতুন বাড়িতেও তারা দুইজনেই থাকে। আমরা এই আগের ঘরেই থাকি। এক মেয়ে, এক ছেলে, আমি আর আমার বউ— আমরা চারজন। ছেলে-মেয়ে দুইজনই পড়ালেখা করে। আমি আগে কৃষিকাজ করতাম। কিন্তু এহন শ্বাসকষ্টের কারণে তেমন কোনো কাজ করতে পারি না। আমার একটা গাভী আছে, এটার দুধ বিক্রির টাকা দিয়াই কষ্ট করে চলতেছি।”
বীরাঙ্গনা বেদনা দত্ত ও তাঁর সন্তানদের এই ত্যাগ ও দুর্দশার চিত্র আমাদের ইতিহাস ও মানসপট থেকে কখনোই হারিয়ে যাবার নয়। অন্ধকারে তাঁরাই আমাদের আলোকরেখা। আমাদের উচিত, ইতিহাসের ধুলোর আস্তরণ মুছে এরকম আত্মত্যাগী চরিত্রদের খুঁজে বের করা এবং তরুণ প্রজন্মের সামনে দেশ গড়ার পাথেয় হিসেবে সর্বদা হাজির রাখা। তাহলেই অর্ধশত বছর ধরে বেদনা দত্তদের ভুলে থাকার দায় হয়তো-বা ঘুচবে, কিছুটা হলেও।
তথ্যসূত্র
১. বেদনা দত্ত, গোপাল দত্ত ও মল্লিকা দত্তের সাক্ষাতকার;
২. সাংবাদিক শরীফ ইকবাল রাসেলের সাক্ষাতকার;
৩. ‘প্রতিদিনের সংবাদ’ ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক।