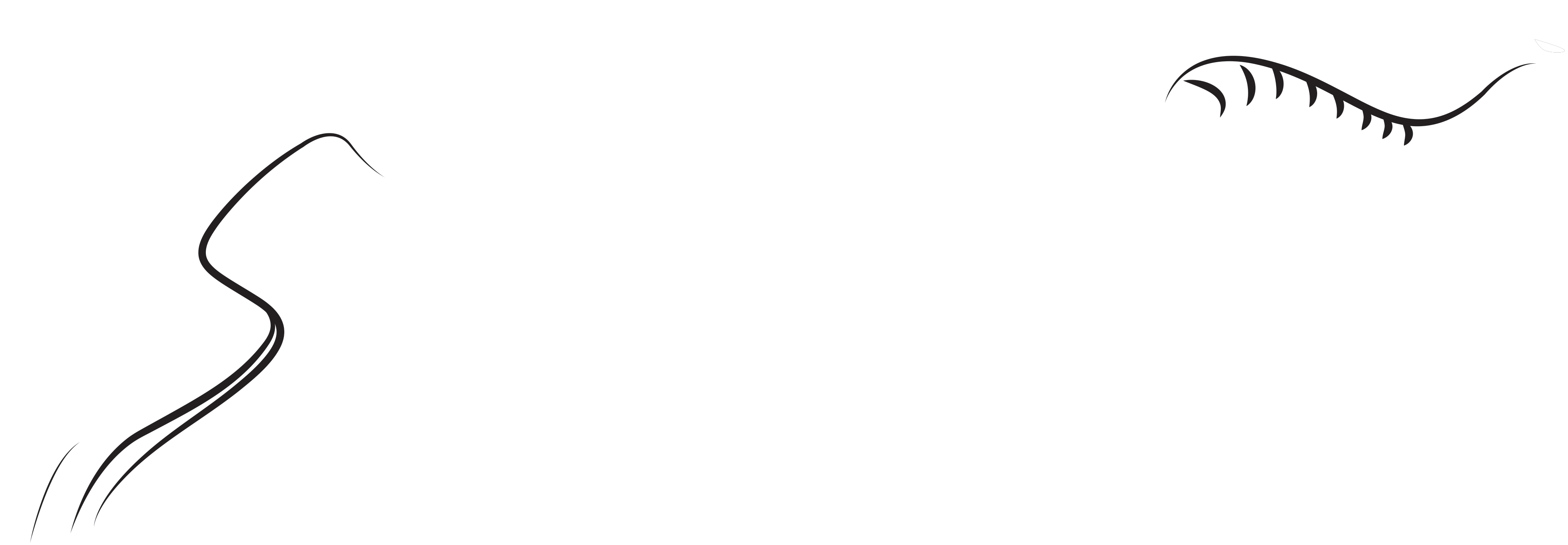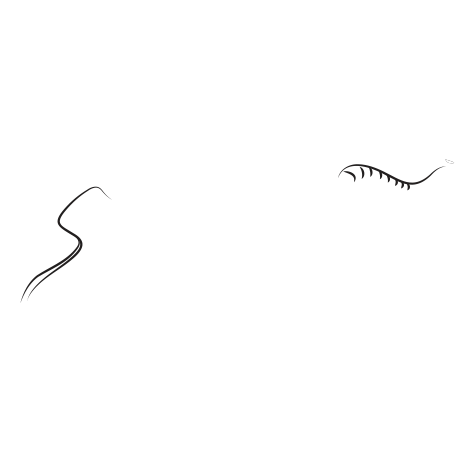বস্ত্রশিল্পের প্রাণকেন্দ্র হলো নরসিংদী। দেশের অন্যতম ধনাঢ্য জেলার তালিকায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে জনপদটি। মসলিন-জামদানির ঐতিহ্য বুকে ধারণ করা নরসিংদী আধুনিককালে বস্ত্রশিল্পে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মেঘনা, হাড়িধোয়া, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, বানার, কয়রা, কলাগাছিয়া ও শীতলক্ষ্যা নদ-নদী বিধৌত জেলাটির পথচলা শুরু হয়েছিলো সামান্য একটি গঞ্জ হিসেবে। পরবর্তীতে একটি ঐতিহাসিক ও সমৃদ্ধ নদীবন্দরে পরিণত হয় গঞ্জটি। আর এর নেপথ্য কারিগর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সাটিরপাড়ার জমিদার, বিদ্যোৎসাহী, প্রজাহিতৈষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ললিতমোহন রায় বিএবিএল। মূলত এই মনীষীতুল্য জমিদারের সমৃদ্ধির সাথে সাথে হেঁটেছে নরসিংদী। তাঁর উন্নয়নের হাত ধরেই এলাকার যতো সাফল্য। আজকে জেলার অবকাঠামো নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে যে-নরসিংদী এগিয়ে যাচ্ছে, তার প্রকৃত রূপকার হলেন ললিতমোহন রায়। কীর্তিগাঁথার হিসেবে নরসিংদীর নামকরণ হওয়া উচিত ছিলো ‘ললিতনগর’। আজকের জেলা শহরটি, তৎসময়ের নদীর তীরবর্তী গ্রামটি নানা পাড়ায় বিভক্ত ছিলো। পাড়াগুলোর নাম ছিলো সাটিরপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কৈবর্তপাড়া প্রভৃতি। আর গ্রামটির নাম ছিলো নরসিংহদী। কালের বিবর্তনে নরসিংহদী শব্দ থেকে ‘হ’ হরফটি বিচ্ছিন্ন হয়ে নাম হয়েছে নরসিংদী।
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে নরসিংদীর খ্যাতি সর্বত্র। বস্ত্রশিল্পের সবচেয়ে বড়ো মোকাম বাবুরহাটের কারণে জেলাটি প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এর শুরুটা কিন্তু হয়েছিলো একটি ছোটো গঞ্জ হিসেবে। মেঘনা-হাড়িধোয়ার মিলনস্থলের কাছে জেলে-মাঝিতে আনাগোনা হতো। সেখানে সীমিত আকারে মাছ, তরি-তরকারি, পেঁয়াজ-রসুন, চাল-ডাল বেচাকেনা হতো। মাঝে-মধ্যে মালবোঝাই নৌকা ভিড়তো সেই গঞ্জে। তা থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্যে নদীর তীরে ছোটো একটি রাজস্ব আদায় কেন্দ্র (কোতঘর) স্থাপন করা হয়। লোক-সমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। তখন উক্ত এলাকার জমিদারির বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার পাল। তিনি ছোটো-খাটো জমিদার হিসেবে নরসিংদী এলাকা থেকে খাজনা আদায় করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে কালী কুমার পাল জমিদারি বন্দোবস্ত নেন। তিনিই সাটিরপাড়ায় জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন। তখন নরসিংদী পশ্চিমের এলাকাটি ঝোপ-জঙ্গলে ভরপুর ছিলো। জমিদার বাড়ির প্রয়োজনে আশেপাশে ধোপা, নাপিত, দাস, কৈবর্তদের জন্যে ৬০ টি বাড়ির জন্যে নিষ্কর ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। যার মাধ্যমে সেখানে ‘ষাটেরপাড়া’ গড়ে ওঠে। এই ‘ষাট’ শব্দটি পরবর্তীতে সাটিরপাড়া হয়ে যায়। এখনো জমিদার বাড়ির পাশে শীল বাড়ি, দাস বাড়ির অস্তিত্ব রয়েছে। মূলত জমিদার বাড়ি গড়ে ওঠার পরই নরসিংদী জনপদ চারদিকে প্রশস্ত হতে থাকে। এই পাল জমিদার বংশের কীর্তিমান পুরুষ হলেন ললিতমোহন রায়।
জমিদার কালী কুমার পাল তাঁর সন্তানকে ঢাকা-কলকাতা থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত করার সব রকম চেষ্টা-তদবীর করেন। সফলও হন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন ললিতমোহন। তিনি নিজ যোগ্যতায় জমিদারি এস্টেট বৃদ্ধিসহ অনেক জনহিতকর কাজ করেন। একজন প্রজাহিতৈষী জমিদাররূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। নিজ জমিদারিকে গড়ে তোলার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রজাদের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে তিনি নরসিংদীকে একটি পূর্ণাঙ্গ গঞ্জ বা বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বাবা কালী কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনা-হাড়িধোয়ার পাড়ের ছোটো হাটটিকে ‘গঞ্জ’ হিসেবে ঘোষণা করেন। কালী কুমার তার নামকরণ করেন ‘কৃষ্ণগঞ্জ বাজার’। মূলত তখন থেকেই এলাকাটির সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে পথচলা শুরু হয়। যেখানে পরবর্তীতে বিশাল বাজার ও নরসিংদী নদীবন্দর গড়ে ওঠে। তখন কৃষ্ণগঞ্জ বাজার দ্রুত প্রসার লাভ করলেও তা ছিলো ৪০ মাইল দূরবর্তী রূপগঞ্জ থানার অধীনে। মেঘনা নদীর পূর্ব তীরের এলাকা ছিলো ত্রিপুরার বরদাখাল পরগণার আওতাধীন। তাই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্যে জমিদার ললিতমোহন রায় নদীর তীরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। উপর মহলে তদবির করে তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সফল হন। বর্তমান নৌ-পুলিশ কার্যালয় ছিলো নরসিংদীর পুলিশ ফাঁড়ি। তখনো থানার কার্যক্রম পরিচালিত হতো রূপগঞ্জ থেকে। অপরদিকে পলাশ-ঘোড়াশাল ছিলো কালীগঞ্জ থানার অধীনে। সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ছিলো রূপগঞ্জ ও কালীগঞ্জ। এতে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হতো। নরসিংদীর লোকজনদের প্রশাসনিক কাজে নানা স্থানে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো। এটি অনুভব করে ললিতবাবু ফাঁড়িটি থানা হিসেবে উত্তীর্ণকরণের জন্যে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন মহলে জোর প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নরসিংদীকে একটি থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটান। এরই ধারাবাহিকতায় থানা শহরটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে বর্তমানে নরসিংদী জেলা একটি গুরত্বপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়েছে। বস্ত্রশিল্প ও খাদ্য-শস্য উৎপাদনে শীর্ষ জেলা হিসেবে নরসিংদী এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় নৌ-পথ ছাড়া যোগাযোগের বিকল্প মাধ্যম ছিলো না। শুধু নরসিংদীরই নয়, পার্শ্ববর্তী নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর প্রভৃতি এলাকার লোকজন নৌ-যানে নরসিংদী এসে কেনাকাটা করতেন। অনেকে রেলপথে ঢাকা-কলকাতা যেতেন। ঠিক তখনই জমিদার ললিতমোহন রায় নরসিংদীর সঙ্গে স্থলপথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের চিন্তা-ভাবনা করলেন। তৈরি করলেন নরসিংদী-পাঁচদোনা-মাধবদী-পুরিন্দা-পাচরুখী-ভূলতা-ডেমরা কাঁচা সড়ক, যার উপর পরবর্তীতে ঢাকা-নরসিংদী পাকা সড়ক প্রতিষ্ঠিত হয়। চল্লিশের দশকে সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ভাড়া নিয়ে ঢাকার মোমিন মটরস কোম্পানি ইটের পাকা রাস্তা তৈরি করে নরসিংদী থেকে বাবুরহাট হয়ে তারাব পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করে, যা ছিলো এ-অঞ্চলের প্রথম বাস সার্ভিস। অবশ্য জমিদার ললিতমোহন রায় এই সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।
নরসিংদী বর্তমানে শিল্পনগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ললিতবাবু যখন জমিদার, তখন নরসিংদী হ্যান্ডলুম বা ঠকঠকি তাঁতের কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত হলেও তা ছিলো কুটির শিল্প পর্যায়ে। তবে এর আধিক্য ছিলো পাঁচদোনা, আমদিয়া, ডাঙ্গা, মেহেরপাড়া, শেখেরচর, মাধবদী, বালুসাইর, আলগী প্রভৃতি এলাকায়। এই হ্যান্ডলুম তাঁতশিল্প ঘিরে প্রথমে মাধবদী এবং পরে বাবুরহাট কাপড়ের হাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয় লোকজন কৃষিকাজের পাশাপাশি তাঁত বোনার কাজ করতেন। শাড়ি, লুঙি, চাদর, গামছা ও থান কাপড়ের মধ্যেই তাঁতীদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকতো। কৃষকেরা বসতঘরের পাশে ছোটো করে একটি তাঁতঘর গড়ে তুলতেন।
এখন নরসিংদী অঞ্চলে অসংখ্য শিল্প-কারখানা ও মিল-ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠেছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, নরসিংদীর প্রথম মিল-কারখানার জনক কে? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়েও পাওয়া গেছে জমিদার ললিতমোহন রায়ের নাম। তিনি সাটিরপাড়া কালী কুমার ইনস্টিটিউশনের পূর্বপাশে একটি চিনির মিল প্রতিষ্ঠা করেন তিরিশের দশকে। তা পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন বড়ো ছেলে নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়কে। তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি চিনিকলের দেখাশোনাও করতেন। এই কারণে অনেকে মনে করতেন, মিলটির মালিক নৃপেন্দ্র রায়। আসলে সাটিরপাড়ার জমিদার পরিবারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন ললিতবাবু। তিনি যেহেতু পেশাগত কারণে ঢাকা-কলকাতায় ব্যস্ত থাকতেন, তাই জমিদারি বলেন আর সুগার মিল বলেন, তা নৃপেন্দ্র ওরফে বঙ্গবাবু পরিচালনা করতেন। মূলত ব্রিটিশদের কারখানায় উৎপাদিত চিনি বর্জনের জন্যেই তিনি চিনিকলটি নরসিংদীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিনিকল প্রতিষ্ঠার আরেকটি কারণ ছিলো। সে-সময় নরসিংদী অঞ্চল তথা মহেশ্বরদী পরগণা আখ চাষের জন্যে বিখ্যাত ছিলো। এখানকার আখের তৈরি গুড় ছিলো বিশ্ববিখ্যাত। তাই সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত চিনি উৎপাদনের জন্যে তিনি নিজ জমিদারি এস্টেটে মিলটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কয়েক বছর চলার পর মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন পরিত্যক্ত মিলের জায়গায় ললিতবাবু তাঁর মা কমল কামিনী দেবীর নামে একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নরসিংদীতে নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

স্বদেশি উদ্যোগ শুধু এটাই প্রথম ছিলো না। তিনি জাহাজ কোম্পানি খুলেছিলেন। মানুষ যাতে ব্রিটিশ বেনিয়াদের স্টিমার ব্যবহার না করে, সেজন্যে প্রচারণাও চালাতেন। আর ভারতবর্ষের প্রথম বৈদ্যুতিক ল্যাম্প কোম্পানি খুলে ললিতমোহন অমরত্ব লাভ করেছেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন ললিতমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠজন। তাই তিনি একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, “আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কবে স্বদেশি মিল-ফ্যাক্টরি তৈরি করবে?” সঙ্গে সঙ্গে ললিতবাবু বললেন, তিনি এই উদ্যোগ নেবেন। আমেরিকা ও জার্মান থেকে পাশ করে আসা দুই ইঞ্জিনিয়ার পুত্রকে বেঙ্গল ল্যাম্পস নামে কারখানা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। তখন ইউরোপের মালিকানাধীন ফিলিপস বাল্বে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে গিয়েছে। সেই বাল্বকে পেছনে ফেলে একচ্ছত্র বাজার দখল করে নেয় স্বদেশি বেঙ্গল ল্যাম্পস। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে নরসিংদীর স্বদেশি জমিদার ললিতবাবুর নাম-যশ।
আজকের যুগে মিথ্যা হিসেবে প্রচারিত হয়, অতীতে প্রজারা জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে দিয়ে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে চলাফেরা করতে পারতো না। খাজনা অনাদায়ে প্রজাদের ধরে এনে শারীরিক নির্যাতন করতো। বাইজি নৃত্য, মদ্যপান, গান-বাজনার জলসা তো জমিদারদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু সাটিরপাড়ার রায় জমিদারেরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইজি নাচ বা গান-বাজনার পরিবর্তে সেখানে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা হতো। প্রজা নিপীড়নের জায়গায় বিধবা বিবাহ ও জাতপাত বিরোধী কর্মকাণ্ড চলতো। খাজনা দিতে না পারলে প্রজাদের নির্যাতন তো করা হতোই না, বরং অসহায় প্রজাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হতো। একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি, যা ‘নরসিংদীর গুণীজন’ বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
আনুমানিক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। মনোহরদীতে খাজনা অপরিশোধের জন্যে এক বিধবা নারীর জমি নিলামে তোলা হয় স্থানীয় নায়েবের কারসাজিতে। তখন সেই বিধবা দুই শিশুপুত্র নিয়ে মনোহরদী থেকে হেঁটে ২২ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সাটিরপাড়ার রায় জমিদার বাড়িতে হাজির হয়। তাদের কান্নাকাটি দেখে জমিদার বাড়ির মেয়েরা বাইরে এসে তাদের ভেতরে নিয়ে সান্ত্বনা দেন এবং আদর করে খাওয়া-দাওয়া করান। জমিদারবাবু বাড়িতে এসে তাদেরকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। পরে বিধবার পক্ষে জমিদারবাবু নিলামের বিপক্ষে আপিল করেন নিজ খরচে। তখন সেই বিধবা জমি ফেরত পান। এমন প্রজাদরদী এবং মানবিক জমিদার ছিলেন তারা। জমিদার বাড়ির এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত ছিলো। বিধবাদের প্রতি জমিদারেরা অত্যন্ত সহায় ছিলেন। অনেকেই অল্প বয়সে বিধবা হতো। সমাজে তারা ছিলো অপয়া। নানা অপবাদ ও অপমান সহ্য করে জীবনযাপন করতো। পুনর্বিবাহ করার অনুমতি পেতো না। কিন্তু ললিতমোহন রায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাল্যবিধবাদের এনে জমিদার বাড়িতে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বিয়ে দিয়ে তাদের সুখী-সুন্দর জীবন উপহার দিতেন। তিনি এমন জমিদার ছিলেন, যিনি নিজ এলকার মেথর, মুচি, কৈবর্ত, দাসদের সঙ্গে এক থালায় খেয়ে প্রমাণ করতেন, মানুষের মধ্যে কোনো জাত-পাত নেই। সবাই ঈশ্বরের কাছে সমান। সমাজে জাত-পাত সৃষ্টি করেছে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল।
অতীতে নরসিংদীর চরাঞ্চল ও রায়পুরা সদর থানার কিয়দংশ অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিলো। মারামারি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এমনকি খুনোখুনিতে নিত্যদিন লেগেই থাকতো। এ-কারণে জেল-জরিমানা ও মামলা-মোকদ্দমায় সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হতো সবসময়। তা দেখে জমিদার ললিতমোহন রায় বেশ ব্যথিত হতেন। লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য মানুষ মামলায় পড়ে সর্বশান্ত হতো। কীভাবে তাদের রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তা-ভাবনা করতেন। তার চেম্বারে নরসিংদীর তথা মহেশ্বরদী পরগণার অনেক মক্কেল যেতো। ললিতবাবু তাদের মামলা করার জন্যে নিরুৎসাহিত করতেন। অনেক মামলা দুই পক্ষের অনুমতি নিয়ে মীমাংসা করে দিতেন। গরীব-অসহায় মক্কেলদের সুবিচারের জন্যে বিনা পয়সায় মামলা লড়ে যেতেন। আইনজীবী পেশার বিরোধী আদর্শ হলেও শুধুমাত্র মানবিক কারণে তিনি এসব পদক্ষেপ নিতেন। তিনি যখন দেখতেন, অনেক গরীব মক্কেল ফি দিতে না পেরে তাঁর কাছে হাঁস-মুরগী কিংবা শাক-সবজি নিয়ে এসেছে, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠতো।
মহকুমা শহর হিসেবে নারায়ণগঞ্জ ও জেলা শহর হিসেবে ঢাকায় চেম্বার ছিলো ললিতবাবুর। এসব চেম্বার মক্কেলে ভরে যেতো। সৎ, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে তিনি মক্কেলদের জিতিয়ে আনতেন। তাঁর প্রতি মক্কেলদের অগাধ বিশ্বাস জন্মেছিলো। তারা মনে করতো, ললিতবাবু যখন কেস হাতে নিয়েছেন, তখন অবশ্যই জিতবেন। অনেক মক্কেলেরই ঢাকায় থাকার জায়গা ছিলো না। তখন আবাসিক হোটেলের আইডিয়া আসেনি। মেস বা সরাইখানায় থাকার ব্যবস্থা ছিলো। এমনসব মক্কেলদের রাত্রি যাপনের জন্যে তিনি নিজ চেম্বার ছেড়ে দিতেন। ঘনিষ্ঠ মক্কেলদের তিনি লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি এমন প্রজাহিতৈষী স্বভাবটা পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে। অনেক মামলায় দেশবন্ধুর সঙ্গে মামলা পরিচালনা করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধু অর্থের জন্যে উকালতি করলে মানবতা হারিয়ে যাবে। সাধারণ মক্কেলরা সুবিচার পাবে না। এজন্যে তিনি অন্তত ৪০ ভাগ মামলা পরিচালনা করতেন সহযোগিতা আর মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, আইন পেশার মাধ্যমেও দেশসেবা করা যায়, এটা প্রমাণের জন্যে তিনি কলকাতা থেকে বিএবিএল পাশ করেও কলকাতা হাইকোর্টে থিতু হননি। জন্মভূমির মক্কেলদের আইনি সহযোগিতা দেয়ার জন্যে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জন্মভূমিতেই মানুষের সেবা করে গেছেন। তাঁর কাছে এসে সহযোগিতা পাননি, এমন নজির ছিলো না। তাঁর মতো নিঃস্বার্থ ও দরদী একজন প্রশাসক ও মানুষ অন্তত নরসিংদীর ইতিহাসে খুব কমই এসেছে।
আপেল মাহমুদ
সাংবাদিক, গবেষক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক