লোকসঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ভাটির দেশ নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের একটা কৌতূহল ছিলো। সেই কৌতূহলটা যে এখন আমার মিটে গেছে, তেমন নয়। তবে একটা প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি সেখানকার লোকসঙ্গীতের কয়েকজন কিংবদন্তীর জবানবন্দী থেকে। ভাটির দেশ খ্যাত সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের কিয়দংশ ঘিরে এতো সমৃদ্ধ কবি-মালজোড়া গান, বাউল, জারি-সারি, ভাটিয়ালি ও বিচ্ছেদ গানের উর্বরভূমি কীভাবে গড়ে ওঠলো? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি অবিভক্ত বাংলার লোকসঙ্গীতের কিংবদন্তী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের (১৯১২-১৯৮৭) লেখা ‘উজান গাঙ বাইয়া’ গ্রন্থটি সংগ্রহ করি। বইটি পড়ে জানতে পারি, তাঁর সঙ্গীতের মূল অনুপ্রেরণা হলেন পাগল দ্বিজদাস ও তাঁর শিষ্য হরিচরণ আচার্য্য। তাঁদের কবিগান শুনে ছেলেবেলায় তিনি মাতোয়ারা হয়ে ওঠেছিলেন। তাঁদের গানে বুঁদ হওয়ার পথ থেকে আমৃত্যু ফিরতে পারেননি।
তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, খুব ছোটোবেলায় পূজা ছিলো তাঁর আনন্দের অন্যতম সঙ্গী। সে-সময় তাঁদের জমিদার বাড়ির নাটমন্দিরে পাগল দ্বিজদাস আর হরিচরণ আচার্য্যরে কবিগান ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। কবিয়ালরা পানসি নৌকায় চড়ে পূজার সময় তাঁদের বাড়িতে এসে গান গাইতেন। দোহারা-নট্ট সহকারে তারা যখন বাড়িতে আসতেন, তখন পুরো হবিগঞ্জ জুড়ে হৈচৈ পড়ে যেতো। হাজার হাজার মানুষ কবিগান শুনতে আসতেন। এদের শিডিউল ঠিক রাখার জন্যে পূর্ব থেকেই জমিদার হরকুমার বিশ্বাস বায়না করে রাখতেন।
কবিয়াল দ্বিজদাস ছিলেন একজন তাত্ত্বিক ব্যক্তি। তিনি গান গাওয়ার চেয়ে কবিগান রচনা, কবির জবাব, টপ্পা প্রভৃতি রচনায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রচ্ছন্ন কবি হিসেবে গানের আসরে তিনি অনেক টপ্পা, গান মুখে মুখে রচনা করে দিতেন। তিনি যার পক্ষে থাকতেন, সেই কবিয়াল গানের আসর মাত করতে পারতেন। যার কারণে অবিভক্ত বাংলায় তাঁর কদর ছিলো সবচেয়ে বেশি। অনেক কবিয়াল দিনের পর দিন তাঁর কাছে বসে থাকতেন গান কিংবা টপ্পা লিখে নেয়ার জন্যে। বাস্তবে দেখা গেছে, যে-কবিয়াল যতো বেশি দ্বিজদাসের কাছ থেকে টপ্পা ও গান লিখিয়ে নিতে পারতেন, তিনি গানের আসর ততো মাত করতে পারতেন। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হলেন অবিভক্ত বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল হরিচরণ আচার্য্য কবিগুণাকর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি নিজে একজন প্রতিভাবান ও দক্ষ কবিয়াল ছিলেন। এর সঙ্গে গানের গুরু দ্বিজদাসের লেখা গান, জবাব ও টপ্পা যোগ করে তিনি প্রতিটি আসর মাতিয়ে তুলতেন। ডাকছড়া গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করে নিতেন।
পাগল দ্বিজদাস নিয়ে বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯) চমৎকার একটা মূল্যায়ন করেছেন। সিলেটের খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লোকগবেষক সুমন কুমার দাশ ভাটির লোকসঙ্গীত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন। এই সংক্রান্ত তাঁর অনেকগুলো গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। দ্বিজদাসের গান নিয়েও তাঁর গবেষণা রয়েছে। সেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, শাহ আবদুল করিম পাগল দ্বিজদাসের গানের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত জীবনে দ্বিজদাসের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গান গেয়ে আসর জমাতেন। ভাটির দেশের বিভিন্ন স্থানে পাগল দ্বিজদাসের অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী সঙ্গীতের প্রভাব ছিলো প্রকট। তাঁর লেখা গান ছিলো দর্শক-শ্রোতাদের কাছে লোভনীয়। ভাটির দেশে কোথাও তাঁর গান হলে নানা স্থান থেকে সেখানে হাজার হাজার দর্শক হাজির হতেন। সেটা আর কোনো কবিয়াল বা শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। শাহ আবদুল করিম গান রচনার আগে, শিল্পী জীবনের প্রথমদিকে, দ্বিজদাসের গান গেয়ে গ্রাম্য আসর থেকে শুরু করে সারস্বত সমাজ মাত করেছিলেন। শাহ করিমের উত্থানের পেছনে দ্বিজদাসের গান যে জাদুর মতো কাজ করেছিলো, সেটা করিম বিভিন্ন আলোচনা, বিতর্ক কিংবা সাক্ষাতকারে নির্মোহভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।
ভাটির দেশের আরেক কালজয়ী সঙ্গীতজ্ঞ দূরবীন শাহ (১৯২০-১৯৭৭) ছিলেন পাগল দ্বিজদাসের গানের অনুরক্ত। তিনিও শাহ করিমের মতো বিভিন্ন আসরে দ্বিজদাসের গান গাইতেন। তাঁর গান গাইতে গাইতেই দূরবীন শাহ একসময় বাউল সাধক হয়ে ওঠেন। দূরবীনের ছেলে আলম শাহ সুমন কুমার দাশের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, তাঁর বাবা পাগল দ্বিজদাসের অনুসারী ছিলেন। দ্বিজদাসের গান তাঁর নমস্য ছিলো। তাঁর গানের খাতায় নিজ হাতে দ্বিজদাসের কিছু গান লিখে রেখেছিলেন। তিনি পাগল দ্বিজদাসকে গানের মুর্শিদ হিসেবে গণ্য করতেন।
মালজোড়া গানের জন্ম ভাটির দেশ নেত্রকোণা ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন বাউল ও লোকসঙ্গীত শিল্পীদের মাধ্যমে। শুধু সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলেই নয়, নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ এলাকায় মালজোড়া গানের যে-প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেখানেও পাগল দ্বিজদাসের প্রভাব প্রকট ছিলো। সেখানকার কিংবদন্তীতুল্য বাউল রশিদ উদ্দিন (১৮৮৯-১৯৬৪), উকিল মুন্সি (১৮৮৫-১৯৭৮) ও জালাল খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২) প্রমুখ ছিলেন পাগল দ্বিজদাসের গুণমুগ্ধ। একসময় নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের আনাচে-কানাচে শিল্পীরা পাগল দ্বিজদাসের গান গাইতেন। অনেক শিল্পী-গীতিকার তাঁর গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই ঘরানায় অনেক গান লিখেছেন। নেত্রকোণার বাউল সুনীল কর্মকার আর সালাম সরকাররা এখনো দ্বিজদাসের গানকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। সেখানকার অত্যন্ত গুণীজন উকিল মুন্সি, রশিদ উদ্দিন আর জালাল খাঁর অসংখ্য কালজয়ী গান থাকার পরও পাগল দ্বিজদাসের গানের মূল্য আকাশচুম্বি। অনেক নবীন শিল্পীর গানের খাতা নিরীক্ষা করলে দু-চারটা দ্বিজদাসের গান পাওয়া যাবে। বাউল, কবিগান, মুর্শিদী ও ভাটিয়ালি গানের তাত্ত্বিক পুরুষ হিসেবে তাঁরা দ্বিজদাসের গানকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে থাকেন। পাগল দ্বিজদাসের পারিবারিক নাম শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী (১২৫২-১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। পাগল দ্বিজদাস তার কবিনাম। এই নামের ভনিতায়ই তিনি গান রচনা করতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী শিবপুরস্থ যোশর পাদরী এস্টেটের নায়েব হিসেবে চাকুরি করতেন। এই পাদরী এস্টেটটি ছিলো নাগরী খ্রিস্টানপল্লী পর্তুগীজ জমিদারির একটি অংশ। তিনি সেই জমিদারির একজন নায়েব হয়ে কৃষকের পক্ষে গান লিখতেন।
দ্বিজদাসের জন্মস্থান পারুলিয়া গ্রাম ছিলো প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। অনেক ভাবুক, সাধক, পণ্ডিত ও ইংরেজি শিক্ষিত লোকের বাস ছিলো সেখানে। প্রাচীনকালে টোল-চতুষ্পাঠীর জন্যে পারুলিয়ার নাম বিক্রমপুর, নদীয়া, কমলাকান্ত (কুমিল্লা), বোয়ালিয়া (রাজশাহী) প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে তুলনীয় ছিলো। তেমন টোল-চতুষ্পাঠীতেই পাগল দ্বিজদাস প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একাডেমিক শিক্ষা বাদ দিয়ে তিনি প্রকৃতি, স্রষ্টা, সৃষ্টি রহস্য, রূপবৈশিষ্ট্য, সমাজ-সংস্কৃতি, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক ও মনুষ্য জগতের বিচিত্র ঘটনাবলি নিয়ে ভাবতে থাকেন। একপর্যায়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হয়ে ইহলোক-পরলোক নিয়ে গভীর ভাবনায় নিয়োজিত হন। এটাকে পূর্ণাঙ্গতা দিতে তিনি বাড়ির পাশে উঁচু ঢিবিতে গড়ে তোলেন ‘শক্তিমঠ’ নামে একটি আধ্যাত্মিক সাধনা কেন্দ্র। তা একসময় সারা ভারতবর্ষের খ্যাতিমান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে সাধক, বাউল, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, ধার্মিক, পণ্ডিত প্রমুখরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁদের সাধন-ভজন ও থাকা-খাওয়ার জন্যে তিনি বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে দেন। আশ্রমের আদলে মাটির ঘর আর গাছ-গাছালি আবৃত ‘শক্তিমঠ’ ভাবুকদের কাছে ‘শান্তিনিকেতন’ হয়ে ওঠে। পারুলিয়ার চক্রবর্তী বংশ সে-সময় ধনে-মানে বেশ সম্পদশালী। তাই দ্বিজদাস শক্তিমঠের খরচ যোগাতেন তালুকদার তহবিল থেকে। দেশি-বিদেশি অনেক আধ্যাত্মিক সাধক, সাধু-সন্ন্যাসী শক্তিমঠে অবস্থান করে সাধন-ভজন করতেন। যেখানে ধর্মীয় শাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংস্কৃত শ্লোক, স্রষ্টা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবন-মৃত্যুর রহস্য বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হতো। সেখানেই পাগল দ্বিজদাস আধ্যাত্মিক জ্ঞানচক্ষু লাভ করেন। সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টি-স্রষ্টার রহস্য, জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনার খোরাক পান। একই সঙ্গে সঙ্গীত রচনা শুরু করেন। সঙ্গী হিসেবে পান শ্রী জ্ঞানানন্দ গোস্বামী নামে আরেক পণ্ডিতকে। তিনি পারুলিয়া তথা নরসিংদী এলাকার মানুষ ছিলেন না। পণ্ডিতের ভিটা নামে খ্যাত চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে তিনি পাগল দ্বিজদাসের ডাকে সাড়া দিয়ে পারুলিয়ায় চলে এসেছিলেন। তাঁকে স্থানীয়ভাবে দ্বিজদাসের দক্ষিণহস্ত হিসেবে গণ্য করা হতো।
জ্ঞানানন্দ গোস্বামী প্রথমে শক্তিমঠের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে শক্তিমঠের পাশাপাশি সেখানে ‘শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা’ নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিজদাস। তাঁকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন জ্ঞানানন্দ গোস্বামী। সঠিকভাবে শক্তিমঠ ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার সময়কাল জানা না গেলেও পাঠশালাটি ইংরেজি স্কুল হিসেবে ঘোষিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামটি পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। উঁচু টিলার উপর শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার জায়গায় সাইবোর্ড উঠেছে পারুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের। একই সঙ্গে শক্তিমঠটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। পারুলিয়ার অনেক শিক্ষিত ও গুণীজনের সঙ্গে কথা বলে এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণ জানতে পারিনি। এমনকি পাগল দ্বিজদাসের বাড়িঘর কীভাবে প্রভাবশালী মহলের কব্জায় চলে গেছে, সে-বিষয়ে মুখ খোলার কাউকে পাওয়া যায়নি। এতোকিছুর পরও পাগল দ্বিজদাসকে দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। উত্তরসুরীদের মাধ্যমে তাঁর গান, পদ, ছড়া, মালসী ও ডাক বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকের হৃদয়ে রাখা আছে দ্বিজদাসের গান। সেখান থেকে তা বের করে এনে আর ধ্বংস করা যাবে না। পাগল দ্বিজদাস ছিলেন একজন যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী মানবিক মানুষ। তাঁর গানের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণিত হয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিষয়ক অনেক গান রচনা করে তিনি বিষয়টিকে এক রহস্যময় বিষয় করে তুলেছেন। যুক্তিবাদকে তিনি বুকে ধারণ করে অসংখ্য গান লিখেছেন। যার সিংহভাগই হারিয়ে গেছে। যা অক্ষত আছে, সেটা টিকিয়ে রাখার কৃতিত্ব হলো শক্তিমঠের কর্মাধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ গোস্বামীর। তিনি প্রথমবার দ্বিজদাসের গানগুলো সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। ‘শক্তিমঠ গ্রন্থমালা-১’ নামে তিনি প্রথমবার ১৭৫ টি গান সংকলন করেন সেই বইয়ে। বইয়ের আখ্যাপত্রে উল্লেখ করা হয় :
পাগল
দ্বিজদাসের গান।
শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী
বিরচিত
প্রথম সংস্করণ
প্রকাশক—
ব্রহ্মচারী শ্যামানন্দ।
পো. : পারুলিয়া, ঢাকা।
১৩৩২।
সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত মূল্য— পাঁচ সিকা।
Printed by Gopal Chandra De
at The Hena Press, Lakshmibazar,
Dacca.
পাগল দ্বিজদাসের গান’ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন জ্ঞানানন্দ। আসলে এই নামটি শক্তিমঠের কর্মাধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ গোস্বামী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি সংক্ষেপে নাম লিখতেন জ্ঞানানন্দ। ভূমিকায় তিনি লিখেন :
আমি কবি অথবা গায়ক নহি। সুতরাং গানের ভাল-মন্দ বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তবে কবি অথবা গায়েকরা যে গান রচনা করেন, তাহা শুধু তাঁদের নিজেদের জন্য নহে, আমাদের সকলের। এই ভরসাতেই সাধারণ জ্ঞানের দিক দিয়া আজ দ্বিজদাসের গান সম্বন্ধে দু’ একটি কথা বলিব।
প্রথমেই বলিয়া রাখি, পারুলিয়ার স্বনামধন্য শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী মহাশয় নিজেকে দ্বিজদাস পরিচয় দিয়া এই গানগুলি রচনা করেন। মহা-পাগলেরাই এমন করিয়া নিজের নামের আকাঙ্ক্ষাকে কাজের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিতে চাহে। তাই প্রকাশক দ্বিজদাসকে পাগল খেতাব দিয়াছেন। পৃথিবীর মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের আর এক নাম পাগল।
‘দ্বিজ-দাসের গান’ বাঙ্গলার পূর্ব্ব প্রান্তে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত। বাউল সম্প্রদায়ের অনেকেই এই গান গাহিয়া দেশ দেশান্তরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। অধিকাংশ গানের বর্ণিত ঘটনা সমূহ কবি বৈকুণ্ঠনাথের নিজের জীবনের উপর দিয়া ঝড়ের ন্যায় বহিয়া গিয়াছে বলিয়াই গানগুলি এমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘটনার স্রোতের সহিত কবি আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ঐ গানে উন্মাদনা আসে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতির তরঙ্গ-সঙ্গে নিজে নৃত্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ঐ গান মর্ম স্পর্শ করে। সমাজ, ধর্ম ও দেশের আকুলতায় কবি নিজে ব্যাকুল হইয়া গাহিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ঐ গানে চোখে জল আসে, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়, পলকে পলকে পুলক জন্মে। এক কথায় বৈকুণ্ঠনাথের গান তাঁর কর্ম ও অনুভূতির উলঙ্গ বিকাশ। বৈকুণ্ঠনাথ চিরকাল খেয়ালে চলিয়াছেন। তাই যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, জন-মতের অপেক্ষা না করিয়াও তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর প্রাণের ও গানের এই সারল্যে আমি মুগ্ধ। তাঁর ধর্মমত মহান, উদার। নিদর্শনÑ ‘হরি কি কালী বলা ভুল’। সমাজ-মত সঙ্কীর্ণতা-রহিত। পরোপকার তাঁর দৈনিক ব্রত। তাঁর গানে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর খাঁটি প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়।
‘দ্বিজ-দাস’ বৈকুণ্ঠনাথ আজও জীবিত। বয়স প্রায় আশীর কাছাকাছি। অদ্যাপি চশমার প্রয়োজন হয় না। শিশুকালে মাতৃ-হীন, পিতার দুলাল ছিলেন। তথাপি তাঁকে জীবন সংগ্রামে বুঝিতে হইয়াছিল যে, ‘মানুষ মনীব ভয়ানক জীব’। সংসারে তাঁর দুই গৃহিণী, আজও সমভাবে বর্ত্তমান। আত্মজ পুত্র নাই, দত্ত্ক গ্রহণে পিন্ড রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সংসারকে হাড়ে হাড়ে চিনিবার মতন সকল সুযোগই তাঁর ছিল। তাই তিনি বুঝিয়াছেন ‘ধনী আর রমণী জীবন্তে খায় প্রাণ’। বৈকুণ্ঠনাথ জীবনে অনেক উপার্জন করিয়াছেন, ব্যয়ও যথেষ্ট করিতেন। তাঁর অন্নে অনেক গরীব পরিবার প্রতিপালিত হয়।
‘পারুলিয়া শক্তিমঠ’ তাঁর শেষ জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। মঠের অধিকাংশ ভূমি বৈকুণ্ঠনাথের দান।
বৈকুণ্ঠনাথ দ্বিজের সেবায় আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় ‘দ্বিজ-দাস’ নামে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।
কবি বা গায়কের রচিত গানের বইয়ের ভূমিকায় রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আনুষঙ্গিক না হইলেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিশেষত: আত্ম-গোপন পটু ‘দ্বিজ-দাস’ বৈকুণ্ঠনাথ যে আজ নিজের রচিত গীতি-মাল্যে ভূষিত হইয়া হাতে হাতে ধরা পড়িলেন, ইহাতেই আমার আনন্দ।
নানা কারণে বইখানা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রকাশিত হয়। ফলত: অনেক স্থলে গ্রাম্যতা-দুষ্ট শব্দগুলির পরিবর্তন ঘটিয়া উঠে নাই। স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদও রহিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রার্থনা করি, ‘পাগল দ্বিজদাসের গান’ বাঙ্গালার প্রতি পল্লী বাট মাতাইয়া তুলুক, রাজপথ মুখরিত করুক, ঘরে ঘরে বিরাজিত হোক।
‘শক্তিমঠ’। ইতি—
তারিখ— মহাকাল। শ্রীনারায়ণে—
তিথি— মহামায়া। জ্ঞানানন্দ
১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সালমা বুক ডিপো থেকে ‘পাগল দ্বিজদাসের গান’ বইটির একটি সস্তা সংস্করণ বের করা হয়। এতে প্রথম সংস্করণের ৩৩ টি গান বাদ দেয়া হয়। তবে এই সস্তা সংস্করণে নতুন করে ৪ টি গান সংযুক্ত করা হয়। এসব অসঙ্গতি কিছুই সালমা বুক ডিপোর সংস্করণে বলা হয়নি। ১২ টাকা মূল্যের নিউজপ্রিন্টের ছাপা বইটিতে দ্বিজদাস সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘বাউল-ফকির উৎসব কমিটি’ কর্তৃক ‘পাগল দ্বিজদাসের গান’ বইটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পারুলিয়া শক্তিমঠ থেকে প্রকাশিত বইয়ের অনুরূপ। প্রথম সংস্করণের দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বইয়ে অনুসরণ করা হয়েছে। এই বইয়ের ভূমিকা থেকে জানা যায়, পাগল দ্বিজদাসের পৌত্রী ছিলেন শ্রী লক্ষ্মী চক্রবর্তী। তারই ছেলে গৌতম চক্রবর্তী প্রথম সংস্করণটি বাউল-ফকির উৎসব কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী চক্রবর্তী বইটি পেয়েছিলেন তাঁর কাকিমা মায়া চক্রবর্তীর কাছ থেকে। এতে বোঝা যায়, পাগল দ্বিজদাসের বংশধররা পারুলিয়া ছেড়ে ভারতের কোচবিহার গিয়ে বসতি স্থাপন করার সময় সর্বস্ব হারালেও পূর্বপুরুষদের মেধার সৃষ্টি স্বরচিত বইটি যক্ষের ধনের মতো বুকে লালন করেছিলেন। যার কারণে একশত বছরের পুরোনো সেই মহামূল্যবান দলিলটি নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। সেই মহামূল্যবান দলিলের ভূমিকায় পার্থ মজুমদার উল্লেখ করেন, “নরসিংদী তার বাউলদের জন্য বিখ্যাত। পাগল দ্বিজদাস সেখানকারই লোক আর তাঁর গান বহুকাল ধরে বাউলদের মুখে মুখে ফিরছে। তিনি কখনো আসরে গান গাইতে যেতেন না। জমিদারী সেরেস্তার কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ সামলাতেন আর পদ রচনা করতেন। সেই পদ বাউলদের মুখে মুখে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পাগল দ্বিজদাস তাঁর সাংসারিক জীবনে দুটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঔরসজাত কোনো সন্তান ছিলো না। তিনি একজন পুত্রসন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। ধারণা করা যায়, লক্ষ্মী চক্রবর্তী তারই মেয়ে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইয়ের সংস্করণে একটি চিঠি ছাপা হয়, যা লিখেছিলেন আইনসভার সদস্য ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের বাবা। তিনি ম্যাজিস্ট্রেসি জীবনের উপর ভিত্তি করে লিখেছিলেন ‘ডেপুটি জীবন’ গ্রন্থটি। তিনি পাগল দ্বিজদাসের গান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি দ্বিজদাসকে চিঠিটি দিয়েছিলেন। যা তাঁর পালকপুত্রের বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত ছিলো। চিঠিটি নিম্নে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।
শ্রীচরণকমলেষু—
আজ একটি বিষয় আপনাকে লিখিতে ইচ্ছা হইল। আপনাকে অযথা তোষামোদ করিবার অভিপ্রায়ে নয়, আপনার গুণাবলীর কথা মনে হওয়াতেই লিখিতেছি।
কয়েক মাস পূর্বে আমি ‘ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের’ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বামীবাগের কারখানায় বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলাম। সেখানে বাউল সঙ্গীত হইতেছিল। একদল বাউল গায়ক বড় মনোহর দেহতত্ত্ব বিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট গান শুনাইয়াছিল। ঢাকার অনেক গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। গানগুলি অতি মনোহর বোধ হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম গানগুলি কার রচিত? তখন তাহারা বলিল, অধিকাংশ গান আপনার রচিত। আপনাকে আমি একজন দক্ষ জমিদারের কর্মকুশল কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া জানতাম; কিন্তু গানগুলি শুনিয়া বুঝিলামÑ আপনি একজন ভাবুক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কবি। আপনার প্রতি আমার ভক্তি বর্ধিত হইল। আমি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আপনার পরিচয় দিলাম। তাঁহারাও একবাক্যে আপনার প্রশংসা করিলেন। দেহতত্ত্ব, বৃন্দাবনলীলা, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সাকার নিরাকার প্রভৃতি মীমাংসা অতি মনোমুগ্ধকর ভাষাতে আপনার গানে করিয়াছেন। ভাষা যেমন সরল তেমন মধুর। আপনি আমাদের দেশে গোপন থাকিয়া এমন সুন্দর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম। আপনি এ সব গান কোন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন কি না, জানি না। না করিয়া থাকিলে সত্বর প্রকাশ করা উচিত। সাহিত্য জগতে উহা অত্যন্ত আদৃত হইবে। যদি কোন বই থাকে, তাহা হইলে আমি একখানা বই পাইতে লালায়িত। আমার মনের প্রকৃত ভাব লিখিলাম। আপনাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়। ইতি—
10E, Qieemswau Raosoma
Delhi
2nd, March, 1924
সেবক
(স্বাক্ষর) শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ।
প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, লোকগবেষক ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান তাঁর ‘নরসিংদীর লোককবি’ গ্রন্থে পাগল দ্বিজদাস সম্পর্কে কিছু অভূতপূর্ব তথ্য উপস্থাপন করেন। সেই তথ্যমতে, পাগল দ্বিজদাস টাঙ্গাইলের আটিয়া পরগণার জমিদার এস্টেটের নায়েব হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার জমিদার ছিলেন অত্যাচারী ও অযোগ্য। খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর নির্যাতন চালাতেন। যার কারণে তিনি সেখানে বেশিদিন চাকুরি করেননি। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তাই তিনি গান বাঁধলেন :
ইস্তফা করি নায়েবগিরি, আমি চাই না এ চাকুরি আর।
নাহি বুঝ ভালো-মন্দ তুমি নিজে অন্ধ জমিদার।।
১ নম্বর আটিয়া পরগণা, কেহ আটিয়া ওঠেনা।
আমার আগে কত জনা পালিয়েছে পদ্মাপার।
আটিয়া জমিদারের নায়েবের চাকুরি ছেড়ে এসে তিনি যোশর পর্তুগীজ জমিদারি এস্টেটের নায়েব হিসেবে যোগদান করেন। নায়েবের কাজ করলেও প্রজা নিপীড়ন কখনো সমর্থন করেননি। কাজকর্মে করিৎকর্মা ছিলেন বলে খ্রিস্টান পাদরীরা তাঁকে তেমন ঘাটাতেন না। অপরদিকে দ্বিজদাস স্বাধীনচেতা হিসেবে কবিগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তবে অনেক সময় কৌশলে প্রজাদের খ্রিস্টান জমিদারদের হাত থেকে রক্ষাও করতেন।
তেমন একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হলো। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কালীগঞ্জের নাগরী-ধর্মপল্লীর পর্তুগীজ জমিদার হাতিতে চড়ে যোশর কাচারিতে আসতেন। মূলত খাজনা আদায়ের তদারকি করার জন্যেই আসা। বাকি খাজনা আদায় করার জন্যে জমিদারি এস্টেটের বিভিন্ন গ্রামে সফর করতেন পাইক বরকন্দাজসহ। একবার খাজনা অনাদায়ের কারণে পাদরী জমিদার ছুটাবন্দ গ্রামে ছুটলেন। হাতির গলায় ঘণ্টা বেজে চলেছে। এই আওয়াজে অনেক প্রজা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে গেলেন। কিছু প্রজা সঙ সেজে অদ্ভুত পোশাক পরে হাতির গায়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। এতে জমিদার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠলেন। পাইক-পেয়াদারা প্রজাদের উপর লাঠিচার্জ করার প্রস্তুতি নিলো। ঠিক তখনই নায়েব বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী তথা পাগল দ্বিজদাস বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, জমিদার মহাশয়, এরা আসলে পাগল, তাই এমন ব্যবহার করছে। এদের বেশভূষা দেখেন না কেমন বিশ্রী। পাগলের সঙ্গে কি বিবাদ করা সাজে? পাদরী জমিদার নায়েব দ্বিজদাসের কথা শুনে শান্ত হলেন। বললেন, সত্যিই এরা বদ্ধ পাগল। পাগলের আবার খাজনা কীসের? চলো সবাই কাচারিতে ফিরে যাই। এভাবে দ্বিজদাস তাঁর মানবিক গুণ ও বুদ্ধি দিয়ে ছুটাবন্দ গ্রামের অসহায় প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন।
কবিগানের আসরে মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন পাগল দ্বিজদাস। কণ্ঠে গান না তুলেও অসংখ্য গান, টপ্পা, ছড়া রচনা করে কবিয়ালদের মাথার তাজ হয়ে বেঁচে ছিলেন। তাঁর শিবলিঙ্গের টপ্পা, অগ্নিদেব ঘরজামাইয়ের টপ্পা, বসুমতির টপ্পা একসময় সারাদেশ মাতিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেগুলো হারিয়ে গেছে। তিনি কবিগানের আসরে ছুটে যেতেন। কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই কবিদের প্রশ্ন ও উত্তর বাতলে দিতেন। ছড়া, টপ্পা, গান রচনা করে দিতেন। একবার শিবপুর এলাকার নৌকাঘাটা গ্রামে হিন্দুপাড়ায় হরিচরণ আচার্য্য ও আলগীর পঞ্চানন আচার্য্যরে কবিগান হয়। পাগল দ্বিজদাস তখন অদূরবর্তী যোশর কাচারিতে ছিলেন। তিনি নৌকাঘাটা গ্রামে উপস্থিত হলেন। তিনি সন্তানতুল্য শিষ্য হরিচরণ আচার্য্য কবি গুণাকরকে সেখানে গান, ছড়া, টপ্পা প্রভৃতি যোগান দেওয়ায় সেই আসরে পঞ্চানন আচার্য্যরে পরাজয় ঘটেছিলো।
শিষ্য হরিচরণ আচার্য্যকে অবিভক্ত বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসেবে গড়ে তোলার নেপথ্য কারিগর ছিলেন গুরু পাগল দ্বিজদাস। তেমন আরো অনেক কবিগানের আসরে তিনি ছুটে গেছেন শিষ্যের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখার জন্যে। হরিচরণ আচার্য্যও গুরু দ্বিজদাসকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। হরিচরণ ‘বঙ্গের কবির লড়াই’ বইটি গুরু পাগল দ্বিজদাসকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, “আপনি দেশবিশ্রুতে পরম রসজ্ঞ কবি। আপনার ছদ্ম নামের ‘দ্বিজদাসের গান’ কাব্যজগতের অমূল্য সম্পদ। আপনার মর্ম্মস্পর্শী রচনা কৌশল অতুলনীয়। আপনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। কবিগান আপনার চিরপ্রিয়-কাব্য-সাহিত্যে আমার যা কিছু সুকৃতি তাহা আপনারই প্রতিভা প্রভাবের ফল।”
কবিগানের মুসলমানকরণই মালজোড়া গান। ভাটির দেশের মুসলিম কবিয়ালরা মালজোড়া গানের প্রবর্তক। এর মধ্যে নেত্রকোণার রশিদ উদ্দিনকে কেউ কেউ মালজোড়া গানের পথিকৃৎ বলে থাকেন। যা পরবর্তীতে বাউল গান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এলাকাভেদে বাউল গান কোথাও শরীয়তি-মারফতি, কোথাও বিচার গান, কোথাও পালাগান আবার কোথাও বয়াতি গান হিসেবে পরিচিত। ঢোল, হারমোনিয়াম, দোতারা, বেহালা, সারিন্দা, মন্দিরা, বাঁশি সহযোগে সারারাত পক্ষ-প্রতিপক্ষ গান গেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এতে দোহারের উপস্থিতিও থাকে। ভাটির দেশ ছাড়াও কবিগান বা মালজোড়া গানের একটি বড়ো ঘরানা রয়েছে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর দক্ষিণপাশে, বামনসুর গ্রামে। যা দেওয়ান ঘরানা হিসেবে পরিচিত। শত শত বাউল শিল্পী এই ঘরানার অধীনে গান গেয়ে আসর মাত করে যাচ্ছেন। বামনসুর গ্রামের দেওয়ান ঘরানার আদিপুরুষ হলেন আলফু দেওয়ান। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং লোক- সঙ্গীতের খ্যাতিমান শিল্পী। তাঁর দুই সন্তান মালেক দেওয়ান ও খালেক দেওয়ান প্রায় ৩ হাজার বাউল, মুর্শিদী, বিচ্ছেদ, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গান লিখে এবং মঞ্চে পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁদের তৃতীয় পুরুষ আরিফ দেওয়ান, মাখন দেওয়ানসহ আরো অনেকে বাউল গানে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে খালেক দেওয়ান ও তাঁর শিষ্য মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান বাউল বা আধ্যাত্মিক গানকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁদের লেখা ও সুর দেওয়া অনেক গান এখন বাংলার সর্বত্র গাওয়া হয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের গান নিয়মিত গাওয়া হয়। মাতাল রাজ্জাক এবং তাঁর গুরু খালেক দেওয়ান ছিলেন পাগল দ্বিজদাসের অনুরক্ত। তাঁরা প্রথম জীবনে পালাগান বা বাউল গানে দ্বিজদাসের অসংখ্য গান গেয়ে আসর মাত করেছিলেন। তাঁদের গানের খাতায় দ্বিজদাসের অনেক গান লিপিবদ্ধ থাকতো। তাছাড়া তাঁদের লেখা গানে দ্বিজদাসের গানের অনেক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা মনে করতেন, দ্বিজদাসের মতো সহসী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী সঙ্গীতজ্ঞ বাংলায় বিরল।
লেখাটি শেষ করবো একটি ঘটনা দিয়ে। বামনসুরের খালেক দেওয়ান তখন ভারবর্ষব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতা এইচএমভি থেকেও তাঁর গানের রেকর্ড বের হয়েছে। গ্রাম বাংলার বিয়েতে খালেক দেওয়ানের গান রেকর্ডে না বাজালে সেই বিয়ে ভেঙে যেতো। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই খালেক দেওয়ানের কাছে গান শেখার জন্যে ভিড় করতে থাকতেন। তেমন দুজন ছাত্র ছিলেন অন্ধ গায়ক শামসু দেওয়ান ও পাগল বাচ্চু। দুজনেই পরবর্তীতে বাংলায় বাউল গানের আসর মাত করে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। এই পাগল বাচ্চু পরে বাংলায় ‘পাগল’ পদবী দিয়ে নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেন। তাঁর ছোটো ভাই মনির হোসেনও ‘পাগল মনির’ নাম ধারণ করে বাউল-বিচ্ছেদ গানে নাম করেন। তাঁরও অনেক শিষ্য-সাগরেদ গানের আসরে গুরুর নাম-যশ বজায় রাখছেন। তবে এই ‘পাগল’ উপাধিটা গায়ক বাচ্চু পেলেন কোথায়? এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে আবার খালেক দেওয়ানের কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি যখন অসংখ্য শিষ্যকে বাউল, মারফতি গান শেখাতেন, তাঁদের মধ্যে বাচ্চুকে তাঁর আলাদা প্রতিভার মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে সে যোগ্য শিষ্য হয়ে ওঠতে পারবে বলে ‘পাগল’ সম্বোধন করতেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু পাগল দ্বিজদাসকে স্মরণ করে। গুরুর ভবিষ্যতবাণী প্রমাণ করেছিলেন পাগল বাচ্চু।
আপেল মাহমুদ
সাংবাদিক, গবেষক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক
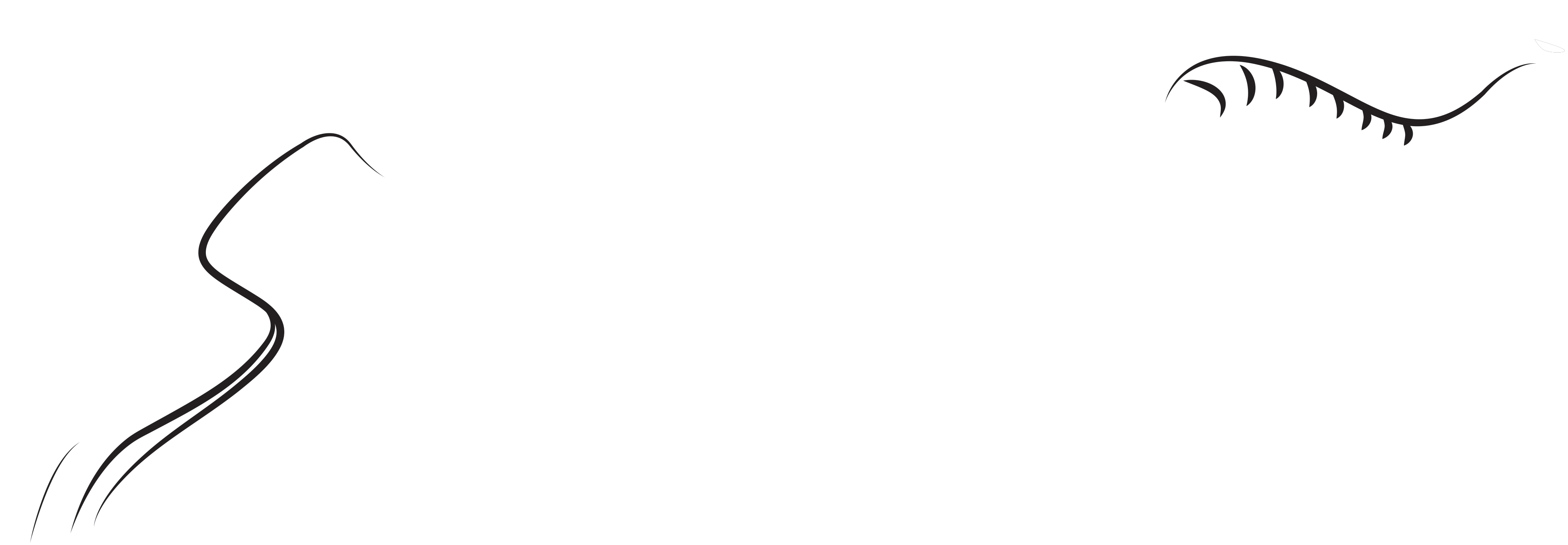
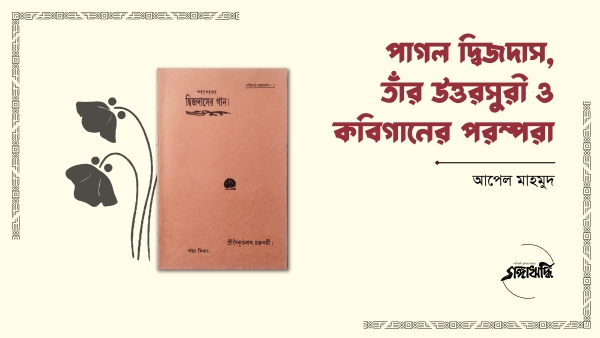
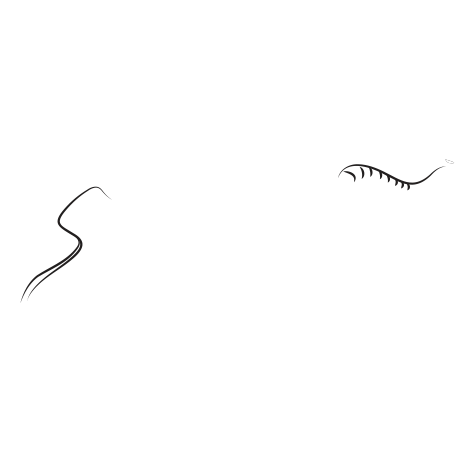
[…] যুক্তির গঠন যথেষ্ট গোলমেলে দেখায়। পাগল দ্বিজদাস চালাক লোক ছিলেন। বিশ্বাসীদের যুক্তি […]