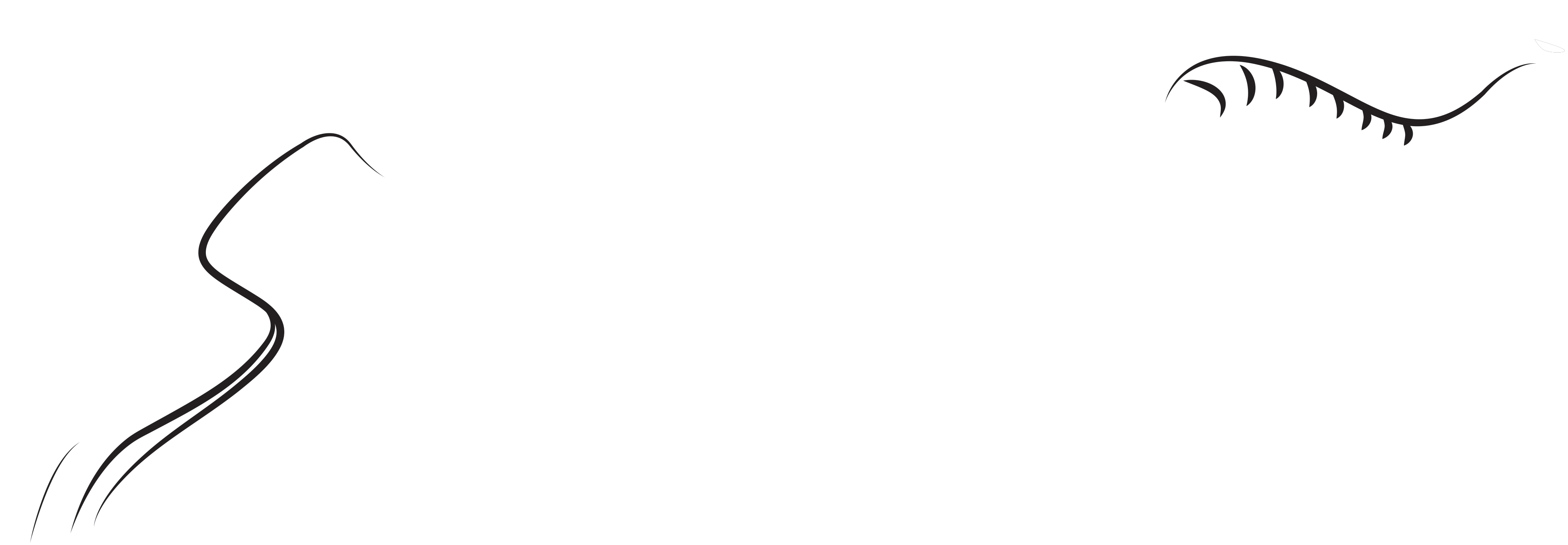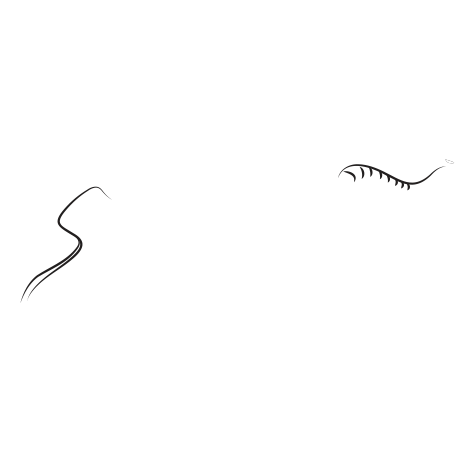ষোড়শ শতকের দিকে ইউরোপে বাড়ির কাছে মানুষের বর্জ্য সংগ্রহের জন্যে সেসপিট এবং সেসপুল গর্ত করার সংখ্যা বেড়ে যায়। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে রাস্তার নিচেও মানুষের মল-মূত্র যাওয়ার জন্যে নালা-খাল ইত্যাদি খনন করা হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ বৃষ্টির পানিতে বয়ে যাওয়ার মতো ছিলো না। সেসপুলগুলো তখন বিভিন্ন ট্রেডম্যান দ্বারা পরিষ্কার করানো হতো। এরা প্রতিরাতে আসতো এবং এক ধরনের লিকুইড নিক্ষেপ করে কঠিন মল বের করে নিয়ে আসতো। আর এই কঠিন বর্জ্য বাজারে বিক্রি করতো নাইটসয়েল নামে সার উৎপাদনের জন্যে। তারা ঊনিশ শতকের দিকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ম্যানহোল ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন, যা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু সংকট ক্রমেই বাড়তে থাকে। ম্যানহোলের মধ্যে ময়লা আটকে শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়।
দূষণ একটি অপবিত্র কাজ
দূষণের মধ্য দিয়ে পরিবেশ হত্যা একটি অপবিত্র কাজ হিসেবে বিবেচিত। ময়লার ভাগাড় থেকে আগত দুর্গন্ধ যেমন মানুষের দৈনন্দিন চলাচলে ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করছে, তেমনি গণস্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জনগণের সেবার নাম করে চেয়ার অলঙ্কৃত করা কথিত ডায়নামিক কর্তৃপক্ষ ‘গোলেমালে যাক কয়দিন’ সিস্টেমে শহরের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছেন। ময়লার ভাগাড়ে প্রতিদিন টনের টন আবর্জনা জমা হচ্ছে। তবে যেভাবে হওয়ার কথা, ঠিক সেভাবে নয়, পুরোটাই অব্যবস্থাপনায়। জনজীবনে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করছে শহরের এসব ময়লা। উন্নত দেশে যেভাবে ময়লা ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেছে, উন্নত বলে তারা পেরেছে, ‘আমরা তাদের মতো নই’ বলে কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব সেরে স্বর্গীয় সুখ লাভ করতে চায়। তাদের ধারণা, সব অটোমেটিক চলবে। এবং নিজেরা পকেট ভারি করার ধান্দায় এসব দায়িত্ব পালন না করে অন্যদিকে মনোযোগ দেন। মেয়র পদটা কেবলই একটা অর্থ কামানোর ম্যাগনেটিক গেট। একটা ‘এ’ গ্রেডের পৌরসভার যে-পরিমাণ লোকবল থাকা প্রয়োজন, সেটা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। জানা মতে, নরসিংদী পৌরসভার যথেষ্ট ফান্ড রয়েছে। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দিয়ে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সময় নষ্ট করতে রাজি নন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শহরের লোকসংখ্যা
তথ্য মতে, নরসিংদী শহরের লোকসংখ্যা প্রায় তিন লাখ। এখানে রয়েছে অসংখ্য স্কুল-কলেজ এবং অফিস। স্থানীয় এবং ভাড়াটে মিলিয়ে উল্লেখিত জনসংখ্যা প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন করছে। এসব বর্জ্য বিশাল বর্জ্যের পাহাড় সৃষ্টি করছে। তারপর আছে ভ্রমণকারী হিসেবে অস্থায়ী লোকসংখ্যা, যেটা হিসেবের বাইরে। অন্যদিকে, সদর উপজেলার মাধবদী পৌরসভার জনসংখ্যার হিসাব তথ্যের অভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। তবে আনুমানিক লাখের উপর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, শহরটিতে অসংখ্য কারখানা আছে, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করছে।
বর্জ্য আসার স্থানসমূহ
নরসিংদী শহরটির বর্তমান অবস্থা খুব বেশি দিনের নয়। ক্রমবর্ধমান জনবসতি প্রতিনিয়ত ময়লার ওজন বৃদ্ধি করে চলেছে। এসব ময়লার উৎস বিভিন্ন জায়গা। মূলত সাতটি জায়গাকে ময়লার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জায়গাগুলো হচ্ছে : ১. বাসা-বাড়ি (৭০%), ২. বাজার (১০%), ৩. মেডিক্যাল (৫%), ৪. শিল্প কারখানা (৫%), ৫. যানবাহন (৩%), ৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৩%) ও ৭. অনুষ্ঠান (৪%)। মূলত কোন স্থান থেকে কী পরিমাণ বর্জ্য আসে, তা বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী শতকরা হিসাবে দেখানো হয়েছে।
বর্জ্য ফেলার স্থানসমূহ
বাসা-বাড়ি, মেডিক্যাল, শিল্প কারখানা, বাজার, যানবাহন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানস্থল থেকে উৎপাদিত বিশাল পরিমাণ ময়লা ফেলা হয় মূলত তিন ধরনের জায়গায় : ১. নদীর ধারে (বড়ো বাজার, শেখেরচর), ২. বড়ো রাস্তার ধারে (নরসিংদী-মদনগঞ্জ রাস্তা) ও ৩. খাল বা কোনো নালা-নর্দমায় (মাধবদী)।
নদীতে বা নদীর ধারে ময়লা ফেলা হলে সেটা আবার নদীর পানিকে দূষিত করে থাকে। অনেকে এই পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। গোসল করার কারণেও অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, যেটি এখনো কোনো গবেষণার মুখ দেখেনি। অন্যদিকে ময়লার এই দূষিত পানি পান করে অনেক পশু-পাখি আক্রান্ত হচ্ছে, যা ইকোসিস্টেমে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।
বর্জ্যের ধরন
বিভিন্ন কারণে পরিবেশে নানা রকমের বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এসব বর্জ্য পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ১. কঠিন, ২. তরল ও ৩. গ্যাসীয়।
বিষক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আবার একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. বিষাক্ত বর্জ্য ও ২. বিষহীন বর্জ্য।
বিষাক্ত বর্জ্য
বিষাক্ত বর্জ্য কঠিন, তরল ও বায়বীয় হয়ে থাকে। যন্ত্রশিল্প, নির্মাণশিল্প, মোটরের নষ্ট পার্টস ও হাসপাতাল থেকে আসা বর্জ্যই বিষাক্ত বর্জ্য। এসব বর্জ্য মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এগুলো পরিবেশের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়। তাই এসব বর্জ্য পদার্থকে বিপদজনক বর্জ্য পদার্থ বলা হয়।
বিষহীন বর্জ্য
অফিস, রেস্টুরেন্ট, স্কুল-কলেজের বর্জ্য, পরিত্যক্ত খাবার, ফলের খোসা, পচা শাক-সবজি, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি বিষহীন বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। এগুলোকে সঠিকভাবে বিয়োজিত করলে পরিবেশের উপর অনেক কম ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।
লোকসংখ্যাপ্রতি বর্জ্যের পরিমাণ
নরসিংদী শহরে প্রায় ৩ লাখ লোকের বাস। এখানে মাথাপিছু দৈনিক ৫০০ গ্রাম বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এসব উৎপাদিত বর্জ্যের মধ্যে ৬.৭১ শতাংশ আবার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে সেই হিসেবে ৩.৫ টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর ৭০ শতাংশ বাসা-বাড়ি থেকে আসে। আর ১০.৪২ বর্গকিলোমিটার শহরটি থেকে প্রায় ৪০ টন বর্জ্য আসে। সংগৃহীত বর্জ্যের ৬৮ শতাংশের বেশি চলে যায় ল্যান্ডফিলে। ৪ শতাংশের মতো বর্জ্য রিসাইক্লিং হচ্ছে। বাকি সব নদী বা খাল-বিল বা অনির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। (বিবিএসের জরিপ)
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যয়
দেশের প্রতিটি স্থানীয় সরকার মোট ব্যয়ের ৮ শতাংশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় খরচ করে। এতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বছরে মাথাপিছু গড় ব্যয় হয় ৫২০-৫৩০ টাকার মতো। বিবিএস জরিপ অনুযায়ী নরসিংদী পৌরসভার হিসেব করলে দেখা যায়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তদারকির হার ৬০ শতাংশের কম। ২০২২ সালের বিবিএস প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিটি শহুরে নাগরিকের পেছনে ৫৫৮ টাকা ব্যয় হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে। এটি ২০২৫ সালে এসে ৬০০ টাকার কিছু বেশি দাঁড়িয়েছে। এটা অপ্রতুল। এটা বাড়িয়ে জনবল সংকট কমিয়ে শহরবাসীকে স্বস্তি দিতে হবে।
অস্থায়ী কর্মী ও দক্ষ লোকবল
বিবিএস জরিপ অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে ২০ হাজার ১০৫ জন স্থায়ী কর্মী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যা এই খাতে মোট কর্মীর ৩৮ শতাংশ। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে এই হার ৫০ শতাংশের মতো, আর পৌরসভায় ৩০ শতাংশেরও কম। জরিপ অনুযায়ী, এসব খাতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। নরসিংদী পৌরসভার ময়লা বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী, নরসিংদীতে ২০০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে। এছাড়া বাজারগুলোতে অস্থায়ী কর্মীও চোখে পড়ে। কিন্তু এই সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R
সমন্বিত ও সম্পূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 3R নীতি প্রয়োগ করা হয়। তিনটি R হলো :
১. Reduce (কমানো);
২. Reuse (পুনর্ব্যবহার) ও
৩. Recycle (পুনর্চক্রীকরণ)।
অর্থাৎ নীতিগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য না ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তারপর পণ্যের পুনরায় ব্যবহার এবং পণ্যের পুনর্চক্রীকরণের উপর বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন। এটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকরী দিক।
বর্জ্যের সম্ভাবনাময় অর্থনীতি
বর্জ্য নিয়ে দুটো প্রচলিত কথা হলো ‘আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ’ এবং ‘আবর্জনাই নগদ অর্থ’। নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা কিংবা জার্মানি বর্জ্য পদার্থকে সম্পদে পরিণত করছে। আবর্জনা থেকে এখন তৈরি হচ্ছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার এবং বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান তৈজসপত্র। নরসিংদীকে একটি A গ্রেডের শহর ধরে নিলে ও মোট জনসংখ্যা যদি ৩ লাখ ধরা হয় এবং বিবিএসের হিসেব অনুযায়ী জনপ্রতি ৫০০ গ্রাম আবর্জনা যদি দিনে উৎপাদিত হয়, তাহলে দিনে ১৫০ টন এবং মাসে ৪ হাজার ৫০০ টনের বেশি ময়লা উৎপাদিত হচ্ছে। এই বিপুল আবর্জনা ব্যবহার করে জেলায় বিশাল পরিমাণ সার, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চাহিদা এবং প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের চাহিদা মেটানো সম্ভব। পৌরসভার যদি যথেষ্ট অর্থ না থাকে, ঋণ নিয়ে এই প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে যশোর পৌর কর্তৃপক্ষকে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখেছি, যারা দুই বছরের মধ্যে লাভের মুখ দেখেছে। প্রকল্পের প্লান্ট থেকে উৎপাদিত সার, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বাজারমূল্য থেকে কম দামে তারা বিক্রি করছে। দিনে ৩০ থেকে ৪০ টন বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে এসব সার, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন করছে। এদিকে হিসেব করলে দেখা যায়, নরসিংদীতে বিরাট পরিমাণের বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করে পরিবেশ ও জনজীবনের ক্ষতি সাধন অর্থাৎ সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, যশোরের প্রকল্পটি দেশের প্রথম পাইলট প্রকল্প।
বর্জ্যের স্তূপ স্থাপন
১৯৯১ সালে Environment Protection Agency ল্যান্ডফিল সাইটের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতিমালা প্রদান করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, একটি ল্যান্ডফিল সাইটের ৩০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোনো খাবার পানির নলকূপ থাকা যাবে না এবং ৬৫ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোনো ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ ও পার্ক থাকা যাবে না। এছাড়াও রাস্তার পাশে ময়লার ভাগাড় রাখা যাবে না। ময়লার স্তূপ স্থাপন করার জন্যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ময়লা রাখার স্থান পাকা করা। কিন্তু যেখানে ময়লা ফেলা হয়, সেখানে দেশের কোথাও পাকা করা হয়েছে বলে দেখা যায় না। কারণ বিশাল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রচুর তরল রস বেরিয়ে আসে, যেগুলো পানির স্তরে মিশে মিঠা পানির ক্ষতি করছে। এছাড়াও এই তরল রস খোলা জায়গায় ফেলার কারণে ফসলি জমিতে গিয়ে পড়ছে। ফলে ফসল ও জমিÑ উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নরসিংদীর শালিধা এবং মাধবদীর ফায়ার সার্ভিস এলাকায় প্রায় অর্ধ কিলোমিটার করে যে-পাহাড় পরিমাণ ময়লার ভাগাড় সৃষ্টি করা হয়েছে, এতে বিশাল পরিমাণ জমি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে যারা নরসিংদী থেকে মদনগঞ্জ রাস্তাটি ব্যবহার করেন, তাদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ হাজারের বেশি। রাস্তার পাশে থাকা ময়লার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়। চালকেরা এই ভোগান্তির শিকার প্রতিদিনই হচ্ছেন। অনেক সময় যানজট সৃষ্টি হতে দেখা যায় এই ময়লার ভাগাড়ের ঠিক মাঝখানে।
প্লাস্টিক পণ্য
বিগত কয়েক বছরে নতুন বর্জ্য হিসেবে প্লাস্টিক বর্জ্য বেড়েই চলেছে। মূল বর্জ্যের ১০ শতাংশ এখন প্লাস্টিক বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। তার মানে ৪ হাজার ৫০০ টন বর্জ্যের মধ্যে ১০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য। এগুলো রিসাইক্লিং না করার ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এসব প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশে মিশে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এসব বর্জ্যের মধ্যে ৩৯ শতাংশ ভাগাড়ে ফেলা হচ্ছে, তার ৩৬ শতাংশ মাত্র রিসাইক্লিং হচ্ছে।
মাইক্রোপ্লাস্টিক
প্লাস্টিকের ব্যাগ, সিন্থেটিক পোশাক, প্লাস্টিকের কার্পেট, থালা-বাসন, বোতল, টায়ার, খেলনা, বাসায় ব্যবহৃত প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যদ্রব্য, প্যাকেটজাত দ্রব্য এবং প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্য ব্যবহারের পর ফেলে দেয়া হয়। সেগুলো ফেলা হয় ময়লার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। ফেলে দেয়া ময়লা যখন দীর্ঘ সময় ধরে রোদে পড়ে থাকে, তখন রৌদ্রতাপ ও অণুজীব এবং পরিবেশের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে এসব প্লাস্টিক ভেঙে তৈরি হয় বিভিন্ন আকৃতির প্লাস্টিক, যা আবারো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ক্ষয় হয়ে পরিণত হয় ছোটো ছোটো প্লাস্টিক কণায়। এগুলোকেই বলা হয় মাইক্রোপ্লাস্টিক। মাইক্রোপ্লাস্টিক মূলত চার ধরনের হয় : ১. অতি ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা (ন্যানোপ্লাস্টিক, ১-১০০০ ন্যানোমিটার), ২. ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক ১- ১০০০ মাইক্রোমিটার), ৩. মাঝারি আকারের প্লাস্টিক কণা (১-১০ মিলিমিটারের বেশি) ও ৪. বড়ো প্লাস্টিক কণা (১ সেন্টিমিটারের বেশি)।
এসব প্লাস্টিক মাটিতে ফেলা হলে ৪০০ বছরেও নষ্ট হয় না। বরং প্রতিনিয়ত গলে গলে বাতাসের সাথে মিশে বছরের পর বছর ধরে পরিবেশের ক্ষতি করে। তাই বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাস্তুতন্ত্রে মাইক্রোপ্লাস্টিক সূর্যতাপে গলে বাতাসের সাথে মিশে প্রাণীর খাবারে পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে মানুষও বাদ পড়ছে না। ভয়ের কারণ হচ্ছে, ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ফিল্টার করার পরও খাবার পানি থেকে এসব প্লাস্টিক কণা আলাদা করা যায় না। তাহলে ময়লার স্তূপে থাকা এসব প্লাস্টিক অবশ্যই উদ্বেগের কারণ। কেননা এসব প্লাস্টিক মানুষের লালা, রক্তে ও মলে ঢুকে যাচ্ছে। তারপর এগুলো ফুসফুস হয়ে রক্তের মাধ্যমে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগের কারণ হচ্ছে।
বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৫ সালে ঢাকায় মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিলো ৩ কেজি। সেটা ২০২৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫ কেজির কাছাকাছি। নরসিংদী ঢাকার খুব কাছের একটি শহর। এখানে জীবনযাত্রার মান ঢাকার কাছাকাছি। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি, শহরে থাকা প্রায় তিন লাখ মানুষের জনপ্রতি ব্যবহৃত প্লাস্টিক অন্তত ২০ কেজির কম হবে না।
গরীব-ধনীর তুলনামূলক বর্জ্য উৎপাদন
গড়ে একজন মানুষ বছরে ১৮০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে। শহরে যেহেতু তুলনামূলক আর্থিকভাবে মোটামুটি স্বাবলম্বীরাই বসবাস করে, সেই হিসেবে গরীবের তুলনায় ধনীরাই বেশি বর্জ্য উৎপাদন করে থাকে। আনুমানিক ধরে নিলে তুলনাটি হতে পারে ৭৫ : ২৫ অনুপাতে। অর্থাৎ নরসিংদী পৌরসভার ৩ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৫ হাজার মানুষই বেশি বর্জ্য উৎপাদন করছে।
বায়োমাইনিং
ময়লার দুর্গন্ধে নগরবাসী অতিষ্ঠ। এটা থেকে মুক্তির জন্যে পৌরকর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। নরসিংদীর শালিধা, মাধবদীর ফায়ার সার্ভিস এলাকা, শেখেরচর বাজার, মাধবদী শহরের নদীর পাড় এবং ভেলানগর ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ময়লার দুর্গন্ধে নগরের বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। অথচ পৌর কর্তৃপক্ষ চাইলেই এটার একটা চমৎকার সমাধান করতে পারে। সেটি হচ্ছে বায়োমাইনিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ময়লার উপর গজিয়ে তোলা হয় সবুজ গাছ। সবুজায়নের মাধ্যমে ময়লার ভাগাড়কে বাগানে পরিণত করা সম্ভব। এই পদ্ধতিটি কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে শুরু করে দিয়েছে এবং যথাযথ ফলও পাচ্ছে তারা। নরসিংদী শহরের শালিধা অঞ্চলে বিশাল ভাগাড়ের পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম ভাগাড়টিতে চোখ বুলালেই দেখা যাবে এর প্রমাণ। সেখানে প্রাকৃতিক উপায়েই গাছ জন্মাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ চাইলেই অল্প খরচে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করতে পারে।
পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্য পৃথকীকরণ
দুর্গন্ধে নাকাল শহরবাসী। এটার পেছনে অব্যবস্থাপনাকেই মূলত দায়ী করা যায়। কর্তৃপক্ষ যদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নির্দেশ দেয় যে, তারা যখন বাসা-বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করবে, তখন তারা ময়লাকে দুটি ভাগে সংগ্রহ করবে। ভাগ দুটি হচ্ছে পচনশীল দ্রব্য এবং অপচনশীল দ্রব্য। পাশাপাশি পৌরকর্তৃপক্ষ সারা শহরে মাইকিং করে শহরবাসীকে অনুরোধও করতে পারে যে, তারা যখন দ্রব্য ব্যবহার করবে, তখন যেন ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করে রাখেন। তখন পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরও পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্য পৃথক করতে বেগ পেতে হবে না। তারপর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে যখন ময়লা ফেলা হবে, তখন প্রথমে অপচনশীল, তারপর কিছুটা দূরত্বে পচনশীল ময়লা ফেলা হবে। এতে দুর্গন্ধ অনেকটা কমে আসবে। এখানে সচেতনতার পাশাপাশি সদিচ্ছার প্রয়োজন। গরম বাড়ার সাথে সাথেই পচনশীল দ্রব্যের দুর্গন্ধ চারদিকে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ যেন তাদের দক্ষতা ব্যবহার করে দুর্ভোগ কমিয়ে আনে, সেটার জন্যে নগরবাসীদেরও ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

হাসপাতালের বর্জ্য আলাদাকরণ
হাসপাতালের বর্জ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু থাকে। এগুলো থেকে বড়ো একটা অংশ রোগ ছড়িয়ে থাকে। শহরে লোকসংখ্যা বেশি থাকায় নরসিংদী সদরেই শুধু বিশের অধিক সরকারি ও প্রাইভেট হাসপাতাল গড়ে ওঠেছে। প্রাইভেট হাসপাতালগুলো ছোটো এবং তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন থাকলেও সরকারি হাসপাতালগুলোর অবস্থা নাজুক। প্রতিদিন এগুলো থেকেও ভালো পরিমাণে বর্জ্য আসছে এসব ভাগাড়ে। তাই পৌরকর্তৃপক্ষ এসব হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থের জন্যে আলাদা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করতে পারে, যেটা হবে লোকালয় থেকে দূরবর্তী স্থানে। এতে দুর্গন্ধ ও জীবাণু— দুটি থেকেই বাঁচা যাবে।
পলিথিন
ময়লার ভাগাড়ে তাকালেই দেখা যায় পলিথিনের বিশাল সমাহার। পলিথিন মাটির সাথে মেশে না। যেহেতু পরিবেশের জন্যে এটা মারাত্মক ক্ষতিকর, সেহেতু এটা নিয়ে পৌরকর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। নরসিংদী এবং মাধবদী শহরে প্রতিদিন গড়ে পরিবারপ্রতি ৪ টি করে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। আর এসব ব্যাগ একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেয়া হয়। সেই হিসেবে শুধু শহরেই তিন লাখ মানুষের গড় পলিথিনের ব্যবহার দিনে ২ লাখ ৭৫ হাজার পিস। সংখ্যাটা মাসে দাঁড়ায় ৮২ লাখ ৫০ হাজারে। এসব পলিথিন নানা উপায়ে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। তাহলে কী পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন উপায়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে, তা ভেবে দেখা দরকার।
ই-বর্জ্য
নতুন বর্জ্য হিসেবে প্রতিদিন ই-বর্জ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। নরসিংদী ঘনবসতি শহর বিধায় এখানে প্রচুর পরিমাণে ই-বর্জ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। শহরে ব্যবহৃত ই-বর্জ্যের মাত্র ৩ শতাংশ পুনর্প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। বাকি ৯৭ শতাংশই জায়গা করে নিচ্ছে ময়লার ভাগাড়ে। শহরে এই হার বছরে ২১ শতাংশ করে বেড়েই চলেছে। ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট স্ট্যাটিসটিকস পার্টনারশিপের এক জরিপ বলছে, বিশ্বে প্রতিবছর ই-বর্জ্য ২১ শতাংশ হারে বাড়ছে। বর্তমানে নরসিংদী শহরেও ই-বর্জ্যের সুনামি দেখা যাচ্ছে। এগুলোতে সিসা, টিন, সিলিকন, দস্তা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ও নাইট্রাস অক্সাইড নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এসব পদার্থ মাটি ও পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে এবং এসব দূষিত রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্নভাবে মানুষের দেহে প্রবেশ করছে। বিশেষ করে, গর্ভবতী মা ও শিশু এটার শিকার হচ্ছে বেশি। অথচ সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণে কমে যেতো। পাশাপাশি পৌরকর্তৃপক্ষ লাভজনক উপায়ে ব্যবসা করে পৌরসভার তহবিলও বাড়াতে পারতো।
পৌর পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য
নরসিংদী পৌরসভার ময়লা বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা মো. ইয়াসিন মিয়ার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শহরে মোট ২০০ পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে। তারা প্রতিদিন বাসা-বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করছেন কোনোরকম প্রটেকশন ব্যবহার না করেই। এতে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। পৌরকর্তৃপক্ষের উচিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং আবর্জনা সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রটেকশন ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা। কারণ ময়লা থেকে বের হওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি তাদের শরীরে প্রবেশ করছে। ফলে চোখ জ্বলা, ফুসফুসে সমস্যা দেখা দেয়াসহ নানাবিধ সমস্যায় তারা ভুগতে থাকে। তারা যদি অসুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শহর আবর্জনার স্তূপে পরিণত হবে। তাই তাদের সুস্থ রাখার জন্যে কর্তৃপক্ষের উচিত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
মাছ ও মুরগির বর্জ্য
শহরের বাজারগুলোতে অনেকগুলো ফার্মের মুরগির দোকান গড়ে ওঠেছে। সব মিলিয়ে একশোর কম হবে না। এসব বাজার থেকে বিষ্ঠা সংগ্রহ করে সরাসরি ময়লার ভাগাড়ে ফেলা হয়। ফলে দুর্গন্ধ আরো বেড়ে যায়। সেই সাথে আছে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। মৎস্য থেকেও প্রচুর বর্জ্য পদার্থ আসে, যেগুলো দুর্গন্ধ ছড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এগুলো অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশে ব্যাপকভাবে ইকোলজি হত্যা করছে। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক নিয়মে করতে হবে। ক্যাটাগরি অনুযায়ী বর্জ্য অপসারণ আলাদাভাবে করতে হবে।

পোশাকের বর্জ্য এবং ক্ষতিকর ফাইবার
প্রকাশিত অ্যালগালিটা ২০১২ নিবন্ধ অনুসারে, একটি পলিস্টার পোশাক থেকে প্রতিবার ওয়াশিং বিমুক্ত করার পর ফাইবার বের হয় ১৯০০-র বেশি। পরীক্ষায় আরো দেখা যায়, প্রতি লিটার বর্জ্যপানিতে নিষ্কৃত মাইক্রোফাইবারের সংখ্যা ১০০-র বেশি। এসব রঙ করা কাপড় ব্যবহারের পর যখন ফেলে দেয়া হয়, তখন ময়লার স্তূপে আরেকটি সংখ্যা যুক্ত রড, যার পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। শহরে যদি ৩ লাখ লোক থাকে, তাহলে এসব রঙ মিশ্রিত কাপড় যায় কোথায়? সূর্যের তাপে কাপড় থেকে বের হয়ে আসা রঙ প্রাকৃতিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতি করছে। কারণ কাপড় উৎপাদনে প্লাস্টিকের যথেষ্ট ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এসব রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথ উপায়ে করতে হবে। নয়তো নরসিংদীর শালিধা এবং মাধবদীর ফায়ার সার্ভিস এলাকায় ময়লার ভাগাড়ে আবর্জনার পরিমাণ হবে আকাশচুম্বী।
ময়লা থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস
বর্তমান বিশ্বে একটা বড়ো আশঙ্কার কারণ হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। পচা আবর্জনা অর্থাৎ মূলত পচা খাবার থেকে ১০ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে। তাহলে শহরে দৈনিক যে-পরিমাণ বর্জ্য হচ্ছে, তার অর্ধেকই পচনশীল দ্রব্য। সেই হিসেবে ৪ হাজার টনেরও বেশি বর্জ্য মাসে পচছে। এবার এটা থেকে যে-পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে, সেটা বড়ো উদ্বেগের কারণ। এই উদ্বেগ শুধু নগরবাসীর জন্যে নয়, সারা দেশের জন্যেই। এসব আবর্জনার কারণে মশার উপদ্রব বেড়ে চলেছে। মূলত তাপ বাড়ার সাথে সাথে এই ঘটনাটি ঘটতে থাকে। শহরের মানুষের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে এই গ্যাস। কর্তৃপক্ষ যদি এটার সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনদুর্ভোগ আরো প্রকট থেকে প্রকটতর হবে।
বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি
নরসিংদী শহরের শালিধা এবং মাধবদী পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস এলাকায় বর্জ্যের বিশাল স্তূপ চোখে পড়ে। প্রতিদিনই দেখা যায়, বর্জ্যগুলোতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলছে। মূলত দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতেই কর্তৃপক্ষ এই কাজ করছে তাদের অজ্ঞতা থেকে। কিন্তু কী পরিমাণ ক্ষতি যে হচ্ছে, সেটার ইয়ত্তা নেই। আবর্জনা পোড়ানোর ফলে নির্গত হয় পার্টিকলস, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাউড্রোজেন ক্লোরাইড, বেনজিন, পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনালস, আর্সেনিক, মার্কুরি ও ফার্নাস।
তাছাড়া ময়লা পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ার কারণে যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটছে।
যে কেউ এসব রিপোর্ট দেখলে আঁতকে না উঠে পারবেন না। অথচ এসব ব্যাপারে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের জ্ঞান শূন্যের কোটায়, এই কথা অবিশ্বাস হয় না। তাদের কাছে এসবের কোনো তথ্যই পাওয়া যাবে না। তারা মূলত প্রাইমারি থেকে ফাইনাল ডিসপোজাল পর্যন্ত ময়লা ফেলে দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন। কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা না করলে তাদের ঘুম ভাঙবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেটা নরসিংদী কিংবা মাধবদীর পৌরকর্তৃপক্ষের বেলায় দেখা যায় না।

টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কিছু সুপারিশ
সঠিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে। নগরবাসীর শান্তির জন্যে কর্তৃপক্ষকে সময়োপযোগী কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শহরে কোনো জঞ্জাল থাকবে বলে মনে হয় না। একটি পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ নিচের সুপারিশগুলো ভেবে দেখতে পারে। সুপারিশগুলো হচ্ছে :
১. বর্জ্য পদার্থের ক্ষতিকর দিক নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি।
২. বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্জ্য উৎপাদনের উৎসস্থলে শ্রেণি অনুযায়ী পৃথক ডাস্টবিনে ফেলার ব্যবস্থা করা।
৩. বর্জ্য পদার্থের পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভজনক পণ্যে রূপান্তরিত করা।
৪. আবর্জনাগারের কাছাকাছি বায়োগ্যাস প্রজেক্ট স্থাপন করা, যাতে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি জ্বালানি খাতে ভূমিকা রাখা যায়।
৫. নগরে জোনভিত্তিক ছোটো আকারের পতিত স্থানে ডাম্পিং জোন গড়ে তোলা।
৬. সড়কে জ্যাম হ্রাস ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ থেকে সাধারণ নগরবাসীকে বাঁচাতে দিনের পরিবর্তে রাতের বেলায় বর্জ্যের গাড়িতে বর্জ্য অপসারণ।
৭. সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে শহরের অভিজ্ঞ মানুষদের নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেয়া।
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রিনক্লাব গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে ছোটো ছোটো কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ-ব্যাপারে সচেতন হতে পারে।
৯. আবর্জনার উপর বায়োমাইনিং পদ্ধতিতে সবুজায়ন।
১০. পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনগুলোর পরামর্শ গ্রহণ।
সুতরাং একটি পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তুলতে হলে বিশেষজ্ঞ টিমের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের দেখানো পথেই হাঁটতে হবে। নয়তো শহরের দুর্গন্ধ আগের অবস্থায়ই থেকে যাবে। যেখানে ডাস্টবিন রয়েছে, সেখানে পর্যাপ্ত কীটনাশক এবং সুগন্ধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। কর্তৃপক্ষ চাইলে এলাকায় এলাকায় ময়লা শোষণ করে এমন ডাস্টবিন ব্যবহার করতে পারে। এলাকার মোড়ে মোড়ে ময়লা ফেলে যেভাবে পরিবেশ ও জনজীবনের ক্ষতি করা হচ্ছে, সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মোড়ে মোড়ে ফেলা আবর্জনা বড়ো গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাস্তার পরিবেশ নষ্ট হওয়াসহ মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই অতি দ্রুত কীভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নগরবাসীকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেয়া যায়, সেদিকে কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে।
বালাক রাসেল
সম্পাদক, dheki24.com