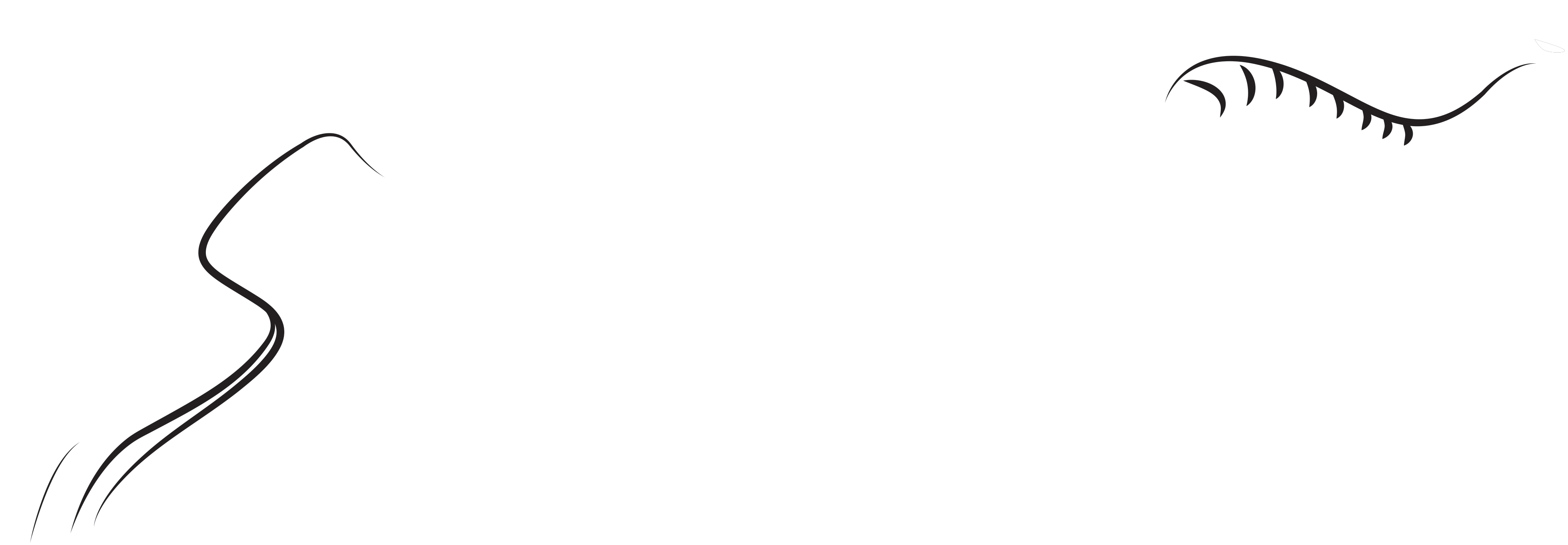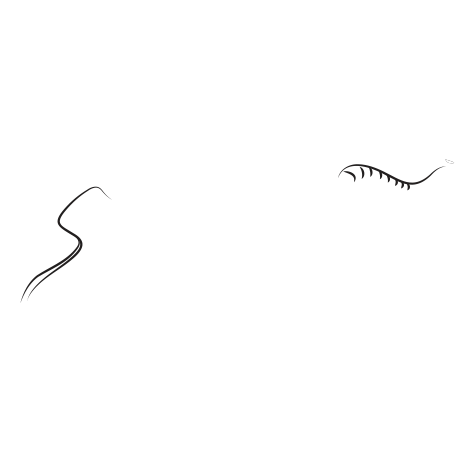নরসিংদী একটি প্রাচীন জনপদ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভূ-ভাগে প্রথম জনবসতি হয় পাথরের যুগে। চার-পাঁচ সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ-এলাকায়ই নিজেদের উদ্ভাবিত লোহার কুড়াল দিয়ে বন-জঙ্গল কেটে কৃষির সূত্রপাত করেন। এ-লোহার উৎস ও ব্যবহার সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ বর্ণনা নিচে লেখা আছে। উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে অনেক কিছুই এখন প্রমাণিত হচ্ছে। অনেক আগে থেকেই নরসিংদী শিল্পসমৃদ্ধ বাণিজ্য এলাকা। অনুমান করা যায় যে, নরসিংদী ছিলো তীরবর্তী অভ্যন্তরীণ ব্যস্ততম নদী বন্দর। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এ-বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। তার কারণ এ-বন্দরের সাথে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলোর যোগাযোগ ছিলো অত্যন্ত নিবিড়। প্রাচীন সমতটের রাজধানী রোহিতাগিরি (ময়নামতি) থেকে গোমতী ও ডাকাতিয়া নদীর স্রোত বেয়ে বণিকেরা আসতো বর্তমান বেলাব থানার উয়ারী-বটেশ্বর বন্দরে। সেখানে তারা বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা করে আড়িয়াল খাঁ’র স্রোত ধরে চলে আসতো মেঘনার তীরে, নরসিংদী বন্দরে। নরসিংদী থেকে নদীপথে দক্ষিণে ২০ মাইল দূরে সোনারগাঁ, আর সেখান থেকে ভাটিয়াল স্রোত ধরে বণিকেরা যেতো বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ ও সামন্দর বন্দরে। এ-বন্দর থেকে রপ্তানি হতো কার্পাস তুলা, মিহি চাল ও বিভিন্ন শস্য সামগ্রী। পরিবর্তে এখানে আমদানি করা হতো সম্ভার থেকে উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র, ময়নামতির মোটা শাড়ি, পুতির মালা ও কাঠের খড়ম। গোমতী (রংপুরের অন্তর্গত) ও ধামরাই থেকে তামা ও পিতলের তৈজসপত্র আর পুণ্ড্রনগর থেকে পোড়ামাটির বিগ্রহ। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বাণিজ্য উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যার তীরে আরবীয়দের জাহাজ নোঙর করতো। আরবীয়রা এ-অঞ্চল হতে লাক্ষ্যা নির্মিত দ্রব্যাদি, মসলিন ও আখের গুড় ইউরোপীয় দেশসমূহে নিয়ে যেতো। শাতিল-লাকমা থেকে শীতলক্ষ্যা নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কেননা সেকালে এ-জনপদ লাক্ষ্যা শিল্পের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলো।
প্রাচীনকালে এ-বন্দরের বিস্তৃতি ছিলো নদী তীরের উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দেড়মাইলের মতো। এই বন্দরের প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিম দিকে দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হতো প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ। পূর্ব দিক দিয়ে বন্দরের কূল ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হতো বিশাল মেঘনা। রেনেলের তথ্য থেকে জানা যায়, সোনারগাঁয়ের সাত মাইল দূরে (উত্তর) নলদী থেকে নরসিংদী পর্যন্ত নদীটি (মেঘনা) সুপ্রশস্ত খরস্রোতা এবং দ্বীপবহুল। অনেক স্থানেই এর পরিসর আড়াই মাইলের বেশি। ব্রহ্মপুত্র থেকে উদ্ভূত হাড়িধোয়া নামক একটি শাখা নদী বন্দরের উত্তর দিক হতে প্রবাহিত হয়ে বন্দরের পূর্ব দিকে মেঘনার সাথে সংযুক্ত ছিলো। হাড়িধোয়া ও মেঘনার এ-সংযুক্তি এখনো বিদ্যমান। নরসিংদী শহরের পূর্ব প্রান্ত (বর্তমান থানারঘাট) থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার মাঝিয়ারা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় সাত-আট মাইল বিস্তৃত ছিলো বিশাল মেঘনা নদী। প্রাচীনকালের ভূ-প্রকৃতির এই রূপ নরসিংদী শহরের আশেপাশের মরা নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও পূর্ব দিকে চরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নিম্নভূমির দিকে তাকালে অতি সহজেই অনুমান করা যায়।
ইলিয়াছ শাহী বংশের পর হাবশী শাসনের যুগে বাংলাদেশে অনেক ছোটো-বড়ো জমিদারের উৎপত্তি হয়। হাবশী শাসনের শেষ পর্যায়ে সোনারগাঁ ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম শীতলক্ষ্যার তীরে ‘ধনপদ সিংহ’ নামে এক ব্যক্তি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করে রাজা খেতাব গ্রহণ করেন। রাজা ধনপদ সিংহের পুত্র নরসিংহ জমিদারির সীমা বৃদ্ধি করেন। রাজা নরসিংহ শীতলক্ষ্যা নদীর তিন মাইল পূর্বে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে নগর নরসিংহপুর নামে আবাসিক স্থান নির্মাণ করেন এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল ভারতের সুবে বাংলার অন্যতম ছিলো ‘মহেশ্বরদী’ পরগণা। বর্তমান নরসিংদী জেলার সমগ্র অঞ্চলই ছিলো মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্ভুক্ত। এই পরগণার উত্তরে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে সোনারগাঁ আর পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী ও ভাওয়াল পরগণা। পূর্ব দিকে মেঘনা নদী ও বরদাখাৎ পরগণা। এই পরগণার সদর দপ্তর ছিলো নগর মহেশ্বরদী। এই মহেশ্বরদী পরগণার ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পারুলিয়া গ্রাম। পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ও পরগণার সদর দপ্তর মহেশ্বরদীর সঙ্গে এ-গ্রামের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিলো অত্যন্ত সুগ্রথিত। স্থলপথে রাজধানী সোনারগাঁ থেকে একটি প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা উত্তরমুখী সাতগাঁয়ের উপর দিয়ে পাঁচদোনা হয়ে পারুলিয়াকে সংযুক্ত করতো। প্রাচীন এ-রাস্তাটি পারুলিয়া থেকে উত্তরমুখী অগ্রসর হয়ে শিবপুর ছুঁয়ে নগর মহেশ্বরদীর উপর দিয়ে পরগণার শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখনো রাস্তাটি আছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পারুলিয়া ছিলো মহেশ্বরদী পরগণার সবচেয়ে বড়ো রাজস্ব আদায় কেন্দ্র ও প্রশাসনিক কাচারি। এখানে পরগণা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি বাস করতেন, যার উপাধি ছিলো নায়েব-ই-দেওয়ান। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ‘নরসিংদী’ নামকরণের উৎস মনে করেন রাজা নরসিংহকে। কেউ মনে করেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত বংশীয় রাজা নরসিংহ গুপ্তকে।
‘নরসিংদী’ নামকরণের কয়েকটি উৎস
‘পূর্ববঙ্গে মহেশ্বরদী’ গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, কোনো কোনো প্রাচীন মানচিত্রে নরসিংদীর নাম ‘নরসিংগড়’ লেখা হতো। শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির ম্যাপে এরূপ লেখা রয়েছে। যদিও এ-অঞ্চলের অনেকের ধারণা, এখানকার লোকজন সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী বলে নাম হয়েছে নরসিংহদী। নরসিংহ অর্থ পুরুষ সিংহ বা সিংহ পুরুষ। আবার কারো মতে, বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার রূপ একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেন রাজারা শহরের কোনো একটি মন্দিরে। সেই থেকে এ-জায়গার নাম হয়েছে নরসিংহদী। প্রথমে নরসিংহডিহি। সংস্কৃত ভাষায় ‘ডিহি’ মানে ডাঙা। আবার ডিহি বলা হয় কতিপয় গ্রাম বা মৌজার সমষ্টিকে। অর্থাৎ নরসিংহদী বলতে মনে করা হয় যেসব গ্রাম বা মৌজায় সিংহের মতো পুরুষ বাস করে। নরসিংদী মূলত একটি উঁচু স্থল এলাকা। এজন্যে নরসিংদীতে বহু এলাকার নামের শেষে ‘দী’ যুক্ত আছে। এক পর্যায়ে ‘ডিহি’ থেকে ‘দী’ হয়ে গেছে।
জাতীয় অধ্যাপক ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নরসিংহ পাল নামের কথা বলেছেন। নরসিংদী নামকরণের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ান ও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ভিখনলাল ঠাকুর আঠারো শতকে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে বাস করতেন। তখন এলাকাটি ভিখনলাল ঠাকুরের বাজার নামে পরিচিত ছিলো। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এক সন্ন্যাসী একবার তাঁর বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসী ভিখনলালের আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে ৪ টি লক্ষ্মী নারায়ণ, দুটি নরসিংহ শিলা এবং একটি দক্ষিণমুখী শঙ্খ দান করেন। ভিখনলাল ঠাকুর দুটি লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার নামকরণ ভিখনলাল ঠাকুরের বাজারের পরিবর্তে লক্ষ্মীবাজার হয়। আরেকটি নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে। নারায়ণগঞ্জ নামের উৎপত্তি উক্ত নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠার কারণেই। বাকি লক্ষ্মী নারায়ণ, নরসিংহ শিলাগুলো ইদ্রাকপুর, পঞ্চমীঘাট ও বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। এর মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ শিলা ও শঙ্খ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পরিষ্কারভাবে জানা গেলেও নরসিংহ মূর্তি দুটি কোথায়, কখন স্থাপিত হয়েছিলো, সেটা আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে নরসিংহ মূর্তিটি নরসিংদীতে স্থাপিত হয়েছিলো এবং তা থেকেই নরসিংহ নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।
আবার নগর নরসিংহপুর থেকেও নরসিংদী নামের উৎপত্তির সূত্র খোঁজেন কেউ কেউ। নগর নরসিংহপুরের পাশেই নরসিংহের চর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থের মতে, এ-এলাকায় নরসিংহ ভট্টাচার্য্য নামে একজন বসতি স্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে হয়েছে নরসিংহের চর। নগর নরসিংহপুরের পাশে বেশ কয়েকটি চর সংযুক্ত গ্রাম রয়েছে। যেমন : ঢালুয়ারচর, সরকারচর, মাঝেরচর, বাড়ারচর, চরনগরদী। এছাড়া কাছাকাছি বেশ কিছু বিল এখনো রয়েছে। যেমন : সিংহের বিল, পৌদঘুরি বিল, শালধোয়ার বিল, কুড়াইতলী বিল ও বিভিন্ন জলাশয়।
সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ নরসিংদীকে ‘নরসিংহগড়দী’ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। যেমন : চরনগরদী গ্রামকে বলা হয়েছে চন্দ্রগড়দী বলে। জিনারদীর প্রাচীন নাম দীনার দ্বীপ ছিলো বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। একসময় চন্দ্রগড়দীর নামও চন্দ্রগড় দ্বীপ ছিলো। পলাশ ও শিবপুরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া হাড়িধোয়া তালতলী বাজারের উত্তর কোণায় এবং নরসিংদী সদর উপজেলার রাজাদী-চিনিশপুর প্রান্তে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে পলাশের চরনগরদী ও কালীবাজারের পাশে সংযুক্ত হয়। এ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়, এখানে একসময় নদী কেন্দ্রিক জীবনধারা ছিলো।
জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাজা নরসিংহের পুত্র রাজা ভগীরথ সিংহ, তাঁর পুত্র রাজা শ্রীধর সিংহ, তাঁর পুত্র রাজা কালিদাস সিংহ। তিনি হোসেনশাহী বংশের শাসনের শেষের দিকে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন এবং সোনারগাঁ অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম শাহ সুরের সেনাপতি তাজ খান কররানীর সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সোলেমান খাঁ’র দুই পুত্র ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ।
অবশ্য ঈশা খাঁ’র পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানা যায়, “মুঘল যুগে ভারতের যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জায়গাকে বায়সওয়ালা বলা হতো। ২২ টি পরগণার দু’হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বায়সওয়ালা রাজ্যটির অবস্থান ছিল। এই বায়স রাজপুত বংশের রাজা ধনপদ সিংহ ছিল দিল্লীর সম্রাটের মিত্র রাজা। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা ধনপদ সিংহের অধঃস্তন পুরুষ রাজা ভগীরথ সিংহের সাথে ঐ বংশের কালিদাস সিংহ সুলতান মাহমুদ শাহের রাজধানী গৌড়ে আসেন। তারা গৌড় তথা বাংলায় তীর্থ ভ্রমণ শেষে ভাগ্যান্বেষণে সুলতান মাহমুদ শাহের দরবারে হাজির হন। সুলতান কালিদাস সিংহকে সরকারের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী দেন। নিজ যোগ্যতা আর পরিশ্রমের ফলে রাজস্ব উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে, কালিদাস ব্রাহ্মণদেরকে স্বর্ণ হস্তি দান করেন এবং ‘গজদানী’ উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান খাঁ নাম ধারণ করেন। তিনি সৈয়দ বংশের শেষ শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করেন। শেরশাহের কাছে এই বংশের পতনের পর সোলায়মান খাঁ পূর্বে ময়মনসিংহ, ঢাকা জেলা, পশ্চিমে সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার অংশ নিয়ে ভাটি অঞ্চলের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন এবং সিংহাসনচ্যুত রাজপরিবারের অভিজাত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় আফগান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনিই এই বংশের প্রথম ব্যক্তি, যিনি অযোধ্যা থেকে বাংলায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।”
ঈশা খাঁর পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ, তাঁর পুত্র দেওয়ান মাসুম খাঁ, তাঁর পুত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁ। দেওয়ান মনোয়ার খাঁর পাঁচ পুত্র ছিলো। তাঁদের একজন দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)। মনোয়ার খাঁ’র জীবদ্দশায়ই তিনি মহেশ্বরদী পরগণার দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং মহেশ্বরদীতে নিজের আবাসিক এলাকা গড়ে তুলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বর্তমান নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত নগর মহেশ্বরদী গ্রামের শেষ প্রান্তে ‘গড়বাড়ী’ নামক স্থানটি ছিলো দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর আবাসিক এলাকা। এ-এলাকার চারপাশ ছিলো গভীর পরিখা ও উচ্চ মাটির প্রাচীরের বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত। এজন্যে স্থানটির নামকরণ হয় গড়বাড়ী। অবশ্য এই গড়বাড়ী নিয়ে মতবিরোধ আছে প্রচুর।
কেউ কেউ অনুমান করেন, এই গড়বাড়ী অনেক প্রাচীনকালে তৈরি। অবশ্য পক্ষে যুক্তি আছে যথেষ্ট। তবে গড়বাড়ী স্থানটি প্রাচীন হলেও পরবর্তী সময় দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) এ-সুরক্ষিত স্থানেই নিজের আবাসিক এলাকা গড়ে তুলেছিলেন। গড়বাড়ী বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে একটি বৃহৎ জলাশয়, জলাশয়ের উত্তর তীরে একটি উচ্চ স্থানের নাম কারখানার ভিটা। এ-ভিটার মাটির নিচে রয়েছে অসংখ্য স্তূপীকৃত ইট। ভিটার বর্তমান মালিক সম্প্রতি মাটি খননের সময় উদ্ধার করেন কয়েকটি লৌহনির্মিত তলোয়ার ও বর্শাফলক। অনুমান করা হয় যে, কারখানার ভিটা ছিলো জমিদার ঈশা খাঁ ও তাঁর বংশধরদের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হাতিয়ারপত্রগুলো এই কারখানায় তৈরি হতো। এ-ধারণা অমূলক নয়, কারণ প্রাচীন গ্রন্থ ‘আইন-ই-আকবরী’তে আবুল ফজল লিখেছেন, ঢাকা থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে ৩০ মাইল দূরে কোনো-এক স্থানে লোহা পাওয়া যায়। সে-স্থান থেকে সংগৃহিত লোহা দিয়ে বাংলায় নিয়োজিত মুঘল সৈন্যবাহিনির জন্যে হাতিয়ার তৈরি হতো। মহেশ্বরদী থেকে অনুমানিক দশ-পনেরো মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত লোহাদী থেকে সংগৃহিত লোহাই ব্যবহার করা হতো কারখানায় হাতিয়ার তৈরির জন্যে। তিনদিকে ব্রহ্মপুত্র ও একদিকে খরস্রোতা শীতলক্ষ্যা নদী বেষ্টিত এবং বনারণ্যে ঢাকা নগর মহেশ্বরদী ছিলো বিদেশি শত্রুর জন্যে প্রাকৃতিকভাবেই দুর্ভেদ্য। নিরাপত্তাজনিত কারণেই এরকম সুরক্ষিত স্থান নির্ধারণ করা হতো অস্ত্র কারখানা তৈরির জন্যে। দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর পূর্বপুরুষগণ কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে [কোনো বর্ণনায় ‘হযরতনগর’ আছে। তবে কিশোরগঞ্জে ঈশা খাঁ’র বংশবদ হযরতনগর রয়েছে। যার সাথে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্ক রয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রধান সেনাপতি সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীন (রহ.)-এর বংশবদদের] স্থায়ীভাবে বাস করলেও একমাত্র প্রশাসনিক সুবিধার জন্যেই তিনি মহেশ্বরদীতে বসবাস করতেন।
দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন জনৈক নাসেরের কন্যা জয়নব বিবি। (আরেকটি বর্ণনামতে, ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন ও তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বিবি জয়নবকে ঈশা খাঁ’র পঞ্চম অধস্তন পুরুষ দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর সাথে বিবাহ দেন এবং উপহার স্বরূপ মহেশ্বরদী পরগণার দেওয়ানী প্রদান করেন।) জয়নব বিবি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ পরহেজগার মহিলা ছিলেন। দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) সুফিদের সংস্পর্শে আসেন। ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন হন ও এলমে মারেফাত অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং দয়ালু ও নীতিবান মুসলমান।
এদিকে অল্প সময়ে নরসিংহপুর (পারুলিয়া) এলাকায় তাঁর ভক্তবৃন্দ ও গুণগ্রাহীও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের অনুরোধে ভ্রাতুষ্পুুত্রের নিকট মহেশ্বরদী পরগণার দায়িত্বভার অর্পণ করে নিজে সস্ত্রীক পারুলিয়ার কাচারি বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তাঁরা নৌকাযোগে এখানে এসেছিলেন। তাঁর নামানুসারে একসময় এটি ‘শরীফপুর’ হিসেবেও খ্যাত ছিলো। তখন এখানে পালতোলা নৌকা চলতো, যা দিয়ে মানুষ নদী পার হতো। স্থানটি শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযোগ রক্ষা করতো। লোকজন প্রচণ্ড স্রোত পেরিয়ে এই নদ পার হতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতো, “পার হইল/ পার হইলাম।” ‘পার হইল’ থেকে ‘পারৈল’, অতঃপর ‘পারুলিয়া’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আরেকটি মত হলো, এককালে এখানে অসংখ্য পারুল গাছ ও পারুলের দ্বীপ ছিলো। তদানুসারে নাম হলো পারুলের দ্বীপ-পারুদিয়া-পারুলদ্যা-পারুল্যা-পারুলিয়া। সময়ের বিবর্তনে এলাকাটি ‘পারুলিয়া’ নামে খ্যাত হয়। আবার দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর মোজেজা এবং ইসলাম প্রসারের ভূমিকায় তাঁর নামের আগে আউলিয়া যুক্ত হয়। যার ফলে ‘পীর+আউলিয়া’ থেকে ‘পারুলিয়া’ নামটি অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। পারুলিয়ার পাশেই একটি বাজার রয়েছে ‘সাধুর বাজার’ নামে। পূর্বকাল থেকেই এলাকাটি পীর-ফকির- দরবেশ-বাউল-সাধকদের উর্বর বিচরণভূমি ছিলো।
ঐতিহাসিক পারুলিয়া মসজিদ
দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) ও জয়নব বিবি ১১২৬ হিজরি (জাতীয় তথ্য বাতায়ন), ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে (বিভিন্ন বর্ণনায় ১১২৮ হিজরি, ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ, ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ দেয়া আছে, যা অন্য হিসাবগুলোর সাথে মিলে না) মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ নির্মাণে জয়নব বিবির বিশেষ ভূমিকা ছিলো বলে জানা যায়। ইরান, বাগদাদ ও ইয়েমেন থেকে কারিগর এনে মসজিদের নির্মাণ ও কারুকাজ করা হয়। এই মসজিদের সবুজ গম্বুজ দেখে মদিনার মসজিদে নববী এবং অলৌকিক মাহাত্ম্যের মসজিদে বনি হারামের কথা স্মরণ করেন অনেকে। ভারি ও মজবুত পাথরের খিলানের উপর তৈরি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যরে এ-মসজিদ মুঘল স্থাপত্যশৈলীর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মসজিদটির অভ্যন্তরের দৈর্ঘ্য ১৮.২৯ মিটার, প্রস্থ ৫.১৮ মিটার এবং মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ১.৫২ মিটার। দুটি ধনুক আকৃতির সমান্তরাল পথের মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরকে বর্গাকারভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগের উপরেই একটি করে গম্বুজ রয়েছে। প্রতিটি গম্বুজে নকশা ও অলঙ্কার খোদাই করা আছে। ব্যতিক্রম হিসেবে মসজিদের চারকোণায় অষ্টভুজ টাওয়ার রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির উচ্চতা কার্ণিশ পর্যন্ত। মসজিদটির মোট পাঁচটি ধনুক আকৃতির ফটকের মধ্যে পূর্ব দিকের দেয়ালে তিনটি, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি ফটক রয়েছে।

মসজিদের মাঝখানের ফটকটি অন্যান্য ফটকের চেয়ে বড়ো। মসজিদের মূল ফটকের বাইরের দিকটির উপরিভাগ অর্ধগম্বুজ আকৃতির ছাদের নিচে অবস্থিত, যেটি একটি আয়তাকার কাঠামোর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালে পূর্ব দিকের ফটকগুলো বরাবর তিনটি মিহরাব অবস্থিত। সবক’টি মিহরাব এবং ধনুক আকৃতির ফটকগুলো অলঙ্কারখচিত আয়তাকার কাঠামোর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। মিহরাব এবং ফটকের উভয় দিকেই ধনুক আকৃতির কোটর রয়েছে। ফটকগুলোর বাইরের অংশে বর্গাকার এবং আয়তাকার নকশা রয়েছে। মসজিদের সামনে বর্গাকার আঙিনাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের পূর্ব দিকে একটি চমৎকার ফটক রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুটি পুকুর মসজিদ অঙ্গনকে ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি মসজিদের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।
পারুলিয়া মসজিদের সৌন্দর্য ও কারুকার্য আজো নরসিংদী তথা দেশের যেকোনো মসজিদ থেকে অনন্য। মূল প্রবেশ দরজার উপরিভাগে স্থাপিত পাথরের শিলালিপিতে ফারসি ভাষায় কবিতার ছন্দে লিপিবদ্ধ আছে মসজিদটির নির্মাণ ইতিহাস। স্মৃতিফলকে লেখা আছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” কর্দে জয়নব বিনতে নাছের জজায়ে দেওয়ান শরীফ ও নির্মাণ সময়। ১৮৯৭ (কোনো বর্ণনায় ১৯০৪) সালের ভূমিকম্পে মসজিদটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮৯ সালে এবং ২০১২ সালে মসজিদটি পুনরায় সংস্কার করা হয়।
১১২৮ হিজরিতে দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) ইন্তেকাল করেন। তার একবছর পর ১১২৯ হিজরিতে জয়নব বিবিও ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর পাশে জয়নব বিবিকেও সমাহিত করা হয়। বর্তমানে স্থানটি দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) ও জয়নব বিবির যুগল মাজার হিসেবে পরিচিত।

প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর মসজিদ ও মাজার অবস্থিত। একসময় তাঁদের ঘোড়া ছিলো। চারটি পুকুর এখনো রয়েছে। কাচারিঘর, রান্নাঘরসহ অন্য স্থাপনার তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই। হুজরাখানার উত্তর দিকে নায়েব সাহেবের কাচারি ও বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ আজকাল দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এখানে একসময় ছিলো সুরম্য অট্টালিকা। মাজারের পশ্চিম দিকে একটি প্রবেশ তোরণ ও সুরম্য দেয়ালের কিছু অংশ এবং একটি অতীব মূল্যবান কালো পাথর এখনো রয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী লোক বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে ইট-পাথর তুলে নিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে আর আবাসিক এলাকাটি পরিণত করেছে ধানের জমিতে।
এই নিষ্কর জমির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বত্ব নিয়ে নরসিংদী জজ কোর্টে একটি মামলা রুজু হয়। বংশতালিকায় নরসিংহের নাম দেখে স্বভাবতই ধারণা করেন যে, রাজা নরসিংহের নাম থেকেই নরসিংহদী তথা নরসিংদী নামের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। যদিও নরসিংদীর প্রাচীন নাম নিয়ে আজো ধোঁয়াশা কাটেনি। সেহেতু নরসিংদী নামের উৎপত্তি ও প্রকৃত ইতিহাস হয়তো এখনো অজানাই রয়ে গেছে।
আরেকটি মজার বিষয় আছে ঘোড়াশাল কেন্দ্রিক। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সেই এলাকার টেকপাড়ায় শেখ গোলাম মোহাম্মদ নামে এক ক্ষমতাধর বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করতেন। দিল্লীর রাজদরবারেও তাঁর নাম সুপরিচিত ছিলো। ঐ-সময় দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) শরীফপুরের জমিদার হয়েও স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কর পাওয়া ব্যতিত জমিদারির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মুঘল সম্রাটের হস্তক্ষেপ করার তেমন নজির ছিলো না।
এখানকার এক ধুরন্ধর প্রজা দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর বিরুদ্ধে দিল্লীর রাজদরবারে এক গুরুতর অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের বিচারকে কেন্দ্র করে জমিদার দেওয়ান শরীফ খান (রহ.)-এর সাথে দিল্লীর রাজদরবারের চরম বিরোধ দেখা দেয়। দিল্লীর সম্রাটের লিখিত ফরমানে শেখ মোহাম্মদ উক্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করে দিল্লীর সম্রাটের সাথে দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর সন্ধি করে দেন। শেখ গোলাম মোহাম্মদের এ-কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতায় সম্রাট আওরঙ্গজেব ও দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) উভয়ই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এ-কাজের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট আওরঙ্গজেব শেখ গোলাম মোহাম্মদকে একটি তেজি ঘোড়া ও মূল্যবান শাল উপহার দেন।
জমিদার দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-ও স্বীয় পালিত কন্যা চাঁদ বিবিকে শেখ গোলাম মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র শেখ গোলাম নবীর সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের উপহার স্বরূপ চরপাড়া, টেকপাড়া, টেংগরপাড়া, বিনাটি, করতেতৈল, রাজাব ও চামরাব নামে ক্ষুদ্র পল্লীগুলো প্রদান করেন। সম্রাট প্রদত্ত ঘোড়া ও শাল দেখার জন্যে দলে দলে লোকজন শেখ গোলাম মোহাম্মদের বাড়িতে আসতো। আগন্তুকগণকে ‘কোথায় যাও’ প্রশ্ন করা হলে তারা বলতো, ঘোড়া এবং শাল দেখতে যাই। সেই থেকে শেখ গোলাম মোহাম্মদের বাসগ্রাম ও বিবাহের উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র গ্রামগুলোর সমষ্টিই ‘ঘোড়াশাল’ নামে পরিচিত হতে থাকে এবং তাঁর পুত্র গোলাম নবীর সময় এলাকাটি ‘ঘোড়াশাল’ নামে অভিহিত হয়।
ঘোড়াশাল দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চল। এ-এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীর বসবাস। দেওয়ান শরীফ খাঁ (রহ.) জিনারদী তথা সেই এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন জিনারদী কালী মন্দিরটি ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিভূজ আকৃতির অনন্য নকশায় নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত পারুলিয়া মসজিদ ও জিনারদী কালী মন্দিরের নির্মাণ একই সময়ে শুরু হয়েছিলো। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে পালনের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় আজ অবধি অঞ্চলটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন বজায় রেখে চলছে।
পারুলিয়া মসজিদ সম্পর্কে বহু মিথ প্রচলিত আছে। বলা হয়, মসজিদটি গায়েবিভাবে নির্মিত। লোকেদের বিশ্বাস, তখনকার সময় এই এলাকায় কোনো বিয়ে-শাদিসহ কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে যাবতীয় হাড়ি-পাতিল-বাসন- কোসন মসজিদের লাগোয়া পুকুর থেকে গায়েবিভাবে পাওয়া যেতো। ব্যবহারের পর আবার পুকুরে রেখে দিতে হতো। একবার এক মহিলা লবণের কৌটা চুলের বেণীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনদিন পর্যন্ত এটা ফেরত না দেয়ায় স্বপ্নে কঠোর পরিণতির বার্তা দেয়া হয়। এরপর তা ফেরত দিলে সেই যে গায়েবি জিনিসপত্র পানিতে মিশে যায়, তারপর থেকে কখনো আর অনুষ্ঠানের সামগ্রী এখানে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখানে একটি বিশেষ বৃক্ষ (বাঞ্জা/বাঞ্ছা) গাছ ছিলো, যার পাতা-ছাল খেলে মানুষের রোগ-বালাইসহ মনোবাঞ্ছা পূরণ হতো। যুগে যুগে এগুলো মানুষের মুখে মুখে জনশ্রুতি হয়ে আছে।
সম্ভবত নরসিংদী জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বয়স্ক কাঠাল গাছগুলোর একটি মাজারের পাশে এখনো রয়েছে। পাশের পুকুরে একসময় বিরল প্রজাতির মাছ পাওয়া যেতো। এখানে সব ধর্মের-বর্ণের মানুষ আসেন। প্রতি বছর ১৭ ফাল্গুন থেকে তিনদিনব্যাপী বাৎসরিক উরস মাহফিল হয়। কোনো-এক কারণে এ-বছর উরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক মাহফিল হয়। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী এখানে আসেন। এখানে আসাও খুব সহজ। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভেলানগর ও পাঁচদোনা এবং ঘোড়াশাল থেকে সিএনজি দিয়ে সহজেই এখানে আসা যায়। ট্রেনেও নরসিংদী কিংবা ঘোড়াশাল স্টেশন থেকে আসা যায় সহজেই।
আজো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন হিসেবে পারুলিয়া মসজিদ ও মাজারটি কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক পারুলিয়া মসজিদ সংরক্ষণ, পুকুর সংস্কার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উন্নয়ন ও দৃষ্টিনন্দন করতে রাষ্ট্রের পরিকল্পিত ভূমিকা প্রয়োজন।
তথ্যসূত্র
১. নরসিংদীর নামকরণ নিয়ে বিতর্ক, আপেল মাহমুদ;
২. নরসিংদীর ইতিহাস-এতিহ্য, আব্দুর রশীদ;
৩. নবম পরশ নরসিংদী জেলা নির্দেশিকা, এম. এ. আসাদ ভূঞা সম্পাদিত;
৪. সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীন (রহ.), এস. এম. ইলিয়াছ;
৫. জাতীয় তথ্য বাতায়ন;
৬. উইকিপিডিয়া;
৭. ‘বিবিসি’সহ বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল;
৮. ঘোড়াশাল ভাস্কর্য;
৯. মাজারের প্রবীণ ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থীর বক্তব্য।
মো. জাকারিয়া
কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
গবেষণা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, নরসিংদী