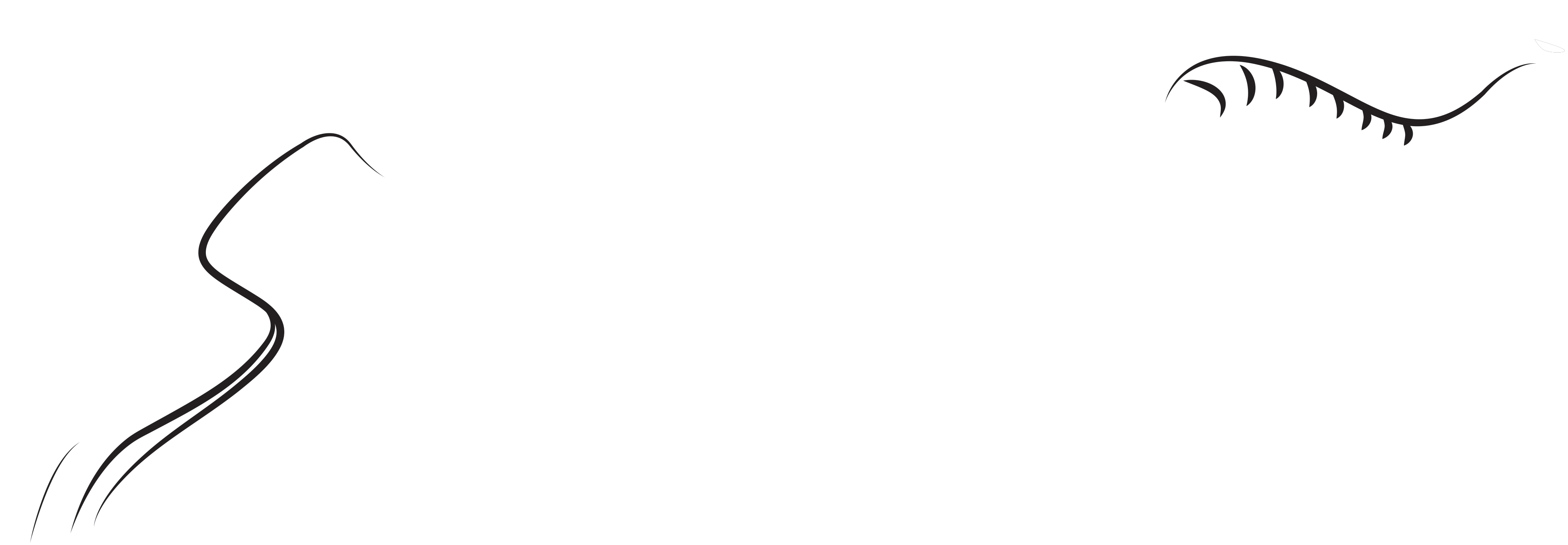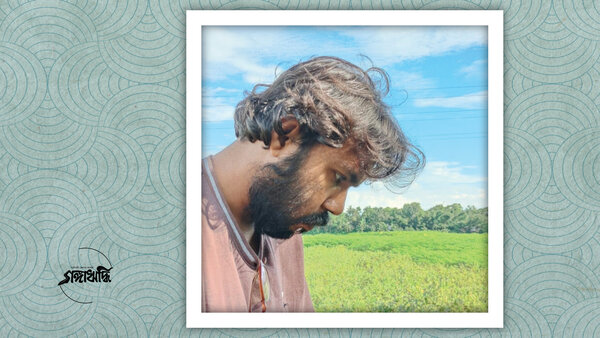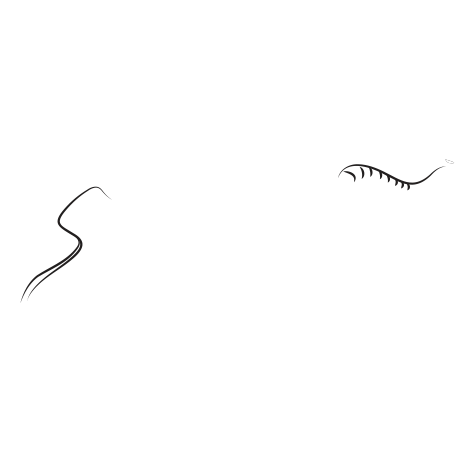আমরা দাঁড়িয়ে আছি মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের মুখোমুখি হয়ে। আমাদের পাশে আমাদের বন্ধুর মৃতদেহ অথবা আমাদের বন্ধুর মৃতদেহের পাশে আমরা। যেমন আমরা পাশাপাশি বসেছি অনেকদিন অথবা দিনের পর দিন। আমরা ভাবছি, আমাদের সময়গুলোকে যেভাবে আমরা ভাবতে শিখেছিলাম কিংবা শিখেছিলাম চিন্তাগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখতে। আমরা বেড়ে ওঠতাম, অশ্বত্থ গাছের তলায় যেভাবে বেড়ে ওঠতো নকশা করা পাতাঅলা গাছ। আমরা বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হতাম আমাদের নিজস্ব কায়দায়। কিন্তু জানাজার নেতৃত্বদানকারী ইমাম সাহেবের অপরিচিত ছিলাম সামাজিক সামষ্টিক কায়দার কারণে। তিনি চিনতে পারতেন না রিপন ইউসুফকে, বিগত দিনগুলোতে এমনকি তার প্রয়াণ দিবসেও। তিনি চিনতে পারেননি আমাদেরকেও, যারা এসেছি এলাকার বাইরে থেকে। তার মতো সবাই তাকে চিনতো এলাকাবাসী হিসেবে, যার বাবা তার মতো অকালপ্রয়াত হয়েছিলেন বেশ আগেই। কিন্তু আমরা চিনতাম আমাদের বন্ধুকে, যে অনুধাবন করেছিলো যে, ‘আগন্তুক’ সিনেমার মামার মতো আমাদের একসাথে বসে আড্ডা নামক বস্তুটির গতিপথটি ঠিক কোনদিকে হওয়া প্রয়োজন এবং আমরা ঠিক কোনদিকে আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে যাবো। তখন আমাদের বাকিদের হয়তো এতো অল্প বয়সে ‘প্রয়োজন’ শব্দের ওজনের মানদণ্ড গজিয়ে ওঠেনি, তাই আমরা হয়তো এর ভার ঠাহর করে ওঠতে পারিনি। আমাদের বাকিদের কাছে এই ‘প্রয়োজন’ শব্দটি ছিলো এক-আধটু বই পড়া বা ভিনদেশি সিনেমা দেখে অন্যদের থেকে নিজেকে একটু আলাদা করার প্রক্রিয়া। সোজা কথায় যদি বলি, একটু লোকেদের দেখানো যে, দেখো, আমরা কেমন জাতে উঠছি! কথাটাকে ‘শোঅফ’ বলে দিলে সবার ধরতে হয়তো সুবিধা হয়। কিন্তু রিপন ইউসুফ হয়ে ওঠছিলো সবার চেয়ে আলাদা। নিজের বোধশক্তির উন্নতির জন্যে ছিলো রিপন ইউসুফের এই যাত্রা। এই যাত্রায় রিপন ইউসুফ যে-আলো জ্বেলেছিলো, বাকি বন্ধুদের মতো সেই আলো প্রবেশ করেছিলো আমার চোখেও। সেই আলোতে আমি বুঝতে চেয়েছি, আমরা কেন রিপন ইউসুফ হয়ে ওঠি।
তার সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য ছিলো জীবনকে নিবিড়ভাবে জানা, আরো বিশেষভাবে বললে এই অঞ্চলের আদি মানুষের সরল জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ। এই বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যও ছিলো তার। এই বিষয়ে তার জোরালো বক্তব্যও ছিলো। তার মতে, এখানকার আদি মানুষের সঠিক ইতিহাস না জানলে এখানকার মানুষকে কখনোই বোঝা যাবে না আর এখানকার মানুষকে না বুঝলে মানুষের জন্যে যেকোনো উন্নয়নই মানুষের কোনো কাজে আসবে না।
আমার বন্ধু রিপন ইউসুফ সদ্যপ্রয়াত। এই প্রেক্ষিতে সামগ্রিক স্মৃতিচারণ আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং আলবেয়র কাম্যু’র মুরসাল্টের মতোন রিপন ইউসুফ কোনো চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলো কি না, যে প্রচলিত সত্যের বাইরে কোনো গভীর সত্যের প্রতি টান অনুভব করতো; যেটা নিশ্চিতভাবেই কোনো দায়বদ্ধতা না হয়ে শুধুই একটা টান অনুভব থেকেই হতো।
নিষ্ঠুর রসিকতার জন্যে সে ছিলো একদমই আলাদা। যেকোনো বিষয়ে তার রসিকতা অনেক সময় মানুষকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করেও দিতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেটা নিষ্ঠুরতার মাত্রা ছাড়িয়ে ব্যক্তিকে বিষাদগ্রস্ত করে দিতো। এখানে একটা বিষয় ভাবার থাকে, এই নিখাদ রসিকতার পেছনে রিপন কতোটা দায়ী ছিলো অথবা যাকে নিয়ে এসব রসিকতা করা হতো, তারা নিজেরা কতোটা দায়ী ছিলো। তাদের ভাঁড়ামির বিপরীতে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় রিপন ইউসুফের কাছে আসা এবং তার বিপরীতে প্রাঞ্জল রসিকতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আত্মপক্ষপাতদুষ্ট না হলে হয়তো তারা নিজেদের ভাঁড়ামি অতিক্রম করে নিজেদেরকে নির্মাণের সুযোগ দিলেও দিতে পারতো। রিপন ইউসুফের আয়নায় তাদের নিজেদেরকে দেখার ব্যর্থতা কি রিপন ইউসুফের আয়নার অস্বচ্ছতা নাকি তাদের নিজেদেরকে না দেখার প্রকাণ্ড অনিচ্ছা, তা বুদ্ধিমানদের কাছে প্রশ্ন রাখা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেচে রসিকতা করার উদাহরণ রিপন ইউসুফের ক্ষেত্রে বিরল। ব্যক্তি রিপন ইউসুফের এই বিতর্কিত গুণটি তাকে অন্যদের থেকে সমাজে আলাদা ও প্রাসঙ্গিক করেছে নিশ্চিত রূপেই। রিপন ইউসুফ সকলের কাছে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়ে ওঠেছিলো একজন চলচ্চিত্র বোদ্ধা হিসেবে। যদিও তার সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যের পাঠ চলছিলো সমানতালেই। সিনেমা নির্মাণ বিষয়ে পরিকল্পনা ছিলো তার বেশ আগে থেকেই। পাশাপাশি চলছিলো প্রস্তুতি। আমার মতো অনেকেরই ভিন্ন দেশের ভিন্ন রূপের সিনেমার পরিচয় হয়তো রিপনের কাছ থেকেই। প্রথম বয়সে সিনেমা নির্মাণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়োজন থাকলেও হয়তো সেটা বাস্তব হয়ে ওঠতো না বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে। সেই সীমাবদ্ধতার ছিলো বিবিধ কারণ, যে-বিষয়ে আমি লিখতে অনিচ্ছুক।
সিনেমাটোগ্রাফি বিষয়ে চমৎকার ধারণা ছিলো তার। বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলো সে এই বিষয়ে। সিনেমা নির্মাণের টানে মফস্বল পেরিয়ে রাজধানীতে গেলেও সেখানকার পেশাদারদের কাজ এবং কাজের মান নিয়ে তার ছিলো হতাশা। যে-মানের কাজ রিপন দেখতে চাইতো বা কাজ হবে বলে মনে করতো, সেই মানের কাজ সেখানে সে পায়নি। নিরাশ হতে হয়েছিলো তাকে। ‘ঘুড়ি’ ও ‘যিশু আপনি কোথায়’ নামক দুইটি শর্টফিল্ম করার চেষ্টা করে। তারপর হাত দেয় শর্টফিল্ম ‘রাস্তার কোণার লোক’ বানানোর কাজে। চমৎকার গল্প আর চিত্রনাট্য থাকলেও যে-সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়, তা হলো কারিগরি ও বাজেট দুর্বলতা। সিনেমাটির গল্প সূক্ষ্ম মেকআপ এবং ফিনিশিংয়ের দাবি রাখতো। সেখানে অপ্রতুল বাজেট এবং মেকআপ সুবিধার কারণে বেশকিছুটা খাপছাড়াও লেগেছিলো। বাজেট যদি আরো বেশি থাকতো, তবে হয়তো তা সত্যজিৎ রায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ না হলেও ঋতুপর্ণর ‘হীরের আংটি’ হয়ে ওঠতে পারলেও পারতো। রিপন ইউসুফের নিজের কাজের প্রতি খুব বেশি আত্মতুষ্টি ছিলো না কখনোই। সিনেমা হচ্ছে এমন একটি শিল্প, যেখানে অনেক লোকের পরিশ্রম একত্রিত হয়ে সিনেমা আকারে রূপ নেয়। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের অনীহা ও আলসেমি রিপন ইউসুফের সিনেমা বিষয়ক প্রতিভা ও জ্ঞানকে বঞ্চিত করেছে নিশ্চিতভাবেই। তবে তার সিনেমা বিষয়ক অগাধ জ্ঞান স্রেফ তার সিনেমার প্রতি অনুরাগের ফসল বলেই আমার মনে হয়। সিনেমা পরবর্তী সময়ে সাহিত্য হয়ে ওঠেছিলো তার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় ছিলো তার বিচরণ। উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা, ইতিহাস, প্রবন্ধÑ সবই ছিলো তার পাঠের বিষয়। তার ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ দেখলে তা সহজেই বোঝা যায়। এমন না যে, শুধু বই সংগ্রহ করতো সে, বই সে পাঠও করতো। তার সংগ্রহে থাকা এমন বই খুব কমই আছে, যা সে পড়েনি। আমাদের পরিচিত একজন লোক ছিলেন, যার সংগ্রহে অনেক বই ছিলো। রিপন ইউসুফের তার বইয়ের উপর বেশ লোভ ছিলো এবং সেই লোকের মৃত্যুর পর তার বইয়ের সংগ্রহের উপর তার একটা বাসনা ছিলো। কারণ সেই লোকের সন্তানেরা বই তেমন পড়ে না, তারচেয়ে রিপন বইগুলো নিয়ে নিলে অনেকদিন ধরে এগুলো সে পাঠ করতে পারবে। যদিও-বা এগুলো ছিলো স্রেফ কথার কথা। আমার এই ঘটনার উল্লেখ করা শুধু এটা বোঝানোর জন্যে যে, পার্থিব জীবনে রিপন ইউসুফের আকর্ষণের বিষয় ও বস্তুটি তুলে ধরা। যদিও হায়, এখন রিপন ইউসুফের সংগ্রহের বই নিয়ে কী করা হবে, তা আমরা বন্ধুরা ভাবছি। এখনো আমরা এই তল্লাটে তার বইয়ের উপর লোভ করা কাউকে খুঁজে পেয়েছি কি? সাহিত্যের ছোটোগল্প ও কবিতার প্রতি তার অনুরাগ ছিলো বিশেষ। সাহিত্যের প্রায় সব জায়গায় তার নিবিড় পাঠ থাকলেও ছোটোগল্প ও কবিতা লেখার বিষয়ে সে ছিলো বিশেষ আগ্রহী। তার কবিতার মাঝখানে লাতিন সাহিত্যের গন্ধ পাওয়া যেতো। লেখাগুলো কেমন তার নিজের লেখারই অনুবাদ মনে হতো। এটাকে হয়তো সাহিত্যে নতুন কিছু করার প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। কবিতা লেখার পর কিছু কবিতা সে আমাকে পাঠ করতে দিতো। কিছু কিছু কবিতার চিত্রকল্প নির্মাণ ছিলো বেশ জোরালো ও সচেতন। কবিতার সচেতন নির্মাণে রিপন ইউসুফ ছিলো অতীব মনোযোগী। শব্দের ভারিক্কিহীন ব্যতিক্রমী প্রকাশ রিপন ইউসুফের কবিতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো কবিতার মাঝে রিপন ইউসুফের নিজস্বতার ছাপ অর্থাৎ কবিতা পড়তে দিলে নাম না দেখেই বলে দেয়া যেতো, এটা রিপন ইউসুফের কবিতা। ছোটোগল্পের ব্যাপারে তাকে বেশ নিরীক্ষাধর্মী লেগেছে। কবিতার মতো গল্পের ক্ষেত্রেও সে তার নিজস্বতার ছাপ রাখতে পেরেছে বলেই আমার মনে হয়। তার কিছু ছোটোগল্প আমার কাছে ভালো লেগেছে। তার একটা গল্প আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছিলো। গল্পটি ছিলো এক যুবক আর একটি বিড়ালকে কেন্দ্র করে। গল্পটিতে চরিত্রের পরিবর্তন বেশ চমকপ্রদ ছিলো। গল্পটি প্রথম পাঠেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এবং তাকে এটা জাতীয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় ছাপানোর পরামর্শ দিই। তখন সে আমাকে জানায়, সে আরো কিছু গল্পসহ বই প্রকাশ করতে চায়। তার লেখার সমালোচনার বিপরীতে তার প্রতিক্রিয়া কিছুটা তীব্র ছিলো। তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়াই হয়তো এর কারণ ছিলো। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, তাকে ইচ্ছে করে রাগান্বিত করার জন্যে আবোল-তাবোল কিছু সমালোচনা করে দিতাম… ওই যে, নিষ্ঠুর মজা…! আমরাও কি কম করেছি? যা-ই হোক, হয়তো গল্পগুলো বই আকারে প্রকাশিত হলে পাঠকের তা ভালো লাগতেও পারে।
তার কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী লেখাও আছে, যা এখানকার ইতিহাস-সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ। সেই বিশ্লেষণ ছিলো সুচিন্তিত ও প্রাসঙ্গিক। এই ধরনের লেখায় তার রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশ পায়। তার রাজনৈতিক চিন্তায় সে এমন একটি ‘টানেল’ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতো, যেখানে আপনি যে-মতবাদেই বিশ্বাস করেন না কেন, আপনাকে নিয়ম মেনে সেই টানেলে ঢুকতে হবে এবং নিয়ম মেনে অন্যের অসুবিধা না করে আপনার নিজস্ব বিকাশ ঘটাতে হবে। চিত্রনাট্য লেখার একটা চিন্তাও সে করেছিলো। লিখেছিলোও একটা। তবে সব ছাপিয়ে একটা বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত, তার সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য ছিলো জীবনকে নিবিড়ভাবে জানা, আরো বিশেষভাবে বললে এই অঞ্চলের আদি মানুষের সরল জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ। এই বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যও ছিলো তার। এই বিষয়ে তার জোরালো বক্তব্যও ছিলো। তার মতে, এখানকার আদি মানুষের সঠিক ইতিহাস না জানলে এখানকার মানুষকে কখনোই বোঝা যাবে না আর এখানকার মানুষকে না বুঝলে মানুষের জন্যে যেকোনো উন্নয়নই মানুষের কোনো কাজে আসবে না। এখানকার তান্ত্রিক জীবনের পদ্ধতির বিস্তারিত ছিলো তার গবেষণার বিষয়। তার মতে, তান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থাই এখানকার আদি এবং প্রাসঙ্গিক জীবন ব্যবস্থা। এটি হারিয়ে যায়নি বরং তান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান আছে বিচ্ছিন্নভাবে। এই জীবন ব্যবস্থাকে কেবল ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে এর নিবিড় পাঠ ও প্রয়োগের মাধ্যমে। সে মনে করতো, এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো আর্যরা, যারা এখানে দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছিলো এবং এখানকার বিদ্যমান তান্ত্রিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো বিভিন্ন ঈশ্বর ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এবং এখানকার আদি বাসিন্দারা পাহাড়ে বা দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও তারা কিছুটা সেই ব্যবস্থা ধারণ করে। তাদের মাতৃতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা এই তান্ত্রিক জীবনের একটি অন্যতম দিক, যেখানে একজন নারী পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেন। তদের জীবন ব্যবস্থার কিছু চমকপ্রদ বিষয় সে আড্ডায় তুলে ধরতো। এছাড়া ইউরোপীয় খাপছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে আমাদের গুরুমুখী শিক্ষার প্রাণনাশ করলো এবং এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মাঝে কীভাবে কেরানি মানসিকতা উৎপাদন করছে আর এই উৎপাদিত মানসিকতা কীভাবে আমদানি করছে পশ্চিমের অযাচিত চাহিদার জঞ্জাল, তা আড্ডায় আলোচনা করতো। এসবই ছিলো তার বিস্তর পাঠের ফসল, যা উৎপাদিত হয়েছিলো কেবল পাঠের প্রতি ভালোবাসা থেকে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তার কখনোই আস্থা ছিলো না। দশম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছিলো সে। অংক এবং হিসাববিজ্ঞানে। ফলে পরের বছর এসএসসি দিতে হয়। এইচএসসিতে সারাদিন কলেজের বাইরে বাইরে বদরপুর থেকে বুধিয়ামারা ঘুরে বেড়াতো বন্ধুদের সাথে আর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আর আড্ডা চলতো। ফলাফল যা হবার, তা-ই হলো, অই কোনোরকম পাশ। ভর্তি হলো শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটিতে ফ্যশন ডিজাইনের ছাত্র হিসেবে। টিকলো না সেখানে। তারপর স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজে। সেখান থেকেও চলে এলো, গ্রাজুয়েশন হলো না। আমি বললাম, গ্র্যাজুয়েশন করলি না, এখন ভদ্রঘরের মেয়ে দিবে তোকে কেউ? উত্তরে হাসতো আর বলতো, আরে খোক্কা, যখন লাগবে, ঠিকই বিয়ে করে নেবো। বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলো একবার, একটা বায়োডাটা তৈরি করেছিলো। আমাকে দেখালো, আমি দেখলাম পেশার ঘরে লেখা : লেখক ও সম্পাদক। আমি পেট ফাটিয়ে হাসলাম আর বললাম, এই বায়োতে বিয়ে হবে না, সংশোধন করতে হবে। লিখতে হবে দলিল লেখক ও সাধারণ সম্পাদক, তাহলেই বিয়ে হতে পারে।
রিপন ইউসুফ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেছিলো এক জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি। কেউ যদি ব্যক্তিবিদ্বেষ এবং তর্কের জন্যে তর্ক করতে না চায়, তাহলে তাকে এই কথাটা মানতে হবে। যদিও কথাটা সিদ্ধান্ত এবং স্পর্শকাতর বিষয়, তবু হ্যাঁ, আমাকে এখানে পৌঁছুতেই হয়। সে আমাদের মধ্যে বহু অপরিচিত ও অপ্রচলিত আলাপ ও চিন্তা জারি রেখেছে। তার এই অপ্রচলিত চিন্তা বর্তমানে ব্যাপক প্রচলিত ব্যবস্থার বিপক্ষে একটি শক্ত ধাক্কা নিঃসন্দেহে। আর এই প্রচলিত অসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে আমরা যখন আমাদের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করি, তখন আমরা প্রকারান্তরে রিপন ইউসুফই হয়ে ওঠি। রিপন ইউসুফ কেবল আমাদের বন্ধুরই নাম নয় বরং একটি চিন্তার নাম। সে মনে করতো, আমাদের এই অঞ্চলে ইন্টেলেকচুয়াল মানুষের বড়ো ঘাটতি। এখানকার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা সবলভাবে দাঁড়ায়নি। এখানকার সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা তার কথার স্বপক্ষে শক্ত প্রমাণ। আমরাও যখন এই দুর্যোগ সমভাবে অনুভব করি, তখন হ্যাঁ, আমরাও রিপন ইউসুফ হয়ে ওঠি।
নাজমুল শাহরিয়ার কবি