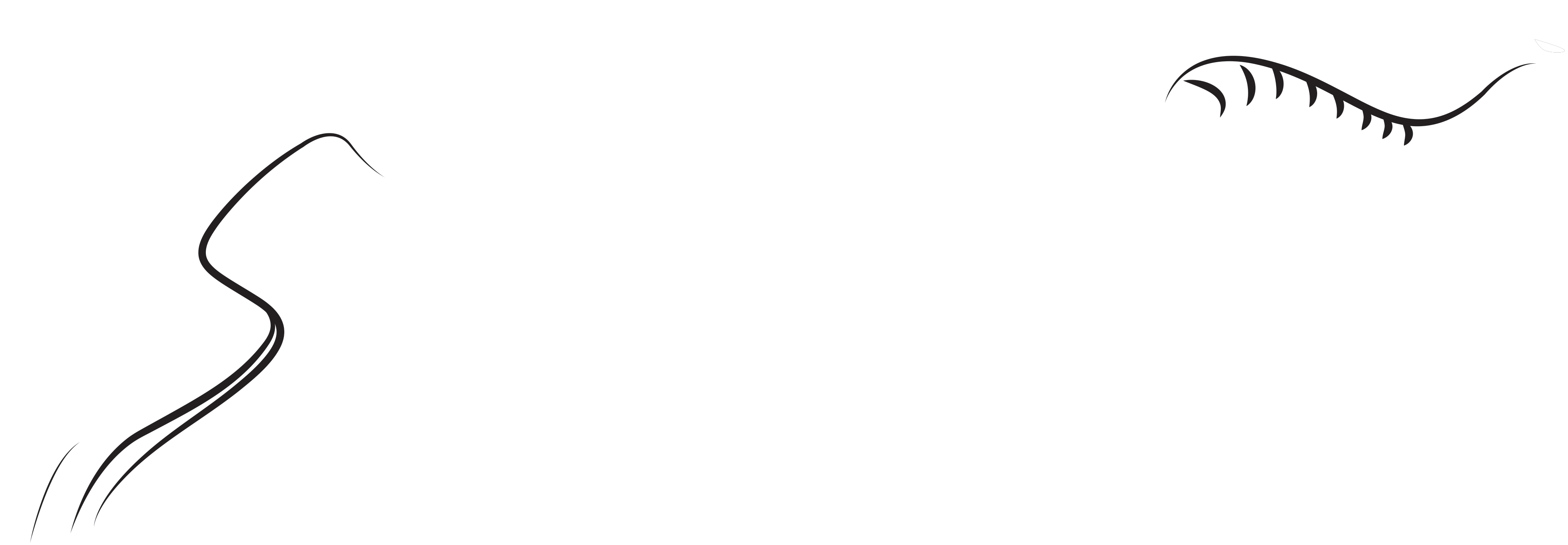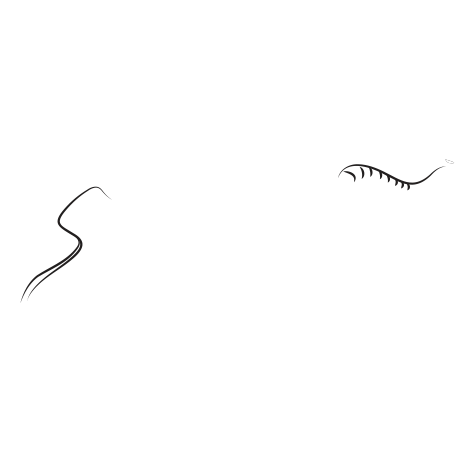হরিপদ দত্ত। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক। বর্তমানে তিনি পশ্চিবঙ্গের নদীয়া জেলায় বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্যে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে আসেন। ৯ জুন ২০২৩ (শুক্রবার) তাঁর এই সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন শহিদুল হক সুমন ও সুমন ইউসুফ।
আপনি দেশে আসার পর থেকে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়েছেন। সবাই একটা প্রশ্ন আপনাকে করেছে। আমিও আমাদের পাঠকদের জন্যে প্রশ্নটি পুনরায় করতে চাই। সেটি হলো, আপনি দেশ ছেড়েছেন কেন?
হরিপদ দত্ত : আসলে বাংলাদেশের অন্য আট–দশজন হিন্দু যেসব কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়, আমি কিন্তু সেসব কারণের শিকার নই। আমাদের যে–এলাকা, সেটি ছিলো একদম কৃষিপ্রধান। তারা কৃষিকাজ ছাড়া আর কিছুই পারে না। সেখানে ইউরিয়া সারকারখানা প্রায় সব কৃষিজমি নিয়ে নেয়। ফলে সেখানকার মানুষজন উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। পুরো একটা গ্রাম ভেঙে যায়। সময়টা ছিলো খুব খারাপ। ১৯৬৪–৬৫। দাঙ্গা হলো। ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ হলো। এরকম পরিস্থিতিতে একটা বিরাট দ্বিধা–দ্বন্দ্বের ভেতর পড়লো সংখ্যালঘুরা। অনেকে অনেক জায়গায় চলে গেলো। আমাদের কিন্তু সেরকম যাওয়ার বিষয় ছিলো না। কৃষিজমি হারিয়ে ভূমিহীন অবস্থায় আমার পরিবার ভারতে চলে যায়। তবে আমি যাইনি। কিন্তু শেকড়ছেঁড়া একটা মানুষের যা হয়, একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমার স্ত্রী–সন্তানদের কোথায় রাখবো, এই চিন্তা করতে করতে তাদেরকেও পাঠিয়ে দিলাম। আমি রয়ে গেলাম বাংলাদেশেই। তারপর ২০১২ সালে এসে আমি দেশ ছাড়ি। আমি জানতাম না যে, আমার কিডনির সমস্যা হয়ে গেছে। আসলে অসুস্থতার জন্যেই আমাকে ভারতে যেতে হয়, বাধ্য হয়ে, পরিবারের কাছে। তবে চিরতরে যাবার জন্যে নয়, চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবো বলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু অসুস্থতা বেড়েই চললো। নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়েছিলো। আবার পাসপোর্টের জটিলতায় পড়লাম। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাই আর আসতে পারিনি। তাছাড়া আমার কোনো সম্পত্তি নেই। না বাংলাদেশে, না ভারতে। সেই যে সারকারখানা আমাদের ভূমিহীন করলো, সেই থেকে এখনো ভূমিহীনই রয়ে গেলাম। আমার বাবা–কাকার শত শত বিঘা জমি ছিলো, সব সারকারখানা দখল করে নিলো। তো এরকম পরিস্থিতিতে আমার সন্তানেরাও আমাকে ছাড়তে চাইলো না। তারা সেখানে শিক্ষকতা করে। এখন প্রকৃতপক্ষে তাদের উপরেই আমি নির্ভরশীল।
সেখানকার কোনো পত্র–পত্রিকায় লেখা দেন? বা কোথাও ছাপা হয়েছে এখনো পর্যন্ত?
হরিপদ দত্ত : না না। এটা আমি আগেও বলেছি, ভারতের কোনো পত্রিকায় লেখার জন্যে তো আমার জন্ম হয়নি। আমার জন্ম হয়েছে খানেপুর গ্রামে, শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে, এই বাংলার মাটিতে। আমার এই ঋণটা তো শোধ করতে হবে। আমার চলে যাওয়াটা ছিলো একধরনের বিট্রেয়ারের কাজ, বিশ্বাসঘাতকের কাজ। আমার মাতৃভূমি ও মানুষের জন্যে আমার যা করণীয়, সেগুলো না করে তো আমি চলে গেছি। বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, জনতা— আমাকে তাড়িয়ে তো দেয়নি তারা। আমি নিজে তা স্বীকার করি। কিন্তু ক্ষমা চাই না। ক্ষমা কী আর! এর ফল তো আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি। এ–বছরেরই ১৮ ফেব্রুয়ারি আমি বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশে ঢুকতে পারিনি। এর অন্যতম কারণ হলো, বিশ্বাসঘাতকদের তার মাতৃভূমি দ্বিতীয়বার জায়গা দেয় না। আর এই কারণেই আমি এবারের বইমেলায় দেশে আসতে পারিনি। যদিও এগুলো আবেগতাড়িত কথা বলে উড়িয়ে দিতে পারে অনেকে, তবুও আমি এটিই মনে করি।
যাই হোক, নরসিংদীভিত্তিক আপনার যে–লেখালেখি, আপনার ‘দ্রাবিড় গ্রাম’, ‘শীতলক্ষ্যা’, ‘জাতিস্মরের জন্মজন্মান্তর’ ইত্যাদি উপন্যাসে আমরা খানেপুর গ্রামের ভাঙনের ইতিহাস উপন্যাসের আদলে পাই। কিন্তু আমরা সারকারখানা কর্তৃক খানেপুর গ্রাম ধ্বংস হবার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।
হরিপদ দত্ত : আগেও একবার মাসুদ রানাকে আমি বলেছি, না জেনে, না পড়ে এগুলো জিজ্ঞেস করা উচিত না। আমার আত্মজীবনী ‘উলুখাগড়া’য় ছাপা হয়েছে। তাছাড়া অনেক উপন্যাসেও এসবের ছাপ আছে। আর অনেক কথা এভাবে বলা যায় না। কেউ বলে না। আমার ঘর–সংসার আছে, নানা সমস্যা আছে। রবীন্দ্রনাথ আর কাদম্বরীর সম্পর্কের কথা কি তিনি স্বীকার করেছেন কখনো?
আচ্ছা, তাহলে ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। এখন আপনি পশ্চিমবঙ্গে আছেন। সেখানে দিন কীভাবে পার করছেন?
হরিপদ দত্ত : ঘুরে–ফিরে কাটাই আরকি। ভাবলাম, বয়স হয়েছে, ধর্মকর্ম করা দরকার। এটা করোনা শুরু হওয়ার দুই বছর আগের কথা। মনে হলো, আমার সৃষ্টির জন্যে পুণ্য অর্জন দরকার আছে। আমি পা বাড়ালাম— প্রথম যে তীর্থস্থানে গেলাম, তার নাম শান্তিপুর। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের বাড়ি, প্রথম মুসলমান লেখকের হাতে রচিত উপন্যাস ‘জোহরা’র লেখক। ওটাই আমার ধর্মস্থান। তীর্থ মানে আমার কাছে গয়া–কাশী–বৃন্দাবন নয়, লেখকের জন্য লেখকের সৃষ্টির জায়গা তার পুণ্যভূমি, এটা আমি মনে করি। ওটাই আমার ধর্মস্থান। এরপরে গেলাম চৈতন্য দেবের আন্দোলনের স্থানে, নদীয়া। গেলাম কৃত্তিবাস ওঝার ওখানে। কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থানে। একটা বটগাছ আছে। বটগাছের সঙ্গে একটা সাইনবোর্ড লাগানো। লেখা ‘এই বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া মহাকবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন’। নিচে সংস্কৃতেও লেখা আছে। দেখলাম, গাছের ওখানে একটা ফুটা আছে। ওখানকার কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুটা কেন? সে বললো, ভেতরের গাছটাই মূল গাছ। যেটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটার বয়স বড়জোড় ৭০ বছর হবে। মূল গাছটাই ভেতরে। উপরেরটা নবীন গাছ। বটগাছ তো একজন আর একজনকে জড়িয়ে থাকে। এভাবেই তারা হাজার বছর টিকে থাকে। ওখানে একটা লাইব্রেরিও আছে। যদিও তেমন কিছু নেই, কিন্তু যেটা অবাক করলো, তা হলো, অনেকগুলো কবর ওখানে। কবরগুলো চৈতন্য দেবের শিষ্যের। হুসেন শাহ, হরিদাস, বলবান হরিদাসের। ভেতরের দিকে আরো আছে, যেতে পারলাম না। ঘন জঙ্গল হয়ে গেছে। এটা সাহিত্যের জায়গা। সেই বটবৃক্ষের উপরে একটি বেদি বাঁধানো আছে। সেই বেদির উপর বসে ভাবলাম, এখানেও হয়তো লেখা থাকতে পারতো, ‘এই বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া হরিপদ দত্ত জন্ম জন্মান্তর উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন’। (অট্টহাস্যে) এমন যদি হতো, খুব ভালো হতো। কবি জয়দেবের তীর্থ বীরভূম; সেখানে ভোজপুরি ভাষা। যেটা রাধা–কৃষ্ণের প্রেমের মূল জায়গা। ওখানে একটা ভাঙা মন্দিরের মতো আছে। এই জায়গাগুলো আমার কাছে তীর্থস্থানের মতো। এই জায়গাগুলোতে গেলে প্রেরণা পাওয়া যায়। সাহিত্যের প্রেরণা পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাসুলী বাঁকের উপকথা’ আমার অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস। বীরভূম, যেখানের কথা এই মহাকাব্যিক উপন্যাসে বলা হয়েছে। জঙ্গল এলাকা। বাঙালি, সাঁওতাল, কাহার পাশাপাশি দীর্ঘ বছর বসবাস করে। আর বাঁকটা হলো অনেকটা কল্পনা। কোপাই নদীটা শান্তিনিকেতন যাবার পথে দেখা যায়। আমি যখন গেলাম, তখন শীতকাল। পানি তেমন নেই। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম নদীর চরার ওপাড়ে একটা বটগাছ আর তার সঙ্গে লাগোয়া একটা দহ। গভীর দহ, দূর থেকে দেখা যায়। হেঁটে ওদিকে যাওয়া নিষেধ, চোরাবালি আছে। উপন্যাসে কালো বউ, নাম নয়ান, যে পরকীয়া করে ধরা পড়ে, পরে একটা জায়গায় বটগাছের কাছে সাপ তাকে ছোবল মারে, পরে দহের মধ্যে পড়ে মারা যায়। হেঁটে ওই দহের কাছে যাবার পর মনে হলো, এটা সেই জায়গা। তারাশঙ্করের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ওখানে বটগাছ আছে অনেক। দহও অনেক আছে। হয়তো ওটা নয়, ওটার মতো। কবির কল্পনা যখন মানুষকে স্পর্শ করে, তখন এমন হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের একটা অংশ চুঁচুড়ার দিকে থাকে। এই স্টেশন দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বহুবার গিয়েছেন। তাঁর বাবা ব্রিটিশ সরকারের চাকুরি করতেন। ওয়ালীউল্লাহ্ থাকতেন উনার সঙ্গে। ওই পথে কলকাতা আসতেন–যেতেন। ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনি’ গল্পে যে–চরিত্রগুলো পাওয়া যায়, ওই যে গৃহকর্ত্রী, দেশভাগের পর ট্রেনে করে চলে গেলেন; কোথায় গেলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জানেন না। কিন্তু যখন সন্ধ্যায় তুলসী গাছের কথা বললেন, এখানে যে লিলুয়া, বৈদ্যবাটি, সেখানে গিয়ে ঠিক একটা বাড়ি দেখে আমার বারবার গল্পটির কথা মনে হতে লাগলো। আমি সেই বৈদ্যবাটি স্টেশনে নেমে গেলাম। দেখি কী হয়। মুশকিল হলো ওসব জায়গায় মিশতে গেলে একটা ভাষা লাগে। জোর করে হলেও উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় বলবার চেষ্টা করলাম। একজনকে বললাম, ওই পাশে যাবার পথ কোনটা? তখন সে বললো, আপনি কেন যাবেন? আমি বললাম, ওই যে বাড়ির উঠান, ওখানে একটু যাবো। উঠানে একটা শাড়ি আড়াআড়ি করে মেলে দেয়া। মনে হলো একটা গৃহস্থ বাড়ি। ঠিক গল্পে যেমন আছে। কোনো রকম ঢুকেই যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে একজন ডাক দিলো, কেন যাবেন, কী কাজ, কোথা থেকে এসেছেন? বললাম, পাশের গ্রামে আমার আত্মীয় থাকেন। এখানে একটু বেড়াচ্ছি। যাই হোক, নানা প্রশ্ন। আর তর্ক করলাম না। কিন্তু দেখো, ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পটা লিখেছেন ১৯৪৮ সালে, কিন্তু আমি এখন তাড়িত হচ্ছি। সাহিত্য কীভাবে মানুষকে আকর্ষণ করে, কীভাবে বিভ্রান্ত করে, আমিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।
আরেকটা বিষয় বলি। তোমরা কি মনে করো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–কে যথাযোগ্য মূল্যায়ন বা মর্যাদা দিয়েছে বাংলাদেশের পাঠক–লেখক–বুদ্ধিজীবীরা? দেয় নাই। কারণ, উনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলে এখন যারা লাফালাফি করে, তারা পায়ের নিচে চলে যাবে। তাঁর সমতুল্য লেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, “পড়ো, পড়ো, শিখো, কীভাবে একজন ওয়ালীউল্লাহ্ ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসে উপমা–চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। শিখো হরিপদ, শিখো। শিখবে, লিখবে।”
ওয়ালীউল্লাহ্’র নকলটা করলো কিছু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর ধারাবর্ণনার নদীর কুয়াশা, কুয়াশা উপরে উঠতেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ লেখলো ভেড়া, ইলিয়াস ভাবলো, কেউ পড়ে নাই এসব, সে লিখলো বাছুর।
আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে নাই আপনার?
হরিপদ দত্ত : ‘উলুখাগড়া’য় ছাপা হয়েছে তো আত্মজীবনী।
ঢাকা কেন্দ্রিক যে–সাহিত্যচর্চা এবং কলকাতা কেন্দ্রিক যে–সাহিত্যচর্চা, এক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান কীরূপ?
হরিপদ দত্ত : একটা সত্য কথা বলি। ঢাকা কেন্দ্রিক মানে হলো মুসলিম সমাজ, পারিবারিক জীবন— এসব, আর মুসলমানরা শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেছে হিন্দুদের অনেক পরে। আর বাংলা ভাষার চর্চা ঠিক ওইভাবে মুসলিম সমাজে ছিলো না। এর ফলে যে–গ্যাপটা তৈরি হয়েছে, পরবর্তীকালে ধরো ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে একটা বিরাট চেঞ্জ আসছে। ফলে সাহিত্যেও একটা চেঞ্জ আসলো। দেখো, এই সময় স্রোতের মতো কবিতা লেখা হয়েছে। নির্মলেন্দু গুণ, হাবিবুল্লাহ সিরাজীর কবিতার বই ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি হতো। নাটক–থিয়েটারের জোয়ার বইলো। কিন্তু যেই না স্বাধীনতার সূর্য আস্তে আস্তে মেঘে ঢাকতে শুরু করলো, স্বাধীনতা মানুষের আশা পূরণ করতে পারলো না, ঠিক শিল্প–সাহিত্যেরও একই অবস্থা হলো। কোথায় গেলো এসব? যৌনতার দিকে চলে গেলো। সেগুলোর বিশাল বাজার তৈরি হলো। তারপর আরো পরে ইলেকট্রনিক ডিভাইস এলো। ছেলেমেয়েরা বইপড়া থেকে দূরে চলে যেতে থাকলো। তবে আমি মনে করি না যে, মোবাইল বা আধুনিকতার কারণেই তারা বই থেকে দূরে সরে গেছে। ইংল্যান্ড–আমেরিকার চেয়ে উন্নত কি বাংলাদেশ নাকি? লক্ষ লক্ষ কপি উপন্যাসের বই বিক্রি হয় আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে, ইউরোপে। ওখানেও তো মিডিয়ামের ছড়াছড়ি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ভেতর বসবাস করে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা। তারপরও তারা বই কিনে, বই পড়ে। যাই হোক, ঢাকার ব্যাপারটা হলো, এখানে সাহিত্যের চর্চাটাই কম হইছে। তবে হবে। আসলে এ–অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদী একটা আগ্রাসন ছিলো, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচারটা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র বহন করতো। সেই যুগটা চলে গেছে।
স্বাধীনতা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমাদের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু আমরা পারিনি সত্যিকার অর্থে। বিশ্বমানের কোনো উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য আমরা উৎপাদন করতে পারিনি। এটা স্বীকার করতে হবে।
এর কারণটা কী? কেন পারিনি? আমাদের ঘাটতি কোন জায়গায়?
হরিপদ দত্ত : ঘাটতিটা হলো, আমাদের চর্চার অভাব আছে।
আমরা কি বৈশ্বিক চেতনা ধারণ করতে পারি নাই?
হরিপদ দত্ত : না না। বৈশ্বিক চেতনা আছে। থাকবে না কেন? অনেক ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যে–চেতনা, এটা তো কেউ জন্মসূত্রে পায় না। এটা পড়াশোনার মাধ্যমে হয়। সেই সুযোগগুলো এখানে নেই। এখানে বিশ্বমানের কোনো পাঠাগার নেই। নেই কিন্তু। সে–ধরনের প্রকাশনা সংস্থাও নেই এখানে। আমি এক প্রকাশককে বলেছিলাম একবার, ভাই, তুমি মনে কিছু করো না, তুমি আনন্দ পাবলিশার্সে গিয়ে ট্রেনিং নাও, কীভাবে বইয়ে বিনিয়োগ করে এটার বিলি–বণ্টন করে আয় করতে হয়, এটা বুঝতে হবে তোমাকে। তুমি যদি বাংলাবাজারে বইসা দুইটা বই বিক্রি কইরা অই পয়সা দিয়া এক সের চাল কিনে মোহাম্মদপুর চলে যাও, তাহলে তোমাকে দিয়ে বইয়ের ব্যবসা হবে না, তুমি যোগ্য নও প্রকাশক হবার। পরে সে রাগ করেছিলো।
মুশকিলটা হলো, আমাদের এখানে খাটনি আছে, শক্তি কম। স্বীকার করতে হবে। তারপর কী বলবো, আত্মমর্যাদা নাই আমাদের মধ্যে। এক কবিকে একবার আমি ফোনে বলেছিলাম, ‘দেশ’ পত্রিকায় তোমার একটা কবিতা ছাপা হলো, ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ছাপা হলো, এতে লেজ নাড়ানোর কিছু নাই। তুমি কি জানো, পূজা সংখ্যার পত্রিকা কীভাবে ছাপা হয়? এমন ঘটনা মাঝে–মধ্যে ঘটে যে, বাংলাদেশের লেখক–কবিদের লেখা ‘দেশ’ পত্রিকায় যেগুলো থাকে, বাংলাদেশের জন্যে আলাদা ছাপা হয়। সেগুলো বাংলাদেশে চলে আসে। কলকাতায় যে–পত্রিকা চলে, সেখানে বাংলাদেশের লেখকদের লেখা থাকে না। আমি তাকে বললাম, তুমি এই লেজুড়বৃত্তি করো না। নিজের দেশ, ঐতিহ্য, ধর্ম— সবকিছু বিসর্জন দিয়ো না। কারণ, এটা একটা মার্কেট। তোমার একটা কবিতা ছাপা হলে তুমি লেজ নাড়তে নাড়তে গদগদ করতে করতে আরো দশটা পাঠক তৈরি করবা তাদের। কোথায় ময়মনসিংহে বসে তুমি পশ্চিমবঙ্গে আমাকে টাকা খরচ করে ফোন করে বললে, দাদা, দেশ পত্রিকার এই সংখ্যা কি আপনার ঘরে এসেছে? আমি তো লিখেছি। আমিও কলকাতার ভাষায় বললাম, আমি পড়েছি বৎস্য, খুব ভালো লিখেছো। এতো গদগদ কেন? বাজার তৈরি করছে তারা। তারা বেনিয়া, এটা মনে রাখতে হবে।
এবার আমাদের করণীয়টা বলেন। ঢাকার সাহিত্যচর্চার জন্যে কী পড়া দরকার, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়া দরকার?
হরিপদ দত্ত : দেখো, আমি কখনোই বলবো না যে, তুমি কমিউনিস্ট লেখকদের বই পড়ো, মানিকের বই শুধু পড়ো। এটা আমি কখনোই বলবো না। আগে বলতাম। প্রত্যেকে পড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন। যা ভালো লাগে, সেটাই পড়বে। তবে তোমাদের শেষ একটা কথা বলে রাখি, তোমরা তৈরি হয়ে থাকো। দিন আসতেছে কিন্তু। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কেন্দ্রিক গদ্য আর বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রিক গদ্য কিন্তু একটা অনিবার্য সংঘাতের কাছাকাছি চলে আসছে। আমিও চাচ্ছি, দ্রুত সংঘাতটা লাগুক। লাগলে সুবিধা কী, স্বাধীন বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব একটা গদ্যরীতি তৈরি হবে। আরেকটা জিনিস হিসেব করে দেখবা যে, সারা বিশ্বে আটাশ কোটির মতো বাঙালি আছে। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহারের একটা অংশ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু আছে— এদের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে হিন্দু–মুসলমানের সংখ্যা কতো? হিন্দু মাত্র নয় কোটি। তাহলে বাকি ঊনিশ কোটিই তো নেতৃত্ব দেবে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার স্বাধীন দেশ কোনটা— পশ্চিমবঙ্গ না বাংলাদেশ? সুতরাং তোমাদের দায়িত্ব বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব নেয়া, লেজুড়বৃত্তি করা নয়।
পঞ্চাশ বছরেও এটা হলো না কেন?
হরিপদ দত্ত : হলো না, ঐ যে লেজুড়বৃত্তি।
কলকাতার লেখকদের সাথে আপনার কোনো যোগাযোগ নেই?
হরিপদ দত্ত : না। যোগাযোগ আমি করিই না। আমার সব লেখা আমি বাংলাদেশেই পাঠিয়ে দেই। জন্মঋণ শোধ করতে করতেই আমার জীবন চলে যাবে।
একাত্তরের যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?
হরিপদ দত্ত : তখন আমি একটা বাম দলের সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি চীনপন্থীদের সাথে ছিলাম। মেননদের সাথে ছিলাম। তাছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে, সর্বহারার সাথেও যোগাযোগ ছিলো। টিপু বিশ্বাস, ভাষা মতিন, বদরুদ্দীন উমর…
বদরুদ্দীন উমর ভাইয়ের জন্যে আমার খুব কষ্ট লাগে। এতো বিশাল পণ্ডিত, উনাকে কে বললো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কমিউনিস্ট রাজনীতি করতে?
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ও–দেশেই থাকার চিন্তা করছেন কি? বা বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?
হরিপদ দত্ত : আমি তো পরনির্ভরশীল এখন। আমার ছেলেরাই আমাকে খাওয়ায়–পরায়। আর ওখানে আমাকে কেউ চেনে না তো। আমি নিরিবিলি স্টেশনে বসে থাকি, একা। আর ওখানে বসলে আমার মাতৃভূমির কথা মনে পড়ে খুব।