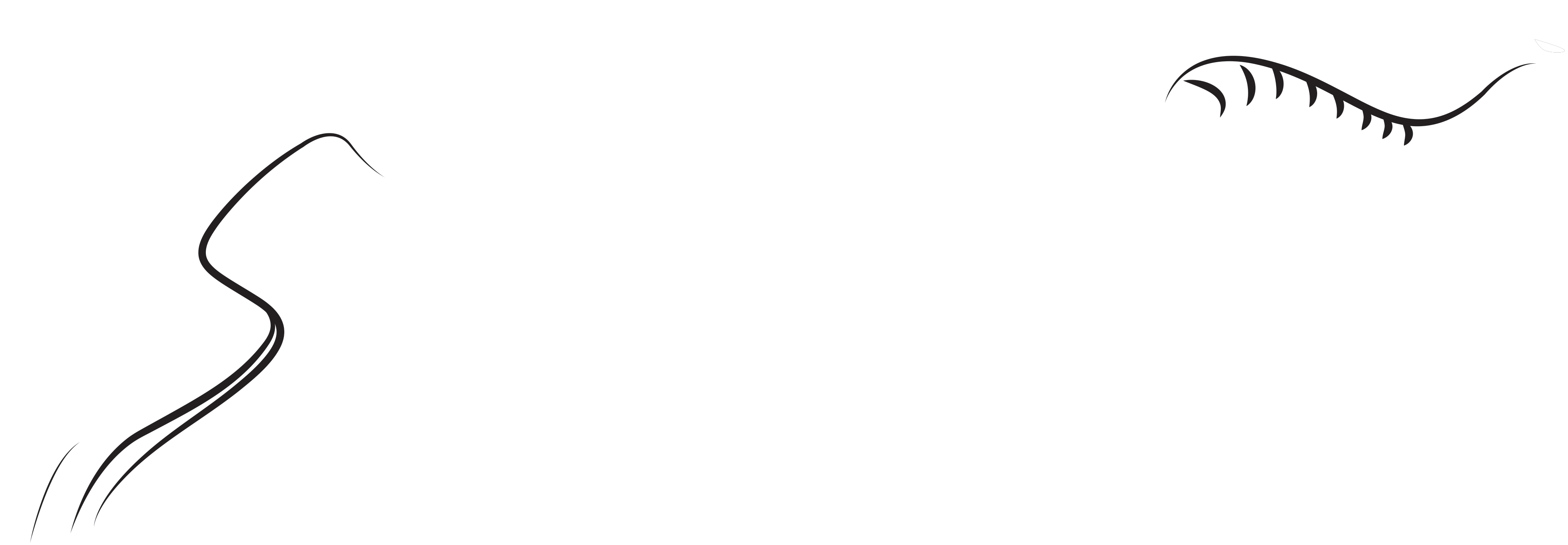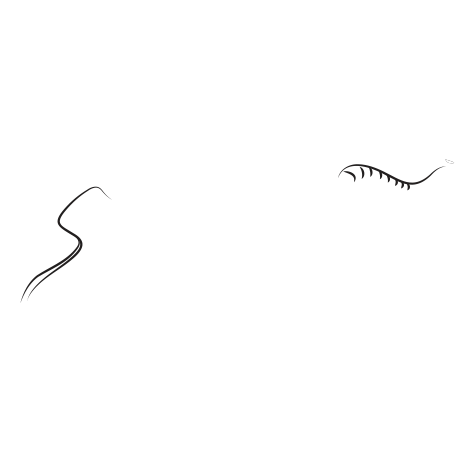সূর্য উঠার পর থেকেই মেঘনার পার ঘেষে পুঞ্জিভূত হতে থাকে মানুষের সারি। গন্তব্য বাউল বাড়ির ঘাট। যদিও বাঁধানো ঘাট বলতে তেমন কিছু নেই, তবে নির্দেশক আছে। বাড়ির দখিনের ফটক বরাবর চলছে পুণ্যস্নান। স্নান শেষে পুণ্যার্থীরা একে একে প্রবেশ করতে থাকে বাড়ির ভেতরের দিকে। দ্বিতল ভবনটি পার হয়ে গেলেই মূল আখড়াবাড়ি। সামনের দিকে ঘিয়ের প্রদীপ, মোম, ধূপবাতির দোকান। একদম উত্তরের আরাধনা কক্ষের সামনের প্রাচীরে পুণ্যার্থীরা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, দরোজার সামনে ছিটিয়ে দিচ্ছেন বাতাসা। ধূপের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আসে। উলুধ্বনি, প্রার্থনা চলছে। আরাধনা কক্ষের ভেতর যজ্ঞের আগুন জ্বালানোর জন্যে ঘি ঢালা হচ্ছে। সার্বিক নির্দেশনার দায়িত্ব পিন্টু বাউলের হাতে, তিনি এই আখড়া বাড়ির সেবায়েত।

আখড়াবাড়ির ঠিক মাঝখানটাতে বৈঠকের ছাউনি। দেশ ও দেশের বাইরের নানা প্রান্ত থেকে আসা বাউল ও পুণ্যার্থীরা সর্পিল হয়ে বসেছেন। থেমে থেমে চলছে গান, গানের ফাঁকে ভাববর্ণনা। সব মিলিয়ে নরসিংদীর মতো একটা কর্মব্যস্ত মফস্বলের ভেতর এ এক ভিন্নরকম দৃশ্য। বাড়ির প্রাচীরের ঠিক বাইরেই বিশাল এলাকা জুড়ে মনোহর পসরা। মুখরোচক খাবারের দোকান, জুয়েলারি–কসমেটিকস, খেলনার দোকান, ক্রোকারিজ, মাটি ও কাঠের তৈজসপত্র… সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। ড্যাবের ঢোল, জিলাপি, পিস্তল, কাঠের ঘোড়া… এক লহমায় শৈশবে ফিরে যাওয়া যায়।
বলছিলাম নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী বাউল মেলার কথা। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার তিথিতে বাউল ঠাকুরের স্মরণে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাউল ও পুণ্যার্থীদের মিলন উৎসব। বলা হয়ে থাকে, এই মাঘী পূর্ণিমার তিথিতে বাউল ঠাকুর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ঠিকঠাক তাঁর সময়কাল, নাম, পরিচয় এখন আর কিছুই জানা যায় না। তিনি ‘বাউল ঠাকুর’ নামেই পরিচিত। অবশ্য কোনো লিপিবদ্ধ তথ্যাদি বা ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকার কারণ বাউল ঠাকুরেরই কিছু শর্ত। তিনি লিপিবদ্ধ করাকে জড়–গুরুত্বহীন কাজ বলে মনে করতেন। যদি শিক্ষা ও সাধনাকে নিজের অন্তরাত্মায় ধারণ করা না যায়, তাহলে পুঁথিগত সকল ব্যাপারই অর্থহীন। ঠাকুরের সহস্রাধিক ভাবসঙ্গীত রয়েছে, যা সেই পাঁচ শতাধিক বছর ধরে শুধু মৌখিকভাবে অনুশীলন ও উচ্চারিত হয়ে আসছে এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মুখে।

এই উৎসবেরই একজন পুণ্যার্থী শংকরলাল পোদ্দারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম এখানকার বাউল মেলা ও বাউল ঠাকুরের আগমনের ইতিহাস। তার ভাষ্য এই যে, “বাউল ঠাকুরের দেহ যে–স্থানে সমাহিত করা হয়েছে (উত্তরের আরাধনা কক্ষের অভ্যন্তরে), সেখানে একটি ফলক রয়েছে। ফলকে ৯৩৪ বাংলা সনের উল্লেখ রয়েছে। তবে বাউল ঠাকুরের ইতিহাস জানার চে’ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁর দর্শন ও শিক্ষাকে ধারণ করতে পারা, তাই এ নিয়ে বোঝাপড়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই। বাউল ঠাকুরের দর্শন–ভাবের বোঝাপড়া, তাঁর শিক্ষাকে ধারণ করাটাই মূলকথা।” সেই জায়গা থেকে এই আখড়াবাড়ি বরাবরই প্রচারবিমুখ। কোনোরকম প্রচারণা ছাড়াই প্রতি বছর ঠাকুরের তিরোধান দিবসে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে অংশগ্রহণ করেন, আত্মশুদ্ধি লাভের জন্যে প্রার্থনা করেন। নরসিংদীর বাউলপাড়ার এই বাউল মেলাটি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা বহু খোঁজ–খবর করেও জানা যায়নি।
এসব বিষয়–আশয় নিয়ে কথা হলো একজন প্রবীণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাথে, যিনি পরলোকগত মণীন্দ্র বাউলের সাথে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। মণীন্দ্র বাউলও পেশায় খুব জনপ্রিয় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় এই আখড়াবাড়ির সেবায়েত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সাহচর্যে থাকায় বাউলবাড়িতে দীর্ঘ সময়ের আসা–যাওয়ায় অনেক অভ্যন্তরীণ তথ্য জানা থাকার কথা। যদিও তিনি সাক্ষাতকার এবং নাম প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তবে আলাপচারিতায় কিছু তথ্য উঠে আসে। তার ভাষ্য অনুসারে, বাউল ঠাকুরের সময়কালটি ভারতবর্ষে মুঘল শাসনামলের, সম্রাট আকবরের সময়ের। আকবরের রাষ্ট্রনীতির সাথে বিরোধের জেরে বাউল ঠাকুর স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেন এবং এখানে এসে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হন। বোধিলাভের পর তাঁর দর্শন প্রচার শুরু করেন। এর আগে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু এখানে এসে বাউল ধর্ম প্রচারের সময় ‘রামদাস বাউল’ নাম ধারণ করেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না। এমনকি পূর্ব জীবনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এখন যারা বাউলবাড়ির সদস্য, তারা ঐ–সময় আখড়াবাড়িতে নিযুক্ত খাদেমদেরই উত্তরসুরী। উন্মুক্ত কোনো নথি না থাকলেও বাউল বাড়িতে কিছু গোপনীয় নথি থাকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।
এই প্রবীণ চিকিৎসকের তথ্যের একটা বড়ো ঐতিহাসিক দুর্বলতা এই যে, খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও এর আগে আখড়াবাড়ির সেবায়েত যারা ছিলেন, ব্রিটিশ শাসনামল থেকে তাদের নামের তালিকাটি পাওয়া যায়। সেই সূত্রে ব্রিটিশ শাসনামলে (কোনো–এক পর্যায়ে) এই আখড়াবাড়ির সেবায়েত ছিলেন স্বর্গীয় নদীরাম বাউল। পরবর্তীতে তাঁর নাতি মণীন্দ্র চন্দ্র বাউল ও বর্তমানে তাঁর ছেলে সাধন চন্দ্র বাউল, মৃদুল বাউল মিন্টু, শীর্ষেন্দু বাউল পিন্টু, মলয় বাউল রিন্টু এবং প্রাণেশ কুমার বাউল ঝন্টু। প্রাণেশ কুমার বাউল ঝন্টুর মৃত্যুর পর মৃদুল বাউল মিন্টু এবং এ–বছর শীর্ষেন্দু বাউল পিন্টু সেবায়েত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এখন নদীরাম বাউল, যার তথ্য ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম সেবায়েত হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তাঁর আরেক নাম রামদাস বাউল। এই জায়গায় এসে বাউল ঠাকুরের নাম সংক্রান্ত যে–দাবি প্রবীণ চিকিৎসক করেছিলেন, তা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার এ–ও সম্ভব যে, একই নামের পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং বাউলদের মধ্যে এ–ধরনের নাম ধারণের ঝোঁক এর আগেও দেখা গিয়েছে।
যাই হোক, এখানকার আগত পুণ্যার্থী, সেবায়েত সকলেই বাউল ধর্মের শিক্ষা, বাউল ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি প্রধান বিষয়বস্তু প্রচার ও ধারণ করার পক্ষপাতী। এ–বিষয়ে কথা হলো এই বাড়িরই বধূ মীনাক্ষি বাউলের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় বাউল ঠাকুরের ভাবের বিষয়টি পুরো ধরা পড়ে।
প্রতিষ্ঠিত মত অনুসারে, বাউলদের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে এ–অঞ্চলে ইসলামের প্রসারের সংযোগ রয়েছে। ইসলামের বিস্তারের সময় এই অঞ্চলে পারস্যের সুফিধারার আগমন ঘটে। যখন সুফিমত এ–অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন এখানকার স্থানিক আধ্যাত্মিকতা ও সাধনপদ্ধতির সাথে মিথস্ক্রিয়ায় একটি লোকধর্মের রূপ লাভ করে। এবং যেহেতু এই অঞ্চলের মানুষ এর আগেই বৌদ্ধ সহজিয়াদের তন্ত্র ও আধ্যাত্মিক যোগ সাধনার সাথে পরিচিত ছিলো, তাই খুব সহজেই সুফিমতের সাথে স্থানীয় মানুষের সংযোগ স্থাপন সহজতর হয়। সামাজিক জাতবৈষম্যবিরোধী–দেহাত্মবাদী দর্শন, তার সাথে সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগ সাধনার সংযোগে বাউল ধর্মমত এ–অঞ্চলের মানুষের মনে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। সুফিবাদের সংস্পর্শে এসে বাউল, বৈষ্ণব ভাববাদ ও লোকায়ত ধারার বিস্তার ঘটে। বাউলদের বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন হচ্ছেন আউল চাঁদ ও মাধব বিবি। তাঁদের প্রয়াসেই বাউলধারার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে লালন সাঁই এই ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অর্ন্তভুক্তি সাধন করেন।
তবে কি নরসিংদীর বাউল ঠাকুর তাঁদেরই চিন্তার উত্তরসুরী? এই জায়গাটিতে এসে আমাদের একটু থামতে হয়। কারণ, বাউল ঠাকুরের সাথে মাধব বিবি বা আউল চাঁদের যে–সংযোগ, তারচে’ অধিকতর সংশ্লিষ্টতা শ্রী চৈতন্য দেবের সাথে।
ব্রাহ্মণ্য–শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে ওঠেছে একটি মিশ্র মত। এর আধুনিক নাম নাথপন্থা। ‘অমৃতকুণ্ড’ সম্ভবত এদেরই শাস্ত্র ও চর্যাগ্রন্থ। এটি গোরক্ষপন্থীর রচনা বলে অনুমিত হয়।
বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনই তাদের লক্ষ্য। ‘হঠ’ যোগের মাধ্যমেই এ–সাধনা চলে। একসময় এই নাথপন্থা ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিলো বাঙলায়, চর্যাগীতি ও নাথসাহিত্য তার প্রমাণ। এই দুই সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়।
: ভূমিকা, বাঙলার সূফী সাহিত্য, ড. আহমদ শরীফ
আহমদ শরীফের এই মতকে আমলে নিলে ধরে নিতে হয় যে, বৈষ্ণববাদের উত্থানের পেছনে সুফিধারার কন্ট্রিবিউশন ছিলো। এই বৈষ্ণব ভাবধারার অন্যতম সংস্কারক হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য। তিনি রূপক ও প্রেম–ভক্তি–সাধনার সমন্বয়ে সনাতন ধর্মের নতুন এক চাঞ্চল্যকর ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন, যা জনমনে ব্যাপক বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ করে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নদীয়ায় এবং পরবর্তী সন্ন্যাসজীবনে ভারতের তীর্থস্থানগুলোতে ভ্রমণের পর দক্ষিণ ভারতের পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন।
পুরীতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে অগণিত ভক্ত সমবেত হতেন। চৈতন্য দেবের মৃত্যু নিয়ে রয়েছে বড়ো এক রহস্য, অনেক কথা–উপকথা। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক রচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ অনুসারে, চৈতন্য মহাপ্রভু একদিন বিকেলে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের একটি উপ–মন্দির টোটা গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পরপরই মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে আর কোনোদিন চৈতন্য মহাপ্রভুর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। দাবি করা হয় যে, মহাপ্রভু সেখানেই জগন্নাথ দেবের সাথে লীন হয়েছেন, তাঁর অন্তর্ধান ঘটেছে। এখন, বাউল ঠাকুরের আখড়াবাড়ির দাবি, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই ‘বাউল ঠাকুর’। টোটা গোপীনাথ মন্দিরে অন্তর্ধানের পর তিনি এখানে বাউল ঠাকুর রূপে আবির্ভূত হন।
এখানকার বাউলেরা মূলত সনাতন ধর্মের অনুশাসনগুলোই অনুসরণ করেন। তবে ঈশ্বর সংক্রান্ত ভাবনা–চিন্তার জায়গাটিতে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, সর্বেশ্বরবাদী। যেহেতু সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই প্রতিটি প্রাণের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন বলে তাঁদের বিশ্বাস। জীবনাচরণের ব্যাপারে তাঁরা খুব সচেতন। খাবার–দাবারের ব্যাপারে বেশকিছু বাছ–বিচার রয়েছে। একদানা খাবারও যেন নষ্ট না হয়, তা কঠোরভাবে নির্দেশিত। মাংস না খেলেও মাছ (যেহেতু জলজাত, তাই) খান। দেহ ও মনের উপর খাবারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা।
বাউল ঠাকুরের দর্শনও মূলত সাংখ্য–তন্ত্র–যোগ সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। মানবদেহের যে–চালিকাশক্তি, সেখানেই পরমাত্মার অবস্থান, সেখানেই ঈশ্বর বিরাজমান। আর মানুষের মনই হচ্ছে জীবাত্মা। জাগতিক জীবনের মোহে পড়ে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার ব্যাপক ব্যবধান তৈরি হয়। তখনই মানুষ রিপুর বশবর্তী হয়। অপরাধে লিপ্ত হয়। তাই জাগতিক যতো অসামঞ্জস্যতা, যতো ধরনের বিশৃঙ্খলা রয়েছে, বাউল ঠাকুর তাঁর সমাধান খুঁজেছেন দেহের অভ্যন্তরে। নিজের মধ্যেকার যেই কাম–ক্রোধ–হিংসা–লোভ, তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেই কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটানো সম্ভব। সম্ভব প্রকৃত অর্থে ‘মানুষ’-এ উন্নীত হওয়া। আর এজন্যেই প্রয়োজন দেহসাধনা। জগতের সবকিছুর প্রতিরূপ মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে। এখানেই দেশ–কাল–পাত্র, এখানেই মন্দির–কাবা। একটি গানের কথা অনেকটা এমন—
এই দেহভাণ্ডে আছে, ব্রহ্মাণ্ডে নাই,
দেহের বিচার করতে হইলো, নইলে মানুষ হারাই…
(দেহের উপযুক্ত সাধনা করতে না পারলে মনুষ্যজন্ম হারাতে হবে, দেহ সাধনা না করলে তো আর এ–দেহের প্রয়োজন নাই। পরবর্তী জন্মে চুরাশি লক্ষ প্রজাতির কোনো একটিতে জন্মলাভ করতে হবে।)
ঠাকুরের সহস্রাধিক ভাবসঙ্গীত মূলত দেহ সাধনার মাধ্যমে নিজের অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করার প্রয়াসেই রচিত। বাড়ির সদস্যরা প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় বৈঠকে পর্যায়ক্রমে সেগুলো পাঠ ও আলোচনা করেন। উন্মুক্ত বৈঠক হওয়ায় পুণ্যার্থীরাও যুক্ত হতে পারেন।
এ–ধর্মমতে নারীকে খুব পবিত্র এবং অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতম হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। বলা হয়ে থাকে, নারীই সৃষ্টির মূল। মাতৃগর্ভকে বিশেষ প্রতীকী অর্থেও ব্যবহার করা হয়। নারী ও পুরুষ দুজনের মধ্যেই ছয়টি রিপু তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য বিদ্যমান। তবে নারী আরো অতিরিক্ত তিনটি রিপুর অধিকারী : মায়া, জঠর (গর্ভ) ও ধৈর্য। বাউলমতে, পুরুষের জন্যে ঈশ্বরের আরাধনা আরো কঠিন এই কারণেই যে, তাকে ছয়টি রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং নারী যে অতিরিক্ত রিপুর অধিকারী, তা পুরুষকে মনে ধারণ করতে হয়, আয়ত্ত করতে হয়। কারণ, মাতৃমনন ছাড়া ঈশ্বরের সাধনা সম্ভব নয়, নিজের দেহের ভেতরে অন্তর্দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। এই কারণেই বাউলদের মধ্যে নারীর মতো করে দীর্ঘ চুল রাখার একটি প্রচলন রয়েছে।
খুব চমৎকার নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনযাপন করেন তাঁরা। জীবনযাপনে রয়েছে চিহ্ন ও প্রতীকের ব্যবহার। তন্ত্র ও যোগ সাধনা যাপনের বড়ো একটা স্থান দখল করে আছে। এমনকি, যদি যজ্ঞের আগুনের কথাই ধরি… সাধারণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞে দেখা যায়, মাটির উপর উঁচু করে কাঠ ও অন্যান্য রসদে আগুন জ্বালানো হয়। কিন্তু বাউল ঠাকুরের তিরোধান উৎসবের মহাযজ্ঞে আগুনের জায়গা তৈরি করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে, ভেতরের দিকে। এই যজ্ঞের আগুনের জন্যে সচেতনভাবে মাটি খুঁড়ে তৈরি যে–গর্ত, তা সম্পূর্ণই মাতৃগর্ভের প্রতীক। এইরূপ অসংখ্য প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে পুরো আখড়াবাড়ি ও তাঁদের জীবনযাপন জুড়ে।
বাউল ঠাকুর ও তাঁর ধর্মমত ইতিহাসের এক অনালোচিত অধ্যায়। এই ব্যাপারে বাইরের জগতের জানাশোনা খুব সামান্যই। অবশ্য আগেই বলেছি, এর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে লিখিত কোনো দালিলিক নথি না থাকা বা না রাখা। তবে যাই হোক, সার্বিক বিচারে ইতিহাসের একটি দুর্গম সময়ে, যখন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতবৈষম্য তুঙ্গে, তখন বাউল ঠাকুর সমতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতবৈষম্যহীন সমাজের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যা এখনো প্রাসঙ্গিক।