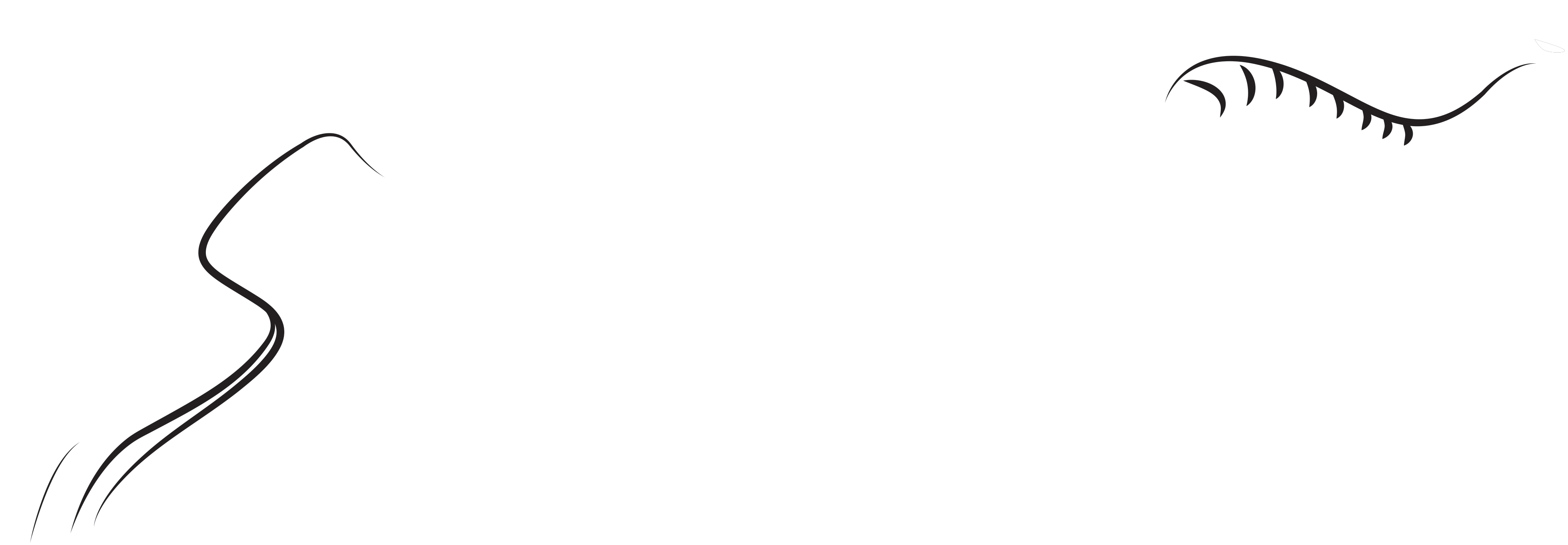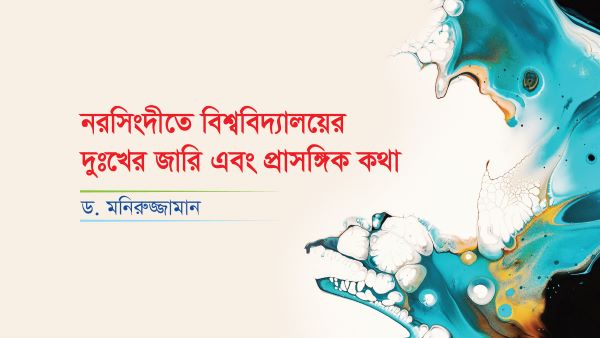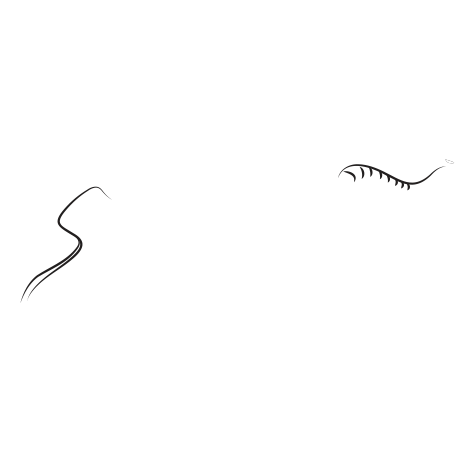যে–কথা নানাভাবে বলা হয়েছে
এই শতাব্দীর গোড়া থেকে কিংবা আরো আগে থেকেই পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়ে আসছিলো, ‘নরসিংদীতে বিশ্ববিদ্যালয় চাই’। বর্তমান শতকের গোড়ায় সংসদে দেশে ১২ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রস্তাবিত হলে তার মধ্যে একটি নরসিংদীতে হবে— এই প্রত্যাশা করা হয়েছিলো। তদুপরি ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস করার প্রস্তাব উঠলে অগত্যা সেটিও যাতে নরসিংদীতে করা হয়, সে-দাবিও রাখা হয় এবং তজ্জন্যে নরসিংদীর অদূরে বিশ্ববিদ্যালয় করার উপযোগী একটি পতিত জমিদার বাড়ি ও তার খাসজমি (পতিত)-র কথাও উল্লেখ করে দেখানো হয় (দ্রষ্টব্য : নরসিংদী জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সরকারি নজরে আনার জন্যে উক্ত বিষয়ক পেশকৃত পত্র, তারিখ— ১২.১১.২০০৮)। পরবৎসর পুনরায় এ-ব্যাপারে ‘নরসিংদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ’-এর পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে সাক্ষাত করে তাঁর বরাবরও আবেদন করা হয় এবং তাতেও বিস্তৃত করে বলা হয় যে, “প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার খ্যাত মাধবদী (বাবুরহাট) বাজার সংলগ্ন ঐতিহাসিক বালাপুর জমিদার বাড়িটি ও তৎসংলগ্ন প্রায় ২ (দুই) হাজার বিঘা খাসজমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে। এখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের সকল প্রকার অবকাঠামো বিদ্যমান। এই ঐতিহাসিক বাড়িটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাস নির্মাণের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান; এখানে তা করা হলে ভূমি ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে না। বরং তা সাশ্রয় হবে। অপরদিকে অন্যভাবে জমি অধিকৃত করতে গেলে বহু মূল্যবান আবাদী জমির ও কৃষকের ঘরবাড়ির ক্ষতি সাধন অবশ্যম্ভাবী।” (আবেদনের তারিখ : ১৯.০১.২০০৯)
আবেদন ও প্রয়াসের ধারা
বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি যেমন রাজনৈতিক দাবি, তেমনি যথাকর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনারও বিষয়। কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা যারা এই দাবি নিয়ে লেখালেখি করছি বা দাবিটা তুলতে বা দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তারা কেউ সক্রিয় রাজনীতিক নই। পেশাগতভাবে আমাদের কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ ছাত্র, কেউ ব্যবসায়ী এবং অনেকে হয়তো চাকুরিজীবী হয়েও লেখক মাত্র। একটা সাধারণ চিন্তা, দেশপ্রীতি ও দায়িত্ববোধ থেকে অনুভূত কিছু অসুবিধার কারণেই আমরা প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র হই ’৮০-র দশকের দিকে। তারপর থেকেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনের সাথে দেখা করে, করণীয় বিষয়ে সকলের বুদ্ধি, পরামর্শ ও উপদেশমতো উপযুক্ত স্থানে যথাপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থিত করতে থাকি এবং পত্র-পত্রিকায়ও নরসিংদীর মতো স্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা এবং বিশেষভাবে এখানকার ছাত্রদের সমস্যার কথা উল্লেখ করে নরসিংদীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আবেদন জানাতে উদ্যোগী হই। এভাবেই আমরা আমাদের নতুন জেলার দরিদ্র ছাত্র ও অভিভাবকদের দুঃখ ও কষ্টগুলি সকলের গোচর করার বা জানাবার উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি চেষ্টা করে আসছি।
এসব ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদীর ছাত্রদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে এর প্রয়োজনীয়তার কথা বহু শতবার আলোচনা করেছি। নরসিংদীতেও এ নিয়ে সংবাদ-সম্মেলন করেছি একাধিকবার। এসব সংবাদ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এবং প্রচারিত পত্রে ও পোস্টারে হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকতে পারেন।
‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংদী ছাত্র সমিতি’
’৮০-র দশক থেকে এই চিন্তাটা বিশেষভাবে কাজ করলেও নবসৃষ্ট নরসিংদী জেলার শিক্ষার্থীদের সমস্যার প্রতিকার ও দৃষ্টিপাত ঘটাতে এই আবেদনটিকে শেষে একটা আন্দোলনের পর্যায়ে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া শুরু হয়। এর পেছনে যেসব বাস্তব কারণ ছিলো, সেগুলো হলো : ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বেশ দুরূহ হয়ে ওঠছিলো; ২. ঢাকায় থাকা-খাওয়ার খরচ সাধারণ ছাত্রদের জন্যে আর্থিক ও সার্বিক ব্যবস্থার দিক থেকে ছিলো বহুগুণ কষ্টের বা দুর্বহ বিশেষ এবং ৩. একইভাবে কষ্টের মাত্রা বেড়ে ওঠছিলো ঢাকার বাইরে (চট্টগ্রাম) যারা যেতে বাধ্য হচ্ছিলো, তাদের।
১৯৭৭ সালে আমি পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেও সেই সময় নরসিংদী থানা প্রথম মহকুমায় উন্নীত হয়েছিলো বলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদীর ছাত্রদের শিক্ষাকষ্ট দূর করার বিষয়ে কিছু করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করতে থাকে। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে CURDP বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা পরিচালক হিসেবে এবং নরসিংদীতে আমার নিজ গ্রামেও বেশ কিছু সামাজিক কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। এসব কারণে ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংদী ছাত্র সমিতি’ গড়ে ওঠলে তার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আমি নরসিংদী থেকে আগত ছাত্রদের সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার কথা ভাবি। তার মধ্যে অন্যতম তাদের চট্টগ্রাম আসা, থাকা ও ভর্তির বিষয়গুলি নিশ্চিত করা। ক্রমে তার সাথে যুক্ত হয় নরসিংদীতে চিটাগাং মেইল ট্রেনের স্টপেজ করার দাবিও, যাতে ছাত্রদের চিটাগাং আসা-যাওয়ার কষ্টটা লাঘব হয়। এসবের সমাধান দুঃসাধ্য না হলেও যথেষ্ট ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিলো। শেষে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে নরসিংদী জেলায় পরিণত হয় (১৯৮৪ সালে) এবং আমাদের আশা-স্বপ্নও বৃদ্ধি পায়। পরে বিশেষত অনুষদের ডিন থাকাকালেও নরসিংদীর ছাত্রদের কষ্টটাকে আরো কাছ থেকে ও স্পষ্ট করে বুঝতে সক্ষম হই। এবং বিষয়টি নিয়ে আরো নানা জনের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর পরিসরে কাজের বাস্তবায়নে এগিয়ে আসি।
বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই এইভাবে অচিরে আমাকে উপদেষ্টা করে ডাক্তার হাসান এবং শ্রীক্ষণরঞ্জন রায় ‘নরসিংদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ’ গঠন করে এবং নরসিংদীতে প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করে।
এছাড়াও এই পরিষদ বার্ষিক সম্মেলন করে স্বাক্ষরতা গ্রহণসহ রক্তদান, চক্ষুশিবির, দন্তপরীক্ষা ও সেবা প্রভৃতি নানা সামাজিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের দাবিটিকে সাধারণের মধ্যে ছড়ানো ও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এসব অনুষ্ঠানে নরসিংদী জেলার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যেমন নরসিংদীর শিক্ষাদাবি উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি অভ্যাগত সকলেই আমাদের দাবির স্বপক্ষে বা অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ ও উপদেশ প্রদানসহ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেছেন।
এভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, নরসিংদীর জনপ্রতিনিধিদের দপ্তর এবং সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রীবর্গের কার্যালয় তো বটেই, সংশ্লিষ্ট আরো নানা জনের সাথেও দেখা-সাক্ষাত করে ও প্রত্যেকের কাছে আমাদের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয় স্মারক পেশ করে নরসিংদীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এ-ব্যাপারে সকলের আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাসে বিগত প্রায় ২৫ বছর ধরে আমরা আমাদের এই প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে আসছি।
আবেদনসমূহে উল্লেখিত বক্তব্য
আমাদের বক্তব্যের মধ্যে আমরা সব সময় এই কথাটাই বলতে চেয়েছি যে, নরসিংদী তার সমৃদ্ধ ইতিহাস সত্ত্বেও শিক্ষাগত দিক থেকে একটি অবহেলিত জনপদ। অনেক আন্দোলন করে এবং স্থানীয় সিনেমা হল, রেলস্টেশন এবং বাজারের তোলা তুলে স্থানীয় নেতৃত্বের সহযোগ-সহায়তায় স্বাধীনতার আগে নরসিংদী কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় এবং অনতিকালে সরকারিকরণসহ তার আরো উন্নতি করাও সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এখনো পর্যন্ত এখানকার শিক্ষার পরিস্থিতি এবং চাহিদার বিষয়টি নিয়ে কেউ বিশদভাবে বিবেচনা করে করণীয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উচ্চশিক্ষার জন্যে এখানকার ছেলেমেয়েরা কতোটা কষ্ট করছে, সেটি সবার অগোচরেই থেকে যাচ্ছে। লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়, পূর্বে কিশোরগঞ্জ এবং পূর্ব-দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পশ্চিমে রেলপথে টঙ্গী পর্যন্ত প্রায় তিন জেলা এবং কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এবং বাংলা ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি জগতের পুরোধা সত্যজিৎ রায়-অতুলপ্রসাদ প্রমুখের মামাবাড়ি-ফুপার বাড়ির এলাকা পাঁচদোনা-রূপগঞ্জ-সোনারগাঁ এলাকা ধরে নিয়ে মেঘনার এপাড়-ওপাড়ব্যাপী ব্রাহ্মণবাড়িয়া- কুমিল্লা-নারায়ণগঞ্জের বহিঃপ্রান্তভাগজুড়ে তথা নরসিংদী সংলগ্ন এক সুবিশাল এলাকার মধ্যে অতীতেও কখনো উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, এখনো তেমনি তার কোনো ব্যত্যয় ঘটছে না। বর্ণিত এই এলাকার মধ্যস্থান হচ্ছে নরসিংদী। নরসিংদীর স্থানগত গুরুত্ব একাধিক কারণে। এটি একটি প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান, মসলিনের জন্মভূমি এবং আমধ্যযুগ বিখ্যাত পাটকেন্দ্র ও বাণিজ্যিক এলাকা। মধ্যযুগের কবি গৌরবনরসিং ওঝা এবং পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের উত্তর বংশধারার চিহ্ন জিনারদীর পুরাণ-অনুবাদক কবি ষষ্ঠীবর শর্মা ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের কথাও এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি। নরসিংদীর বাউল মেলাও এর আরেকটি ঐতিহ্যিক স্মারক।
ঢাকা শহরের পরেই প্রশাসনিক, ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিগত গুরুত্বে নরসিংদীর অবস্থান। অথচ শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এলাকাটি অনেক পেছনে। শুধু কয়েকটি স্কুল-কলেজের বাতাবরণ দিয়ে শিক্ষানগরী বা শিক্ষাএলাকা সৃষ্টি হয় না। ঢাকায় ভর্তি হতে না পেরে এখানকার ছাত্ররা যে-অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে চট্টগ্রামে বা সিলেটে ভর্তি হতে যায় এবং সেখানে যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে যে-অমানুষিক, শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট মেনে নিতে বাধ্য হয়, সেই অবর্ণনীয়তা কি তাতে স্পষ্ট হয়? এসব কথা বহু বহুবার যথাকর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা আমরা করেছি, সে-কথা আগে বলা হয়েছে। এক কথা বারবার বলা হলে তা যে কর্ণকুহরের মধু হয়ে ওঠে, অন্তত আমাদের সে-অভিজ্ঞতা হয়নি। নরসিংদীর ভাগ্য যে-তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরেই আছে আজো।
সংবাদপত্রে নরসিংদী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ও মূল বক্তব্য
পত্রিকার মাধ্যমে জোর লেখালেখি শুরু হয় এই শতাব্দী বা সহস্রাব্দ থেকে। তাতে যাঁরা দাবি করছিলেন, তাঁরা সকলেই যে নরসিংদীর, তা নয়। কেউ কেউ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের, কেউবা আরো দূরের। ঢাকার ফরিদাবাদ থেকে এক মহিলা (বা ছাত্রী)-ও লিখেছেন, যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। অবশ্য অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রামের (আজাদী : ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬, ২১ নভেম্বর ২০০৬, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১, ২৬ জুলাই ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২; সুপ্রভাত বাংলাদেশ : ২০ সেপটেম্বর ২০০৬; ২১ আগস্ট ২০০৮, ৭ এপ্রিল ২০১১, পূর্বকোণ : ৩০ এপ্রিল ২০১৩; দৈনিক কর্ণফুলী : ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬; ডেসটিনি : ২৪ মে ২০০৮; চট্টগ্রাম মঞ্চ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ প্রভৃতি) এবং ঢাকার (দৈনিক প্রথম আলো : ৮ আগস্ট ২০০৬, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১; আজকের কাগজ : ১৮ অক্টোবর ২০০৬; দিনকাল : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭; যায়যায়দিন : ২৮ অক্টোবর ২০০৮; ভোরের কাগজ : ২৮ জানুয়ারি ২০১১; দৈনিক জনতা : ১০ অক্টোবর ২০০৬, ১০ মার্চ ২০১১; খবর : ১১ ফাল্গুন ১৪১৭; দৈনিক রূপালী : ৩০ আশ্বিন ১৪১৩; নয়াদিগন্ত : ১৫ জুলাই ২০০৬, ১০ অক্টোবর ২০০৬; মানবজমিন : ৭ অক্টোবর ২০০৬; আমাদের সময় : ৭ অক্টোবর ২০০৬; দৈনিক আল আমীন : ১১ নভেম্বর ২০০৮ প্রভৃতি) পত্রিকাগুলিতে। এসব কাগজে ফিচার-নিবন্ধ আকারে বা দাবিপত্র আকারেও অনেকে লেখেন। নরসিংদীর স্থানীয় কাগজও এ-বিষয়ে পিছিয়ে ছিলো না। তাদের মধ্যে অন্যতম সাপ্তাহিক নরসিংদীর বার্তা, নরসিংদীর কণ্ঠ, নরসিংদীর খবর, নরসিংদীর চোখের আলো, খোঁজ-খবর ও মাটির পুতুল। এছাড়া নরসিংদীর আদিয়াবাদের গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ‘আদিয়াবাদ সাহিত্য-ভবন ও ভাষাতত্ত্ব-কেন্দ্র’র মুখপত্র তথা নরসিংদীর তথ্যপত্র ‘নিসর্গ-বার্তা’র একাধিক সংখ্যায় এ-বিষয়ে তথ্য দেয়ার চেষ্টা আছে।
এসব চিঠিপত্র, আবেদন, প্রতিবেদন ও দাবিনামা, যা উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, সেসবে এই বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্রের পশ্চাদ্ভূমি (হিন্টারল্যান্ড)-এর বিবরণ এবং তার গুরুত্বের কথাও উঠে এসেছে যথামূল্যায়নসহ। তাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, নরসিংদী আবহমানকাল থেকেই যেমন ধান-পাট-কলা-আখ-কাঁঠাল এবং মেঘনার জলশস্য-সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়-কেন্দ্র, তেমনি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ‘সাইট’ উয়ারী-বটেশ্বরের পশ্চাদ্ভূমি ও প্রাচীন চীন-উপনিবেশ গ্রাম চিনিশপুর ও মাধবদী-বাবুরহাটের নব্য বস্ত্রশিল্পের অতীত রুমাই শহর (রোম), ইতালি ও মিশর-বাইজেন্টাইন নন্দিত মসলিনের ইতিহাস-হারা হতভাগ্য অঞ্চলও। এই প্রাচীন ইতিহাস ও পটভূমি নিয়ে নরসিংদীর মতো স্থান শুধু নতুন জেলা (১৯৮৪ সালে) হওয়ার কারণে আজ তার কোনো দাবির প্রতিই দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ। তাছাড়া প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো, ঢাকার শহরতলীরূপে গড়ে ওঠা এই নরসিংদীর বেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্ধকার যেন আরো বিশেষভাবে তার জন্মগত অধিকার ও অর্জন হয়ে ওঠেছে। পত্রিকা কেন, গিল্টি মারা মহাহ্রস্ব কর্ণকুহরের প্রান্তে বসে যদি সারা নরসিংদীবাসী আকাশ কাঁপানো কোনো মহাক্রন্দসী ভেঁপু বাজাতে শুরু করেন, তাহলেও এই অনন্তকালের মহান কুম্ভকর্ণ মহাশয়েরা মহানিদ্রা ভঙ্গ করে জেগে ওঠবেন, এমন ভরসা আছে কি?
‘নরসিংদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’-এর প্রস্তাবনা কোনো কলুষিত বোধ ও বুদ্ধির উত্তরাধিকারজাত প্রপঞ্চ নয়, বরং প্রকৃত চাহিদার লক্ষ্যে বিকৃতির প্রতিবাদ। বস্তুত নব সৃজনী চিন্তার একটি ধারা প্রতিষ্ঠারই স্বপ্ন নিয়ে এই আন্দোলন শুরু। গলির ধার করা আলো নয়, আবার ঢাকার তলীও নয়, একটা নিজস্বতা নিয়েই যেন শুরু হয় তার চলা। হোক তা স্থানিকতার মূল্যেই। সেই মূল্যেই ধন্য হবে নরসিংদী।
বিশ্বায়নের প্রভাব ও বিশ্ববিদ্যালয় : ‘কি ঘর বানাইলি হাসন শূন্যের মাঝার’
আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তা কার জন্যে? এককালে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে লেখা থাকতো ‘ডগস এন্ড ইন্ডিয়ান্স আর নট এলাউড’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন সাধারণের জন্যে নয়। উপরতলার মানুষের জন্যে। সাধারণের জন্যে উপরে উঠার কোনো পথ নেই সেখানে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘সিঁড়ি নেই’ উপরে উঠার। আধ্যাত্মিকভাবে না, এলিসের আশ্চর্য দেশের মতো বাস্তব এক শূন্যে ঝুলে আছে এই অনুগমনাগমন পথের শিক্ষা-ইমারতটি। কিছু লোকের জন্যে তাই এখন গলির নিয়ম, মানে গলিতে গলিতে অন্য ব্যবস্থা। যাকে বলেছি ‘গলিলিও’ ধারা। এক শ্রেণির ছাত্র এই বিকল্প মেনে নিয়েছে। তারই ফল যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচুর্য।
বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির দিক থেকে বাংলাদেশের যে-রেকর্ডই সৃষ্টি হোক, আমাদের এখন দাঁড়াবার জায়গা চাই, আশ্রয়ের ঘর চাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ এখন আর বড়ো আবশ্যক নেই। নিজের মতোন করে নিজেদের ঘর বানানো কঠিন নয়। পশ্চিম দেশে এখন আমাদের হাতই যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। সেখানে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের অবস্থান লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। শুধু তা-ই নয়, এই বিশ্বায়নের দিনে বহু পূর্বদেশ, যেমন জাপান, চীন, ভারত (বিশেষত দক্ষিণ ভারত) যে এখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে, এটাও আমাদের কাছে আদর্শযোগ্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কেন্দ্র হয়, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির স্থানিক শিক্ষা তার থেকে স্বাধীন না হোক, সিন্দাবাদের বুড়োর মতো অন্তত তাদের ঘাড়ে আর চেপে নেই সেই কেন্দ্রীয় ধারাটা। এখন যেকোনো দেশেরই কেন্দ্র আর প্রান্ত নিয়ে এই তুলনাটা করা যেতে পারে।
বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একসময় সুনাম ছিলো, আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে তা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু আজকের যুগশিক্ষা এবং যুগের দাবির বিষয়টি বিশ্বায়নের ডামাডোলে অনেক কিছুর সাথেই মিশে যাচ্ছে। এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমরা কোথায় আছি বা ছিলাম, কোথায় চলেছি? আসলে মূল বিষয়টি কী? এই ‘যুগের দাবি’ কার স্বার্থে, কে করে? তার প্রকারই বা কী? তার উপযোগিতা কোথায় এবং কীসে? সে কি কেন্দ্রগত শিক্ষায় না বহুকেন্দ্রিক শিক্ষায়, প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে না শত উপ-শিক্ষাকেন্দ্রে, একতম বিশ্ববিদ্যালয়ে না বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে (ভ্যাট-দ্বন্দ্বসহ)? এরকম বহু প্রশ্নের মুখোমুখী আজ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। ভাষানীতির মতোই এ-দেশের শিক্ষানীতিও অস্পষ্ট। এই সমস্যা যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই অমীমাংসিতভাবে সেই বাদুরঝোলা-ই ঝুলছে। আজ গলিতে গলিতে গড়ে ওঠা নানাবিধ ‘গলিলিও’ মহাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা দেখে আল মাহমুদের কবিতার কথাই মনে পড়ে যায়। তাতে আছে, ‘জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো ঝুলে আছে বিষণ্ন বাদুর’ কিংবা ‘বানরের চেঁচানিতে ভরে যায় সেগুনের শাখা’। দুটো উপমাই বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে করুণ চিত্রের দ্যোতক। কে না জানে, মাটির সাথে যোগহীনতায় কোনো কাজের জিনিস জন্মে না। তখন সবই শূন্যে ঝুলে থাকে। অন্যভাবে এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথও উল্লিখিত সেই প্রবন্ধেই বলেছেন তাঁর ‘সিঁড়ি-হারা শিক্ষাবিধান’ তত্ত্ব উপস্থিত করে। অনেক মাল-মশলা দিয়ে দোতালা বা বহুতলা বানিয়ে যদি উপরে উঠার সিঁড়ি না থাকে, তবে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। সিঁড়িহীন বাড়ির প্ল্যানটাকে তাই তিনি এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, “নিচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে, তার ভার বহন করেছে কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করেনি, দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।” আমাদের দুঃখটাই যেন তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে, “অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর নিচে সম্বন্ধ স্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি।” আমরা ঢাকার শিক্ষায় অভ্যস্ত। সেই ঢাকা শুধু নরসিংদী কেন, বাংলাদেশের যেকোনো স্থান থেকে কতোই-বা দূরে। কিন্তু ওই অক্সফোর্ডনামী দালানটা এবং এখন দেখাদেখি গলাগলি করা ‘গলিলিও’ উচ্চশিক্ষার অন্য বাড়িগুলোও যারা নিজেরাই স্বনামে বরহক অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, স্ট্যামফোর্ড ইত্যাদি নানা বসনে কতোই না অভ্রভেদী এবং তারও বেশি সোপানহীন। সেখানে উঠার সাধ্য কী!
আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আন্তর্জাতিক নানা নাম নিয়ে, যতোই আরো উপরে উঠছে, ততোই মাটি থেকে সরে যাচ্ছে। তার সিঁড়ি হয়ে ওঠছে অদৃশ্য এবং দূরের (মফস্বলের) ও গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের এবং ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে তার কাছে পৌঁছানো হয়ে ওঠছে দুরূহ। দেশে আজ মেধাবী ছাত্ররা দুর্লক্ষ্য নয়, জিপিএ ফাইভেরও অভাব নেই, কিন্তু সেই জ্ঞানান্বেষী বা অভীপ্সুদের ক’জন উপরতলায় অর্থাৎ ঢাকায় ভর্তি হতে পারছে? উচ্চশিক্ষার নামে তারা কোথায় পড়ছে ছিটকে, কে জানে? অন্যদিকে শিক্ষার ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় ডিগ্রির কাগজ বা সনদ এবং জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে সমতা এসে গেছে এই ফাঁকে। ডিগ্রি নয়, এখন শুধু কাগজ হলেই চলে। প্রকৃত শিক্ষা আজ কাগুজেশিক্ষা বা সনদধন্য শিক্ষারূপে এভাবেই প্রমোশন নিয়ে ছিক্কাতে উঠেছে নির্বিবাদে। যাদের অর্থবিত্ত আছে, তাদের উপরে উঠার সিঁড়ির প্রয়োজন নেই। আর অন্যদের তা নাগালের বাইরে। তাকে হাতের কাছে পাবার সুযোগ কই? মেধাশূন্য শিক্ষা এবং শিক্ষাশূন্য মেধার প্রতিযোগিতায় ছাত্র এবং অভিভাবক উভয়ের লক্ষ্য এবং লভ্য বিষয় এখন একটাই, সেই কাগুজেবিদ্যা তথা সনদ। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আশু মুক্তি আবশ্যক। কেন্দ্রীয় শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যতিত এশিয়ার অন্যান্য দেশ আজ সেই শিক্ষার পথেই চলেছে। আমরা আরজ আলী মাতুব্বরের স্বশিক্ষার আশায় বা আর ডি বর্মণের বাঙালির ‘এক তারাটা’ বাজাবার স্বপ্ন নিয়ে আনন্দে আছি। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তার জন্যে পথ চাই, সিঁড়ি চাই, সাধনা চাই আর চাই সহযোগিতা। কে করবে সহযোগিতা? কে কাকে বোঝাবে শিক্ষার দারিদ্র্য কী ভীষণ অভিশাপ!
হ্যাঁ, আপন শিক্ষায় যারা শিক্ষিত, তাদের বলা হয় স্বশিক্ষিত। তাদের মূল্য প্রাতিষ্ঠানিক তথা পরশিক্ষায় নয়। এই অর্থে ‘শিক্ষা’র মূল্য কী? কিছুই নয়। কথিত উন্নয়নের সিঁড়িও নয়, মাপকাঠিও নয় এবং দারিদ্র্যমোচনের উপায় তো নয়ই। শিক্ষা, উন্নয়ন, দারিদ্র্য এই শব্দগুলিকে আগে পরস্পর সংশ্লিষ্ট মনে করা হতো। ‘লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।’ কিন্তু দেখা গেছে, সে বড়ো মিথ্যা, কারণ শিক্ষাদাতা স্বয়ং শিক্ষকদেরই দারিদ্র্য ঘোচেনি কোনোদিন। অন্যদিকে জমি-জমা বেচে অশিক্ষিতরাও যারা ‘উন্নতি’ করতে চেয়েছে বিদেশে গিয়ে, তারাও উন্নয়ন বা সৌভাগ্য অর্জন দূরে থাক, বরং নিঃস্ব হয়েই ফিরেছে অনেকে। অতএব এই শব্দগুলি এখন দ্ব্যর্থবোধক কিংবা অতি-তাৎপর্যক। অর্থনীতির লোকেরা আজ স্বীকার করছে যে, কেবল আর্থিক দারিদ্র্যই দারিদ্র্য নয়, আসলে তা একটা দেশের প্রকৃত অভাবকে চিহ্নিত করে না। বাস্তবে ‘অভাব’ অনেক কিছুকেই বোঝায়। অভাব দূর না হলে দারিদ্র্যমোচন হবে না। অভাব সৃষ্টি হয় এবং অদূরীকর হয়, যখন মানুষ আপনাতে হয় নিঃস্ব, নিজস্বতা যখন শূন্য হয়ে ওঠে, অর্জনে হীন হয়। আপনার বলে তার আর কিছুই থাকে না। সেই দারিদ্র্য অমোচনীয়। মধ্যম আয়ে উন্নীত বাংলাদেশ আজ সেই অর্থে বড়োই দরিদ্র। আমরা তা আরো লক্ষ্য করবো নরসিংদীর শিক্ষাচিত্রে। মেঘনার তীরে একটি প্রযুক্তিধর্মী জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপনের ব্যর্থতায় সে কী নিদারুণ দরিদ্র! ঘোষিত ডিজিটাল শিক্ষার দেশে ‘গলিলিও’ শিক্ষালয়ে প্রান্তরের বিমুক্ত শিক্ষা, উদার শিক্ষা ও গন্তব্যগামী স্বাধীন শিক্ষার অভাব আজ সকলেই অনুভব করছে। অন্য ব্যাপারে ঘাটতি বাজেট বা লোন করে তা পূরণ করা যায়, কিন্তু শিক্ষার এই দারিদ্র্যমোচনের সে-দাবি পূরণ হবে কবে, আর কে-ইবা করবে তা?
‘আঞ্চলিক উন্নয়ন’ একটি শূন্যতা পূরণ ও অঙ্গীকার
৮ম জাতীয় পে-স্কেল ঘোষিত হলে সকলেই এবার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, দেশের চলমান অগ্রগতিই যথেষ্ট নয়, মানুষ আপনার স্বাধীনতায় হয় শক্তিমান ও সবল। এই স্বাধীনতাটুকু তাঁর ক্ষেত্রগত অর্জন। আপন ক্ষেত্র থেকে তাকে তুলে নিলে অপর স্থানে সে অকৃষ্ট, অসৃজ ও নিষ্ফলা হয়। কেননা সৃজনতা বা সৃজনশীলতাই তার আদ্যশক্তি ও স্বকীয়তার পরিচয়। তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে তাতেই। ব্যক্তিত্বহীন মানুষ নির্বীর্য এবং অস্তিত্বশূন্য।
আজ দিনের বদল হয়েছে, বিশ্ব কাছে চলে এসেছে। কিন্তু বিশ্বায়নে মানুষের মুক্তি ঘটেনি। দারিদ্র্য-মুক্তি একটা লক্ষ্য হতে পারতো, হয়নি। তাই ‘দারিদ্র্য’র সংজ্ঞা পাল্টানো প্রয়োজন, সেই সাথে দারিদ্র্য মোচনের উপায় বা প্রক্রিয়াও। দারিদ্র্য কোথায় এবং কতোদূর, তার সীমা, তার বিচার বা পুনর্বিচার হয়নি। ‘গরিবী হটাও’ কেবল আর্থিক বা অর্থনৈতিক দারিদ্র্য মোচনে সীমিত থাকায় বিপন্ন মানুষ বিপন্নতর পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। আদিকাল থেকেই মানুষ গরীব থেকেও জীবনকে গুটিয়ে নিয়ে বেঁচে রয়েছে এবং সংগ্রাম করে আজো এগিয়ে চলেছে। (সাধারণভাবে যে-কারণে বলা হয়, মানুষ না খেয়ে মরে না, খেয়েই মরে— জ্ঞানের অভাবে।) সুতরাং সংগ্রামের হাতিয়ার অর্থ (money) নয়, আত্মশক্তি বা বাঁচতে শেখায়, যার অর্থ বাঁচার জন্যে উপযোগী শিক্ষা, তথ্য এবং জ্ঞান চাই। বিপন্ন ভাষা বা Endangered Language এবং সেই সব ভাষাভাষীর মতোই বিপন্ন জাতি বা গোষ্ঠীরাও (যেমন আমাদের দেশের প্রাচীন রবিদাস, ঋষি, চামার, মুর্দাফরাস, কামার, কুমার, গাইন, নাগারচি, সুইপার, বাইদ্যা, বারুই, বেহারা, চৌদালি, বাওয়ালি প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী) আজ বিলীন বা বিলীয়মান অবস্থায় উপনীত। তাদের বলা হচ্ছে ‘হারিয়ে যাওয়া দরিদ্র গোষ্ঠী’ বা সমাজ। সব সমাজ বা গোষ্ঠীরই বেঁচে থাকার মূলে থাকে কিছু সংগ্রামী চেতনা ও জ্ঞান। যারা হারিয়ে যায়, তারা তাদের সেই টেকনোলজি ও যাপিত জীবনের প্রকরণও হারিয়ে ফেলে। জাতি শুধু অনুকরণ করেই উন্নত হয় না। তার অন্তর্গত তপস্যাও তার মূলে কাজ করে। তাকে ইতালীয় নৃ-সাংস্কৃতিক বিচারে বলে ‘সাবস্ট্র্যাটাম’-সম্পদ। (বিজ্ঞানী দীপংকর চট্টোপাধ্যায় যাকে প্রকারান্তরে বুঝিয়েছেন ‘সাবেক সংস্কৃতি’ বলেও) সেটা যেমন প্রকাশ-সত্যের বা ভাষার, তেমনি জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার। ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর থেকে নোয়াম চমস্কি পর্যন্ত সকল ঐতিহাসিক ও রূপান্তরশীল তাত্ত্বিকেরাই তা প্রমাণ করেছেন। উত্তর আধুনিক জ্ঞানবাদীরাও তার থেকে বাদ যাননি।
সেই অবতলবস্তুর শক্তি ও প্রেরণাই গোষ্ঠী বা জাতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। তার আইডেন্টিটিকে সবল করে। তার পারঙ্গমতার প্রকৃতিকে বুঝতে সহায়তা করে। আজ ছোট্টো সিঙ্গাপুরে যা সম্ভব হয়েছে, মালয়েশিয়ায় যা সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে টিংকু আব্দুর রহমান থেকে তাঁর উত্তরাধিকারদের হাতে, বিশেষত মাহাথির মোহাম্মদের স্বপ্নের ঘাটে ঘটে যেতে পারলো, বাংলাদেশে আরো কয়েক যুগেও তা আমরা দেখবো কি না সন্দেহ। বিশ্বায়ন থেকে উদারবাদী বিশ্বায়নে পৃথিবীর নানা কেন্দ্রে (তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও) যেসব পরিবর্তন ঘটছে, তার প্রভাবে স্বপ্রাবল্যে আজ মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্ব এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিও শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-বাসস্থান-যোগাযোগসহ কোথায় না আদর্শতুল্য? কিন্তু সেই তেজ, শক্তি, বীর্য ও সৃজনশীলতা আমাদের মতো হবু (expecting) মধ্যম আয়ের দেশে কোথায়? আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে জাতিমূলের কোনো শক্তিই কি কাজ করেছে বা করছে? কেন নয়? আমরা তাদের আগে স্বাধীন হয়েও কেন এখনো দাসত্বই করছি, এখনো করে চলেছি উপনিবেশী লিগেসি অনুসরণ, এখনো অমানবিক ধর্মের অস্ত্রোপসনাকেই মনে করছি আমাদের শক্তি? আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তনই কাজ করেনি, এ কেমন দুর্ভাগ্য আমাদের!
আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ নরসিংদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
এবার আবার শুরুতে ফিরে যাওয়া যাক। আমরা শুরু করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি নিয়ে। সেখান থেকে আবারো বলি, ‘আর কত খাণ্ডব পোড়াতে হবে’, আর কতোবার বলতে হবে এ-কথা, কতোবার বোঝাতে হবে যে, বস্তুসম্পদে এবং কারুজ্ঞানে আমরা একসময় পিছিয়ে ছিলাম না, কিন্তু আজ আমরা শিক্ষা-দারিদ্র্যে জগত-ভিখারি। এ-দারিদ্র্য মোচনের জন্যে পাশ্চাত্য ঋণ-বিলাসে ভুগতে চাই না। দারিদ্র্য মোচনের মূল চাবিকাঠি শুধু অর্থঋণ নয়, সে-কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই আর পরঅনুকরণ নয়, নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে চাই। প্রযুক্তিজ্ঞান ব্যতিত আজকের পৃথিবীতে তা সম্ভব নয়। শিক্ষার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই। নরসিংদী বড়ো দরিদ্র। তার খাদ্যের অভাব নেই, তার মৃত্তিকাশস্য, জলশস্য সবই পরিপূর্ণভাবে আছে, আছে বস্ত্রও। কিন্তু দারিদ্র্যের শেষ নেই। এককথায় আমাদের মনে পড়বে যুক্ত বাংলায় হক সাহেবের মন্ত্রীত্বের কালে দেশে খাদ্যের অভাব ছিলো না, কিন্তু জয়নুলের তুলি এবং ‘অন্নদাতা’র কৃষাণ চন্দরদের কলম বলছে, তখন রাজধানীতে দুর্ভিক্ষ ছিলো। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সাইট আছে বাংলাদেশে। নরসিংদীতেই এর প্রথম দাবি উঠেছিলো প্রতিষ্ঠার। আজো জানি না, তা হবে কি হবে না। আমাদের দাবির ভিত্তি একটি বিশেষ শিক্ষাদর্শন। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্থক্য থাকবে, সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তা হবে পৃথক, এর প্রতিষ্ঠা হবে আধুনিক চিন্তা ও দারিদ্র্যমোচন-সম্ভব জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় পরিবেশের মধ্যেই থাকবে তার সাধনার মৌল উপাদান। নরসিংদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তার আপন উপলব্ধ ও পরীক্ষিত জ্ঞানেই ফিরিয়ে আনবে তার ঋদ্ধ অতীত ও লোকবিশ্রুত ঐতিহ্য।
ড. মনিরুজ্জামান
ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক
সাবেক অধ্যাপক ও ডিন, কলা অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা একাডেমি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক